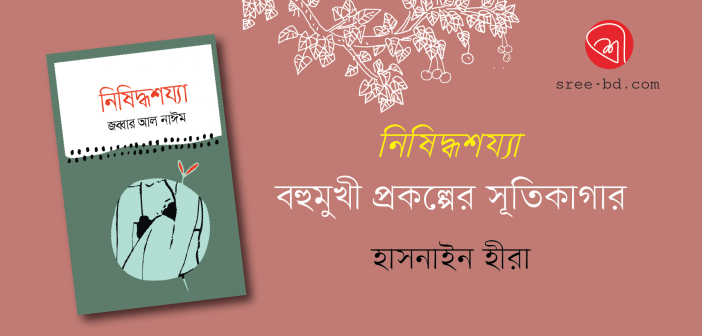‘বেঁচে আছি’ না বলে যদি বলি ‘বেঁচে থাকি’— তাহলে জীবনের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ যেন হারিয়ে ফেলি। ‘জীবন’ যেন অন্যের অধীন হয়ে পড়ে। ক্ষেত্র বিশেষে এই অধীনতা বহু রকম হতে পারে। অলীক ধারণার মানুষ একরকম ভাবতে পারে, আবার লৌকিক ধরণার মানুষ আরেক রকম ভাবতে পারে। তবে সাহিত্যে এই ধারণা অন্য আঙ্গিকে রূপ নেয়। অনেকটা লৌকিক ধারণার সাথে রেখাঙ্কন করলেও শেষ পর্যন্ত তা পুরো বৃত্ত পূর্ণ করতে পারে না। লৌকিক ও অলৌকিক এর মাঝামাঝি কোনো এক ধূসর জগত দিয়ে সাহিত্যের জীবন গমনাগমন করে। মানুষ তাই সাহিত্যের মোড়কে জীবনকে সাজাতে চায়। কারণ, বেঁচে থাকার বাইরে জীবনের আরও একটা বড়ো তাৎপর্য সে অনুভব করে। ফলে জীবনের সাথে নতুন নতুন অর্থ যোগ হয়। বলা যায়, এই নতুন অর্থ যোগ না হলে তাকে সাহিত্য বলা যায় না।

নিষিদ্ধশয্যা | জব্বার আল নাঈম | উপন্যাস | প্রচ্ছদ: বিধান সাহা | প্রকাশক : অর্জন প্রকাশনী | মূল্য : ৪০০ টাকা। বইটি কিনতে কিনতে এখানে ক্লিক করুন।
নতুন অর্থ যোগ হওয়া মানে, নতুন কোনো জ্ঞানজগতের ভেতর ভ্রমণ করা। ফলে মুহুর্মুহু জীবনের রং ও গতি বদলে যেতে থাকে। সাহিত্যের জীবন তাই বাস্তবতাকে উৎরে ওঠার জীবন। বাস্তব জীবন থেকে তার দূরত্ব অনেক। উৎরে ওঠা জীবনের পাঠ নিতে তাই বাস্তব জীবন পারিভাষিকতায় উন্মুখ হয়ে ওঠে। মনে হয়, ‘জীবন যদি এমন হতো!’ আসলে বাস্তবে এমন জীবন হয় না। আর হয় না বলেই আমরা সাহিত্য করি, এবং জীবনের অর্থ যোগ করে করে পাঠ নেই। শরৎ বাবুর ‘দেবদাস’ উপন্যাসের কথা স্মরণে নেওয়া যেতে পারে। দেবদাস-এর উপরে সেই সময়ে একটা সিনেমাও তৈরি করা হয়েছিল। সিনেমাটা যারা দেখেছেন, তারা অনেকেই চোখের জল সিঞ্চন করেছেন। এমন কি দেবদাস পড়েও অনেকে কেঁদেছে। শরৎ চট্রপাধ্যায় নিজেও সেই সিনেমা দেখে বলেছিলেন, ‘দেবদাসের জীবন এতটা নিঃসঙ্গ, অসহায় আর করুণায় ভরা, আগে জানলে দেবদাস এভাবে লিখতাম না।’ সাহিত্যে জীবন এমন প্রগাঢ় হয়ে ওঠার কারণ হলো, বাস্তব জীবনের সাথে ভাষিক জীবনের বাড়তি অর্থ যোগ হওয়া। দেবদাস উপন্যাসকে সিনেমায় কনভার্ট করতে গিয়ে তাই আরও বেশি রসাত্মক, ভাষিক ও শৈল্পিকরূপায়ন ঘটেছে। যা আমাদের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে আরও বেশি ঘন করে তোলে।
এই কথাগুলো হয়তো পুরনো। কিন্তু পুরনো কথাগুলোই নতুন করে হাজির হচ্ছিল জব্বার আল নাঈমের উপন্যাস ‘নিষিদ্ধশয্যা’ পড়তে গিয়ে। জব্বার নিষিদ্ধশয্যায় জীবনের যে, চিত্রপট অঙ্কন করেছেন, তার কাহিনিও ভীষণ নিঃসঙ্গ, করুণ ও অসহায়ত্বে ভরপুর। একইসাথে বিপুল উৎসাহ, উদ্ধীপক ও প্রতিবাদমুখরও। বলা যায় দ্বিমুখি এক দ্বন্দ্বের দাঁড়ি কমায় ভরে উঠেছে পুরো উপন্যাস। জীবনের নানা সংকট, সংশয় ও টানাপোড়নকে জালবন্দি করেছেন নাঈম।
জব্বার নিষিদ্ধশয্যায় জীবনের যে, চিত্রপট অঙ্কন করেছেন, তার কাহিনিও ভীষণ নিঃসঙ্গ, করুণ ও অসহায়ত্বে ভরপুর। একইসাথে বিপুল উৎসাহ, উদ্ধীপক ও প্রতিবাদমুখরও। বলা যায় দ্বিমুখি এক দ্বন্দ্বের দাঁড়ি কমায় ভরে উঠেছে পুরো উপন্যাস। জীবনের নানা সংকট, সংশয় ও টানাপোড়নকে জালবন্দি করেছেন নাঈম।
উপন্যাসের বড়ো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ‘স্বপ্না’। যে কিনা মায়ের পতিতাবৃত্তির হাত ধরে হয়ে উঠেছে আরেক ‘পতিতা’। স্বপ্নার এই হয়ে ওঠা অনিবার্য কি না তা নিয়ে দামি দামি প্রশ্ন খরচ করা যায়। কারণ স্বপ্নার জীবনচক্র অন্য দিকেও ঘুরে যেতে পারত। কিন্তু ঘোরেনি। লেখক ঘটনাচক্রকে যেভাবে ডিল করেছেন, তাতে স্বপ্না কিংবা তার মায়ের প্রতিতাবৃত্তির জন্য তারা নিজেরা দায়ি নয়। সমাজ বা রাষ্ট্র তাদের এই পথে ছুঁড়ে দিয়েছে। উপন্যাসটা পড়তে পড়তে অনেকেই মনে করতে পারেন, এটা একটা পতিতাবৃত্তির গল্প। ধারণাটা একেবারে অমূলক নয়। তবে পুরো সত্য হিসাবে মান্য করা উচিত বলেও মনে হয়নি। যাই হোক, সেই জাজমেন্টের ব্যাপারটা পাঠকের হাতেই ন্যাস্ত থাক। আমি অন্য একটা বিবেচনা থেকে উপন্যাসটিকে দেখতে চাই। আমার বরাবরই মনে হয়েছে, লেখক স্বপ্নার পতিতাবৃত্তির আশ্রয়ে একটা আখ্যান তৈরি করেছেন, সত্য। পতিবৃত্তির একটা জগতকে দেখাতে চেয়েছেন, সেটাও সত্য। কিন্তু তার অন্তরালে অন্য একটা সত্য বা আখ্যানবৃত্ত বড়ো হয়ে উঠতে চায়। আমার মনে হয় লেখক সেই বৃত্তের দিকেই তীর ছুঁড়ে দিয়েছেন ক্ষীপ্রতার সাথে। যেখানে পুরো একটা মানব জীবনকে ইমাজিন করা যায়। আর সেই মানব জীবন অতীতকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমানের যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে, তার ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে? দূর সমকালে কি অপেক্ষা করছে? ঠিক তার একটা সরল ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সময়ের ভঙ্গুরতা বা নির্মাণ-বির্নিমাণ ও জীবনের জটিলতর এক মনস্ততত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেটা বিবেচনায় নিলে উপন্যাসের মূল চরিত্র বলে কিছু থাকে না। কেননা, আখ্যানের চরিত্রগুলো একেকটা একেক রকম। খল চরিত্রের যিনি আছেন, তিনি তো ঐ চরিত্রের মূল বা প্রধান। আবার নায়ক কিংবা নায়িকার চরিত্রে যারা থাকেন, তারা তো স্ব স্ব ঐ চরিত্রের প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তাহলে একটা চরিত্রকে ধরে পুরো আখ্যানকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। তাই প্রধান বা মূল চরিত্র বিবেচনা না করাই ভালো। বরং চরিত্রগুলোকে খণ্ড খণ্ড গল্পাকারে যোগ করে নিলে যোগফল বড়ো একটা আখ্যান বা বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। তখন চরিত্র ছাপিয়ে গল্পটা বিষয়ে পরিণতি লাভ করে। জব্বারের ‘নিষিদ্ধশয্যা’ সেরকমই বড়ো একটা বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।
শুরুটা আশ্চর্যরকম ঝা ঝা করা আবহের উষ্ণতায় মোড়ানো। ছমছমে অদ্ভূত এক অনুভূতির ভেতর পাঠক নিমিষেই নতুন এক জগত কল্পনা করতে পারবেন। মনে হবে, নতুন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন তিনি। যা নতুন এক অভিজ্ঞানও বটে। মনে হতে পারে, গল্পের শেষটা লেখক শুরুতেই বলে নিচেছন জাদুবাস্তবতার মোড়কে। মৃত মানুষের সাথে কথা বলছে বাস্তবের মানুষ। দুইজন দুই জগতের বাসিন্দা। তার মানে লেখক একটা জগতকে আরেকটা জগতের মুখোমুখি এনে দাঁড় করে দিয়েছেন। যারা কেউ কাউকে মানতে চায় না। আরও গভীরের দিকে তাকালে দেখা যাবে, একটা জীবন আরেকটা জীবনকে যেন শাসন করতে চাইছে। মূলত জীবনেরই বহুমুখি দ্বন্দ্ব প্রকল্পের একটা সৌধ এই উপন্যাস। যেখানে জীবনের গভীর কোনো দ্বন্দ্বকে উপলদ্ধি করতে করতে পাঠক কখন যে আখ্যানের সিংহভাগের দুয়ার খুলে বসেছেন, তা তিনি টেরই পাবেন না।
কথাকে শিল্প করার কৌশল জব্বারের কব্জিতে রপ্ত হয়ে আছে। চাইলেই তিনি ঢেলে সাজাতে পারেন। রং লাগাতে পারেন। কথার সাথে কথার সম্পর্ক উত্তীর্ণের পর্যায়ে তুলে শেষ লেপনটাও লেপে দিতে পারেন চমৎকারিত্বের সাথে। কোনো কথাই অন্য কোনো কথার অনাত্মীয় বলে মনে হয় না। এটাই জব্বারের আখ্যান নির্মাণের বড়ো টেকনিক।
কথাকে শিল্প করার কৌশল জব্বারের কব্জিতে রপ্ত হয়ে আছে। চাইলেই তিনি ঢেলে সাজাতে পারেন। রং লাগাতে পারেন। কথার সাথে কথার সম্পর্ক উত্তীর্ণের পর্যায়ে তুলে শেষ লেপনটাও লেপে দিতে পারেন চমৎকারিত্বের সাথে। কোনো কথাই অন্য কোনো কথার অনাত্মীয় বলে মনে হয় না। এটাই জব্বারের আখ্যান নির্মাণের বড়ো টেকনিক। নিষিদ্ধশয্যায় তাই ভাষার কুটকৌশলের আনাগোনা নেই। বরং কন্টেটের উপর চোখ রেখে লেখক দৃঢ় লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করেছেন। তিনি হয়তো ভেবে নিয়েছেন, ‘ধান ভানতে এসে শিবের গীত’ শোনানো সমীচীন নয়। ফলে নিষিদ্ধশয্যার আখ্যান প্যাসপ্যাসে কোনো গল্প না। গল্পের পাশে কিছু নীতিবাক্য এমনভাবে এসে জায়গা দখল করেছে যেন, এটাই তার চিরদিনের আবাসস্থল। যা মননশীলতার বিশেষ উপাদেয় হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে। সভাবতই জব্বার ন্যারেটিভের ভঙ্গিতে নানাবিধ ইতিহাস ও মিথের সন্ধান করেছেন। ঘটনাকে টেনে নিয়ে গেছেন ঐতিহাসিক দেয়ালের দিকে। ঘুমিয়ে পড়া চেতনকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যা ব্যক্তিসচেতনা ও সমাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা আরও বেশি গতিময় করে তোলে। ফলে নৈতিক অনৈতিকের ব্যাপারগুলোও উপন্যাসের পরতে পরতে জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। দেখা যায় সমাজের ধনতান্ত্রিক বা ক্ষমতাবানেরা কীভাবে সমাজটাকে নিজেদের কব্জায় রেখেছেন। বিশেষ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মানবিক সমাজকে কীভাবে ডলে-মুচড়ে স্থলন করছে প্রতিনিয়ত। রাজনৈতিক হ্যানস্থাও করায়াত্ব করে নিয়েছে সমাজকে। যা ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য ভয়ংকর রকমের এক অশনিবার্তা। যেখানে ধর্ম একটা ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ধর্ম যেখানে উদর মানবিকতায় বিশ্বাসী।
তো সমাজের এই জটাজালকে চিহ্নিত করার ভেতর দিয়ে নাঈম মূলত বির্নিমাণ করতে চেয়েছেন পুরো ব্যবস্থাপনাকে। আঙুল ব্যবহার করে নষ্টের জায়গাটা ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। ফলে লেখকের অবস্থান স্পষ্টত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। কারণ, সিষ্টেম বদলানোর একমাত্র নিয়ামক হলো রাষ্ট্র। সুতরাং রাষ্টকেই এই অপব্যবস্থার প্রতিকারে আগ্রহী হয়ে উঠতে হবে। যা সে করেনি।
‘নিশিদ্ধশয্যা’ বহুমুখী আলোচনার দিকে টেনে নিতে চায়। চলমান সমাজে নারীর নিগূঢ়তা ও প্রতিবাদের জায়গা এবং তার পরিভাষা নিয়ে কথা বলা যায়। বললাম না। বিশ্বমানবিকতার অবক্ষয়ের প্রসঙ্গ তুলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা খরচ করা যায়। সেই সুযোগ উপন্যাসটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমি সেদিকেও গেলাম না। আখ্যানের ধারাবহিক বর্ণনা দিয়ে পাঠকের মনকে কিছুটা তৃপ্ততায় ভেজানো যেত। অথচ তা করলাম না। আমি চাই পাঠক নিজেই টেক্সটা পড়ুক। আর তার অভিঘাতের দোতারা নিজেই বাজাতে থাকুক, ঠিক তাঁর মতো করেই।

হাসনইন হীরার জন্ম সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার বাঙ্গালা গ্রামে । জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সহকারী ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। লিখছেন দ্বিতীয় দশক থেকে। ‘বাঁক বাচনের বৈঠা’ তার প্রথম কাব্যগ্রস্থ। এই গ্রন্থের জন্য তিনি অর্জন করেছেন, জেমকন তরুণ কবিতা পুরস্কার-২০২০।