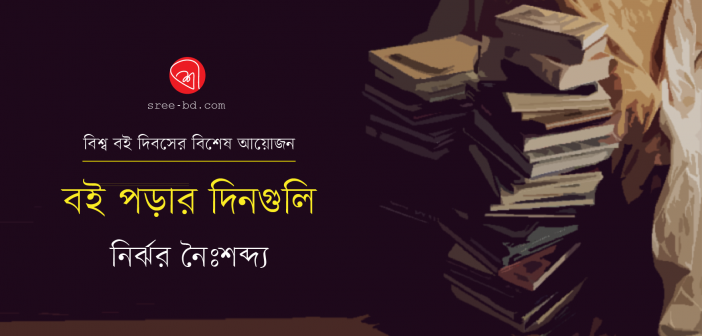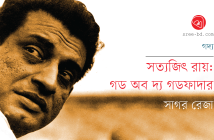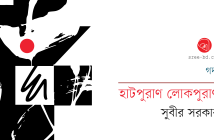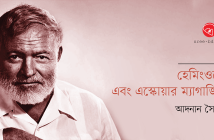একজন পাঠক যদি ৭০ বছর বাঁচেন, আর তিনি যদি ১০ বছর বয়স থেকে প্রতিদিন ১টা করে বই পড়েন তবে সর্বসাকুল্যে ২০ হাজার বই পড়তে পারেন। কিন্তু একজন সিরিয়াস পাঠক তিনি যতই নিয়মিত পাঠক হোন প্রতিদিন একটা করে বই পড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সব বই তো আর চটি বই নয়, বড়ো মানে পাঁচশো থেকে হাজার পৃষ্ঠার বইও থাকে ওখানে। এর বাইরে সেই পাঠকের বিবাহ থাকে, জ্বর থাকে, সুন্নতে খৎনা থাকে, গর্ভধারণ থাকে, ঘুম, আহার, স্নান, গান, কাম, চাকরি, বেড়ানো এমন অনেক কিছুই থাকে। সেই হিসেবে একজন সিরিয়াস পাঠক আমার মতে সারা জীবনে সর্বসাকুল্যে ৭-৮ হাজারের বেশি বই পড়তে পারেন না। কিন্তু বই কিনতে পারেন। বইয়ের সঙ্গে স্নেহ, মমতা, প্রেম, ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়, বইয়ের সঙ্গে বসবাস করতে করতে বই না পড়েই বইয়ের ভেতরে ঢুকে যেতে পারেন। বই হয়ে যায় পাঠকের হাত, পা, চোখ, নাক, জিভের মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।
আর পাঠক যদি পণ্ডিত বা লেখক বা গবেষক হয়ে থাকেন তবে তাদের অত বই পড়া লাগে না, কারণ তারা প্যাশন কিংবা নেশার কারণে বই পড়েন না, তারা পড়েন কাজের প্রয়োজনে। সুতরাং সারা জীবনে তাদের নির্বাচিত চার-পাঁচশো বা বড়োজোর হাজার দুয়েক বই পড়লেই, নোট নিলেই তারা এক একজন পণ্ডিত, গবেষক বা লেখক হয়ে যেতে পারেন। তবে তাদের যদি বই পড়ার প্যাশন থাকে তারাও অনায়াসে এর ৬-৭ হাজার বই পড়ে ফেলতে পারেন।
তথ্য, উপাত্ত ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞান আহরণের জন্য আমি কখনো বই পড়িনি বললেই চলে; পাঠ্যবই ছাড়া। আর সেইসব মহৎ বইয়ের ভেতর আমি দুয়েক পৃষ্ঠার বেশি ঢুকতে পারিনি, প্রাণ টানেনি—সেই জাতীয় বইও পড়িনি তেমন।
ওপরের ভূমিকার তেমন কোনো কারণ নাই। আমি একজন পাঠক এবং অতি ক্ষুদ্র একজন লেখক হিসেবে আমার বই পড়ার স্মৃতি আর দুয়েকটা অভিজ্ঞতার গল্প বলব বলেই একটু কথা বলে নিলাম।
আমি বই কেন পড়ি? চিরদিন আমি বেশিরভাগ বই পড়ে এসেছি আনন্দের জন্য, সময় কাটানোর জন্য, অবকাশ যাপনের জন্য, বিচ্ছিরি বাস্তবতার ভেতর থেকে পালিয়ে থাকার জন্য। এর বাইরেও আরও কতিপয় কারণ থাকতে পারে। তবে প্রধান কারণ হয়তো শেষটাই, মানে, আমার বইপড়ার শুরু হয়তো পলায়নকামিতা থেকে। সেইই কথা, পালিয়ে আনন্দ খোঁজার জন্যই বইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সখ্য। তথ্য, উপাত্ত ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞান আহরণের জন্য আমি কখনো বই পড়িনি বললেই চলে; পাঠ্যবই ছাড়া। আর সেইসব মহৎ বইয়ের ভেতর আমি দুয়েক পৃষ্ঠার বেশি ঢুকতে পারিনি, প্রাণ টানেনি—সেই জাতীয় বইও পড়িনি তেমন। মানে লেখকের লেখকটাইপ লেখকদের বই আমি কম পড়েছি। কতিপয় পণ্ডিত মনে করেন একজন লেখককে পাঠকের কথা ভাবার দরকার নাই, তারা লিখবে মূলত নিজের জন্য। পণ্ডিতগণ চান যে পাঠক হাবিয়া ও রৌরবে যাক, জাহিমে গিয়ে বরফের নিরক্ষর বই পড়ুক। আমি নিজে অবশ্য এমন মনে করি না। আমার মনে হয় লেখা শরীরের মাথা থেকে আঙুলের মাথায় বের হয়ই মূলত পাঠকের জন্য, কতিপয় পাঠকের জন্য নয়, সার্বিক পাঠকের জন্য। নাহয় তো সেইসব লেখা বা চিন্তাপত্র মাথার ভেতরেই প্রতিনিয়ত দাফন আর দাহ হতো। কতিপয় কাজ ছাড়া মানুষ যা করে সবকিছুই অন্যকে দেখানো আর জানানোর জন্য করে। তাই শুধু শুধু মহৎ লেখক হবার বাসনায় সহজ কথাকে কঠিন করে প্রসব করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। সহজ কথা সহজে বলতে পারাটাই যোগ্যতা। সহজ কথাকে ক্রমাগত কঠিনভাবে প্রকট করার ব্যাপারটা খানিকটা ক্রনিক ডিসেন্ট্রির মতো। তবে সহজ মানেই বাজারের ফর্দ, আর জমির দলিল টাইপ কিছু নয়। সহজভাবে প্রকাশ করার জন্য সব থেকে ললিত আর আকর্ষক ভাষাটা জানাই একজন লেখকের যোগ্যতা। জগতের অনেক বড়ো বড়ো লেখকের, মহৎ লেখকের অনেক বইও আমি এখনো মন চাইলেও পুনর্বার পড়তে পারি। সুতরাং লেখকেরও লেখা উচিত আনন্দের জন্য, পাঠককে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়। আর পাঠকেরও পড়া উচিত আনন্দের জন্য।
এখন বিশাল এক লেখকের একটা বইয়ের নাম করি, যে বইটা আমি আনন্দ নিয়ে পড়েছি শৈশবে, যৌবনে আর যৌবনশেষেও। বইয়ের নাম ‘দন কিহোতে’, লেখকের নাম মিগেল দে সেরভানতেস। ইশকুলে থাকতে সেবার অনুবাদে যেটার নাম ইংরেজি উচ্চারণে ‘ডন কুইক্সোট’ ছিল। সেরভানতেস শেক্সপিয়ারের সমবয়সি ছিলেন। যদিও পৃথিবীর প্রথম উপন্যাস ‘দ্য টেইল অব গেনজি’ একাদশ শতাব্দীতে জাপানে লেখা হয়েছিল, মুরাসাকি শিকিবু নামের একজন নারী লেখকের, তবু সেরভানতেসের আগে পৃথিবীর কোথাও কাব্যিক আবহে এমন গদ্যাখ্যান আর লেখা হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।
আমি শৈশবেই উত্তরাধিকারসূত্রে আমার দাদা, বাবা আর বড়োভাইয়ের সংগ্রহের বইগুলি আমার দখলে নিয়েছিলাম। যেহেতু বাড়ির অন্যরা দখল নিচ্ছে না, তাই ঘরের নানা জায়গা থেকে ছড়ানো-ছিটানো বই এক করে নিজের ঘরে নিয়ে এলাম।
বই বেশি ছিল না, সর্বসাকুল্যে চার-পাঁচশো। বইগুলির বিষয় ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি জাতীয়। দুয়েকটা নাম করতে গেলে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘ছেলেদের রামায়ন’, রাজশেখর বসুকৃত ‘কৃষ্ণদ্বৈপায়ন’, বেদব্যাসের ‘মহাভারত’-এর সারানুবাদ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কমলাকান্তের দপ্তর’, ‘কপালকুণ্ডলা’, ডাক্তার লুৎফর রহমানের ‘উন্নত জীবন’-সহ অনেক বই, বার্ট্রান্ড রাসেলের ‘সুখ’, ডেল কার্নেগির প্রতিপত্তি ও বন্ধুত্ব, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, রোমেনা আফাজের ‘দস্যু বনহুর’, নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের ‘আনোয়ারা’, কাজী ইমদাদুল হকের ‘আব্দুল্লাহ’, দানিয়েল দিফুর ‘গালিভারের ভ্রমণ কাহিনি’, কাজী নজরুল ইসলামের ‘রিক্তের বেদন’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষের কবিতা’, ‘গীতাঞ্জলি’-সহ এ জাতীয় আরও অনেক বই।
আমি যখন ফোরে পড়ি মা ছোটো মামাকে দিয়ে নানাভাইয়ের বানানো বেশ বড়ো সাইজের কাঠের একটা শোকেস আমাকে দিলো বই রাখার জন্য। আমাকে দেবার আগে ওখানে কাচের বাসনকোসন, কাপ-প্লেইট, গ্লাস এইসব সাজিয়ে রাখা হতো। আমাকে দেবার কারণ ওটার গ্লাস ভেঙে গিয়েছিল। সে যাই হোক আমি ওইটাতে সব বই সাজিয়ে রাখলাম, ওপরের তিনটা তাকে। আরও খালি রইল তিনটা তাক।
মাঝে মধ্যে পাঁচ-দশ টাকা হাতখরচা পেতাম, ঈদে বড়োদের সালাম করে পাঁচ-দশ টাকা সালামি পেতাম। ওইগুলি খেয়ে না ফেলে জমিয়ে বই কিনতাম। এইভাবে যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন দেখা গেল শেল্ফটার আরেকটা তাকের অর্ধেকটা ভরে গেছে। সিক্সে উঠে একদিন রাহগীর মাহমুদ স্যারের গানের ইশকুল মালঞ্চে গান শেখার জন্য ভর্তি হলাম। উনার বুক শেলফ থেকে প্রথম যে-বইটা চুরি করলাম সেটা একটা কবিতার বই, বইয়ের নাম ‘না প্রেমিক না বিপ্লবী’, লেখক নির্মলেন্দু গুণ। তারপর ইশকুলের লাইব্রেরি থেকে চুরি করলাম সমরেশ বসুর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’। বইয়ের দোকান আদর্শ লাইব্রেরি থেকে চুরি করলাম সমরেশ বসুর ‘প্রজাপতি’। ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি থেকে চুরি করলাম আকবর হোসেনের ‘অবাঞ্চিত’ উপন্যাস। এইভাবে চুরি করে, আর হাতখরচার টাকা জমিয়ে চার নম্বর তাকটা ক্লাস সেভেনে উঠতে উঠতেই ভরিয়ে ফেললাম।
পাঠ্যবইয়ের ভাঁজে আউট বই রেখে রাত জেগে পড়তাম। মা মাঝে মধ্যে এসে দেখে যেত তখন পড়া মুখস্থ করার ভান করতাম, পড়তাম আলোচ্য অংশটুকু অমুকের তমুক গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে… ইত্যাদি। অথচ আমি মুখস্থ কিছুই করতাম না, পারতামও না, ফলে পরীক্ষার আগের রাত ছাড়া ওই অর্থে পাঠ্যবই পড়তাম না।
ভাবলাম, এইবার আমার এই ছোট্ট লাইব্রেরির একটা নাম দেওয়া যাক। তখন রাহগীর স্যারের লেখা একটা কবিতা আমার মেজোভাইকে আবৃত্তি করতে শুনতাম প্রায়ই, ‘আমিও হৃদয়ের নির্জন যমুনা তীরে ভালোবাসার তাজমহল গড়ব…’। লাইনটা আমার বেশ ভালো লাগত। একদিন বাবার আন্ডারে কাজ করত এক ফরেস্ট অফিসার তার একটা কবিতার খাতা বাবাকে পড়তে দিলো। বাবা সেটা পড়ে পড়ে হাসছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে খাতার ওপর লেখা নাম পড়লাম, ‘প্রণয় প্রলাপ’।
ক্লাস সেভেনের বছর আমি একলার একটা ঘর পেয়ে গেলাম বাড়ির পশ্চিম সাইডে। ঘরে কোনো জানালা নাই। বুকশেল্ফটা ঘরের একপাশে বেশ মানিয়ে গেল। আর হয়ে গেল আমার জানালাবিহীন ঘরের একটা দিঘল জানালা। ভাবলাম, এইবার আমার এই ছোট্ট লাইব্রেরির একটা নাম দেওয়া যাক। তখন রাহগীর স্যারের লেখা একটা কবিতা আমার মেজোভাইকে আবৃত্তি করতে শুনতাম প্রায়ই, ‘আমিও হৃদয়ের নির্জন যমুনা তীরে ভালোবাসার তাজমহল গড়ব…’। লাইনটা আমার বেশ ভালো লাগত। একদিন বাবার আন্ডারে কাজ করত এক ফরেস্ট অফিসার তার একটা কবিতার খাতা বাবাকে পড়তে দিলো। বাবা সেটা পড়ে পড়ে হাসছিল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে খাতার ওপর লেখা নাম পড়লাম, ‘প্রণয় প্রলাপ’। এই নামটাও ভালো লেগে গেল। আমি স্যারের কবিতার লাইন থেকে ‘নির্জন’ শব্দটা নিলাম আর ফরেস্ট অফিসারের খাতা নাম থেকে ‘প্রণয়’ শব্দটা নিলাম। শব্দ দুটো জুড়ে দিয়ে বানালাম ‘নির্জন প্রণয়’। এটাই আমার ছোট্ট পাঠাগারের নাম দিলাম। একটা কাগজে লিখে বুকশেলফের একপাশে এশিয়ান গাম দিয়ে লাগিয়ে দিলাম। মন ভরলো না। প্রতিটি বইয়ে এই নাম থাকতে হবে এইটা ভাবলাম। পাঁচ লাইনের একটা রাবারস্ট্যাম্প বানিয়ে ফেললাম। তারপর প্রত্যেকটা বইয়ে সিল মারলাম। স্ট্যাম্পে যা লেখালাম তা হল, ‘নির্জন প্রণয়, ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, স্বত্বাধিকারী: নির্ঝর চৌধুরী, গ্রাম: হালকাকারা, ডাকঘর: চিরিঙ্গা, উপজেলা: চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার। বই নং…’
আমার ক্লাস এইটের শুরুর দিকে একদিন লাল কালি দিয়ে বড়ো একটা কাগজে ‘নির্জন প্রণয়’ লিখে রুমের বাইরে দরজার ওপরে ফাঁকা জায়গায় লাগিয়ে দিলাম। তার কয়েকদিন পর কোনো একদিন ছুটির দিনে বিকেলবেলা শুনলাম বাবা আমার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছেন। আমি প্রায় ছুটে গেলাম। বললেন, ‘এখনই ওই কাগজ খুলে ফেল’। আমি খুলে ফেললাম ভয়ে। বললেন, ‘নির্জন প্রণয় মানে কী, গোপনে প্রেম করা? খুব পেকে গেছিস…’ এ জাতীয় কথা। আমি তো আসলে এত ভেবে ওই নাম দিইনি তখন। কিন্তু বাবার কথায় মাথায় বুদ্ধি এল। আমি বললাম, ‘আপনি যা ভাবছেন, ঠিক তা নয়, এটা আসলে নির্জনে আল্লাহর সঙ্গে প্রেমের মতো ব্যাপার’। এই কথা বলে বাবা সামনে থেকে আমি সেদিনের মতো চলে গেলাম। কয়েকদিন পর বাবা আমাকে ডেকে বললেন, ‘তোর কথা ঠিক আছে। নামটাও সুন্দর। আমাদের নতুন বাড়িটা যখন বানানো হয়ে যাবে তখন বাড়ির নাম রাখব ‘নির্জন প্রণয়’।
কলেজ পর্যন্ত আমার ‘নির্জন প্রণয়’-এ বই জমেছিল হাজার দেড়েক মতো। আমার অনুপস্থিতিতে বেশিরভাগ বই-ই ইঁদুর আর উইপোকা মিলে খেয়ে ফেলেছে। কিছু বই নিজের কাছে এনেছিলাম। এখন বইয়ের মলাট আর কঙ্কাল মিলিয়ে হয়তো শ-দুয়েক বই আছে। একবার বাড়ি গিয়ে কয়েকটা নিয়ে বাকিগুলি ভাইয়ের মেয়েটাকে দিয়ে এসেছি। এখন মা-বাবা কেউই নাই, আমার ‘নির্জন প্রণয়’ও নাই। আর বাড়ি যেতেও মন করে না।
‘ঠাকুরমার ঝুলি’ পড়ার বয়সে আমি বড়োদের বই পড়ি। আর প্রায় প্রতিদিন তিনমাইল হেঁটে একটা কারিতাস নামের এনজিওর পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে আসতাম। মনে আছে একই সঙ্গে কখনো এটা, কখনো ওটা এই করে পড়া শেষ করেছিলাম তিনটা উপন্যাস’ ম্যাক্সিম গোর্কির মা, হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকাস, ভিক্তর ওগোর ‘লা মিজারেবল’। অনেক দিন রাত জেগে বই শেষ করতাম, কোনোদিন শেষ করতাম দুটো বই। তখন আমার বয়স ১১-১২ বছর। হয়তো এইভাবে আমি হয়ে গেলাম ইনসোমনিয়াক। সেই রোগ বয়ে বেড়ালাম ১৫-১৬ বছর।
আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন পড়ে ফেলি নজিবর রহমান সাহিত্যরত্বের ‘আনোয়ারা’ উপন্যাস এইটা ছিল আমার জীবনে পড়া প্রথম প্রেমের উপন্যাস। উপন্যাসে পড়া একটা দৃশ্য এখনো চোখে লেগে আছে। অসুস্থ হয়ে আনোয়ারাদের বাড়িতে আশ্রিত নূর ইসলাম তার সেবাযত্নে সুস্থ হয়, কিন্তু আনোয়ারার প্রেমে পড়ে যায়। ফলে তাদের বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় তার একগোছা চুল চুরি করে কেটে নেয় স্মৃতি হিসেবে। বইটা বাবার কালেকশন থেকে চুরি করে পড়তে হয়েছে। কারণ তখন বাড়িতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ‘আউটবই’ পড়া নিষেধ ছিল। তাই এই বইটা পড়েছি অনেক কষ্টে দীর্ঘদিন ধরে।
ছোটোবেলায় আমার নিয়মিত পাঠ্য তালিকায় ছিল জীবনানন্দ দাশের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, মহাভারতের সারানুবাদ, কুরান শরিফের অনুবাদ, বোখারি শরিফ, নেয়ামুল কুরান, খাব-এ-তাবির, চলন্তিকা, গীতবিতান, সঞ্চয়িতা, সঞ্চিতা, পঞ্জিকা, রামকৃষ্ণ কথামৃত ইত্যাদি। আমার মনে আছে কলেজ সেকেন্ড ইয়ার পর্যন্ত আমি একটা খাতায় কটা বই পড়েছি তার হিসেব রাখতাম। যতদূর মনে পড়ে সেই হিসেব মতে প্রায় আঠারোশো বই আমি পড়ে ফেলেছিলাম।
ক্লাস সিক্সের বছর বইয়ের দোকানের পেছনে বসে পড়েছি অনেক সিরিজ বই ওয়েস্টার্ন, মাসুদ রানা, তিন গোয়েন্দা, কুয়াশা, দস্যু বনহুর, সাইমুম ইত্যাদি। আর পড়েছি অনেক লেখকের বই যথা বেদুঈন সামাদ, আকবর হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক, হুমায়ূন আহমেদ প্রমুখের বই। একই সময় সেলিনা হোসেনের ‘গায়ত্রীসন্ধ্যা’ আর সমরেশ বসুর ‘প্রজাপতি’ও পড়ি। কিন্তু আমাকে আকবর হোসেন আকর্ষণ করেছিলেন। তার উপন্যাস পড়ার সময় আমার মনে হতো পুরোনো দিনের শাদাকালো বাঙলা সিনেমা দেখছি। কাসেম বিন আবুবাকারও আমার প্রিয় উপন্যাসিক ছিল যখন সিক্স-সেভেনে পড়ি।
আমাদের শহরতলির বইয়ের দোকান আদর্শ লাইব্রেরিতে খাতা কলম ইত্যাদি কেনার বাইরেও নিয়মিত যাওয়া-আসা শুরু করি প্রাইমারি ইশকুলে পড়ার সময়। এবং উচা উচা বুক শেল্ফের পেছনে মেঝেতে বসে ইশকুল ফাঁকি দিয়ে বইপড়া শুরু করি, ছাত্রবন্ধু আর আদর্শ লাইব্রেরির বইয়ের তাকের পেছনে ফাঁকা জায়গা ছিল, ওখানে বসে প্রায় দিন ইশকুল ফাঁকি দিয়ে কাসেম বিন আবু বাকারের বই পড়তাম। এইভাবে আমি তার টানা ৪০ টা উপন্যাস পড়েছি। পরে ওইগুলি সংগ্রহও করেছিলাম। এমডি মুরাদের ‘ঘুমন্ত গোলাপ’-এর পরই কাসেম বিন আবু বাকারের ‘ফুটন্ত গোলাপ’ বাজারে আসে। তার মতো আরও কয়েকজন লিখতে আসেন তখন তার মধ্যে আব্দুস সালাম মিতুল অন্যতম। বিষয়বস্তু মূলত ইসলামি সামাজিক প্রেম। এই লেখকদের বেশিরভাগই মনে হতো জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। আরেফা আহসান রত্না নামেও একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন। তার লেখাও এই ধারার। কাসেম বিন আবু বাকারের ‘আধুনিকা’ নামের উপন্যাসে ইসলামি প্রেমের কথা এখনো খানিকটা। রোমেনা আফাজের পর কাসেম বিন আবুবাকারের উত্থান ঘটে বাঙলা সাহিত্যে। এইসব বই থেকে আমাদের সিনেমার স্ক্রিপ্ট বানালে আমাদের সিনেমার চেহারা পালটে যেত।
কলেজ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ে একদিন অস্কার ওয়াইল্ডের ‘পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে’র অনুবাদ পড়ে ডালিম ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকতাম সারাদিন। মা ডাক দিত, ‘ভাত খেতে আয়’। আমি ভাতের প্লেইট নিয়ে ডালিমগাছের সামনে বসে থাকি। এই রকম আরও অনেক বই পড়ে অনেক অদ্ভুত আর উদ্ভট আচরণ করেছি। আমার কোনো ইনটেশন ছিল না। যেমন জি এইচ হাবীবের অনুবাদে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের ‘নিঃসঙ্গতার একশো বছর’ পড়ার পর হাঁটতে হাঁটতে কোনো নর্দমা, খাল দেখলেই মনে হতো হোসে আর্কাদিওর রক্ত গড়িয়ে আসছে। আমার এমন হতো। কেন হতো জানি না। এখন চাইলেই বইটই ঘেঁটে কারণ বের করে ফেলতে পারব। কিন্তু ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে না আমার টকটকে লাল ডালিম ফুল হারিয়ে যাক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চতুষ্কোণ’ পড়ে খুব ইচ্ছে করত রাজকুমার হতে। প্রিয় বই ছিল বুদ্ধদেব বসুর ‘রাতভরে বৃষ্টি’। তারপর আরেকটা প্রিয় বইয়ের স্মৃতি এখনো নিজের মধ্যে লালন করি, ফিওদর দস্তয়ভস্কির ‘অপরাধ ও শাস্তি’। আর নিজেকে রাস্কলনিকভ ভাবি এখনো, ভাবি প্রেম অপেক্ষা শাস্তিই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ। তারপর সলবেলোর ‘হেন্ডারসন দ্য রেইন কিং’ সৈয়দ শামসুল হকের অনুবাদে ‘শ্রাবণরাজা’ পড়ে তার মধ্যে অনেকদিন ডুবে ছিলাম। আর এর আগে সৈয়দ হকের একটা উপন্যাস পড়েছিলাম, নাম ‘খেলারাম খেলে যা’। উপন্যাসের একটা চরিত্রের নাম ছিল জাহেদা। যাকে নিয়ে বাবর আলী নামে এক মাঝবয়েসি আপাত লম্পট এবং মানসিক সমস্যায় জরজর এক লোক উত্তরবঙ্গের দিকে কোথায় বেড়াতে গিয়ে একটা গেস্টহাউজে ওঠে। এবং জাহেদাকে রাতভর যৌনপীড়ন করে। জাহেদা ঘুমুতে পারে না।
আমাদের ছোটোবেলায় একটা বই ছিল, বইয়ের নাম ‘সেলিনার গোপনকথা’। মলাটে খুব সুন্দর একটা মেয়ের থ্রি কোয়ার্টার প্রোফাইল ছবি। আমার মনে হতে মলাটের মেয়েটাই সেলিনা আপা। বইটা বিয়ের উপহার হিসেবে বেশি চলত। বইয়ের প্রথম পেজে লেখা থাকত বিয়ের প্রীতি উপহার। বইটা বিয়ের উপহার হিসেবে বাড়িতে এলেও, বাড়ির কোথাও দেখা যেত না, বাড়িতেও গোপনে লুকিয়ে থাকত। তখনো আমাদের বাড়িতে কোনো বিয়ে হয়নি, মানে ভাইয়ের বিয়ের বয়সই হয়নি। এই বইটার কথা জেনেছি আত্মীয়স্বজন আর লোকজনের বাড়িতে দেখে। একবার পাড়ার এক ভাবির হাতে দেখি, তিনি যখন বইটা পড়ছিলেন, বাড়িতে কেউ ছিল না। আমি কী একটা কাজে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে বইটা আলগোছে লুকিয়ে ফেলে। লুকানোর আগেই মলাট দেখে ফেলেছিলাম। সেলিনার কী এমন গোপন কথা! এই ভাবনা আমার মাথার ভিতর শৈশবে হিজিবিজি হিজিবিজি লাগিয়ে দিত। কল্পনা-জল্পনার শেষ থাকত না। ফোর-ফাইভে যখন পড়ি তখন বইটাকে আদর্শ লাইব্রেরিতে দেখতে পাই। ওখানেও বইটা আমার নাগালের বাইরে, সব থেকে ওপরের তাকে। একদিন সকালে লাইব্রেরির নাসিরভাই আমাকে কয়েক মিনিটের জন্য রেখে বাইরে কোথাও গেলেন। আমি টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বইটা পেড়ে আনি আর শেল্ফের পেছনে বইয়ের খাঁজে গুঁজে রাখি। তারপর নাসিরভাই এলে পেছনে গিয়ে বইটা খুলে বসি। ওইদিন বিকেলের মধ্যেই সেলিনা খালা তার সব গোপন কথা আমাকে বলে দেন, খুব যত্ন করে। জেনে মনে হল এই কথা! কারণ অবশ্য এইসব গোপন এর আগেও আমি অল্পবিস্তর জানতাম। তবে সেলিনা খালার কাছে আরও বেশি করে জেনে মনে হল আমার উচ্চতা কয়েক ইঞ্চি বেড়ে গেছে, রক্তের মধ্যে কেমন এক উত্তাপ নিয়ে সেইদিন আমি ফিরেছিলাম।
১৯৯০ সালে আমি ফোরে পড়ি। সেই বছর প্রথম হাতে আসে ‘মালাইকাইটের ঝাপি’ নামের একটা বই, তারপর ‘রুশদেশের উপকথা’। অল্পদিনের ব্যবধানে এই দুইটা বই আমি বাসায় এনে পড়তে পারি। তারপর আরও বই। আমার মেজো আপার কলেজের ক্লাসমেইট বন্ধু ছিল সাথীভাই। সাথী এলাহী রিপু। ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। থাকতেন খেলাঘরের অফিসে বা সেই অফিসের সঙ্গে লাগানো একটা ঘরে। খেলাঘরের দায়িত্বও সম্ভবত তার হাতেই ছিল। আমি ওই অর্থে নিয়মিত খেলাঘর করতাম সেটা বলা যায় না। তবে সাথীভাই যেহেতু মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসতেন তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। আমি নিজেও বেশ কয়েকবার গিয়েছি। মূলত বইয়ের টানে, আর মাঝে ছবি আঁকার আসর বসলে ছবি আঁকার টানে। খেলাঘর ছিল আমাদের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে নদীর ওপারে, শিকলঘাটা নামে একটা গ্রামে। আমাদের কলেজটাও ওইখানেই। আমি ব্রিজ পার হয়ে নদী মাতামুহুরীর পাড় ধরে সারি সারি শিমুলগাছের তলা দিয়ে স-মিলগুলির পেছন দিয়ে ছোটো ছোটো পা ফেলে কোনোদিন বিকেলে বা ছুটির দিনে খেলাঘরে চলে যেতাম। শ্রেণিহীন দেশের বই প্রথম আমি খেলাঘরের আসরেই হাতে পাই। শ্রেণিহীন দেশ মানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যে-দেশে একদিন সমাজতন্ত্র ছিল। সমাজতন্ত্রের ব্যাপার মোটামুটি বুঝতে আমার কয়েক বছর লেগে যায়।
আমার সিক্সের বছল হাই ইশকুলে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই আউটবই পড়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে একটা ছেলের সঙ্গে আমার ভাব হয়। ছেলেটার নাম রাসেল। পুরা নাম একেএম জামীর উদ্দিন রাসেল। রাসেল আমার সঙ্গে বইয়ের গল্প করে। তার বাড়িতে অনেক বই। আমার বাড়িতেও বই ছিল। আমি আর রাসেল বই দেওয়া-নেওয়া করতাম। রাসেলের কাছ থেকেই বেশি নিতাম। একদিন রাসেল আমার সঙ্গে ‘ইস্পাত’-এর গল্প করল। নিকোলাই অস্ত্রভস্কির ইস্পাত। দুইখণ্ডের উপন্যাস। নায়কের নাম পাভেল। বইটা রাসেলের এতই প্রিয় ছিল যে রাসেল ওই বয়সেই তার কাল্পনিক কোনো প্রেমিকা কিংবা যে-মেয়েটা তার ভালো লাগত সেই মেয়ের নাম দিয়েছিল ‘ইস্পাত’। সে ইস্পাত নামটা লিখে লিখে তার খাতা বই ভরিয়ে ফেলত। একজন অন্ধ লেখক একটা উপন্যাস লিখে পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিলো সেই উপন্যাস না পড়ে আমি কেমন করে থাকি এই বোধ আমাকে সেই ১১ বছর বয়সে তীব্রভাবে তাড়া করল। খুব সম্ভবত সেইদিনই প্রথম আমি রাসেলের সঙ্গে তার বাড়ি চলে গেলাম বইটা নেবার জন্য। রিকশা করে গেলাম। রাসেল আমাকে প্রথম-খণ্ড পড়তে দিলো। এটা ফেরত দিলে আরেকটা দেবে। আমি রাত জেগে পড়ে, পরেরদিন দুপুরের আগেই পড়ে ফেললাম। পরের দিন শুক্রবার ছিল। আমি ইস্পাত প্রথম-খণ্ড হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিনামারা চলে গেলাম রাসেলদের বাড়িতে। বিনামারা আমাদের গ্রাম থেতে তিন গ্রাম পরে। আমাদের বাড়ি থেকে রাসেলের বাড়ির দূরত্ব ছিল প্রায় আড়াই কিলোমিটার। আসা-যাওয়ায় ৫ কিলোমিটার। এই ৫ কিলোমিটার আমাকে প্রায় প্রতি শুক্রবারেই হাঁটতে হতো বইয়ের জন্য। রাসেলের বড়োভাই বামরাজনীতি করতেন, ফলে তাদের বাড়িতে মস্কোর রাদুগা আর প্রগতি প্রকাশনের অনেক বই ছিল। রাসেলের কাছ থেকে নিয়েই আমি প্রথম প্রগতি প্রকাশনের ‘সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ’ সিরিজিরে বইগুলি পড়ি আমার সাত ক্লাসের বছর। প্রথম পড়ি ‘দর্শন কী’ বইটা।
বটতলি স্টেশনের উলটাদিকে দোতলায় ছিল অমর বইঘর। এছাড়া চট্টগ্রাম শহরের আরও অনেক ফুটপাথ ছিল আমার স্বপ্নের বইগুলি কেনার জায়গা। এক এক করে কিনে পড়ে ফেলি তলস্তয়, দস্তইয়েফস্কি, চেখভ-সহ অনেক লেখকের গল্প-উপন্যাসসহ নানা রকম বিষয়ের ওপর লেখা বেশ কয়েকটা বইপত্র। তখন আমার খুবই প্রিয় একটা বই ছিল ইভান তুর্গেনেভের ‘মুমু’।
আমার ক্লাস এইটের বছর গ্রাম থেকে আমি চট্টগ্রাম শহরের সরকারি মুসলিম হাই ইশকুলে টিসি নিয়ে চলে যাই। হোস্টেলে থাকা শুরু করি। আমাদের ইশকুলের গেইট দিয়ে বের হয়ে রাস্তা পার হলেই কোর্ট বিল্ডিং-এর সামনের ফুটপাথ। এই ফুটপাথেই খুবই সস্তায় মানে ১০/২০ টাকায় পেয়ে যাই প্রগতি ও রাদুগা প্রকাশনের বাঙলায় অনুবাদিত অনেক বই। এর বাইরে স্টেশনরোডে নূপুর মার্কেটের পুরোনো বইয়ের দোকানগুলি আর বটতলি স্টেশনের উলটাদিকে দোতলায় ছিল অমর বইঘর। এছাড়া চট্টগ্রাম শহরের আরও অনেক ফুটপাথ ছিল আমার স্বপ্নের বইগুলি কেনার জায়গা। এক এক করে কিনে পড়ে ফেলি তলস্তয়, দস্তইয়েফস্কি, চেখভ-সহ অনেক লেখকের গল্প-উপন্যাসসহ নানা রকম বিষয়ের ওপর লেখা বেশ কয়েকটা বইপত্র। তখন আমার খুবই প্রিয় একটা বই ছিল ইভান তুর্গেনেভের ‘মুমু’। রাশিয়ান এইসব বইয়ের শেষে লেখা থাকত, ‘পাঠকদের প্রতি: ‘বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব। আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।’ তারপর ‘আমাদের ঠিকানা: রাদুগা প্রকাশন, ১৭ জুবোভ্স্কি বুলভার, মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন।’ কিংবা ‘প্রগতি প্রকাশন, ২১ জুবোভ্স্কি বুলভার, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন।’ তারপর কয়েকটা শাদা পৃষ্ঠা থাকত যেন পাঠক নোট রাখতে পারে।
এই তো গেল রাশিয়ান বইয়ের কথা। এর বাইরে আমার খাদ্য ছিল নয়াচীনের ফিনিক্স সাহিত্য প্রকাশনীর বই। এইগুলিও সব আমাদের দেশে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আসত। আর যারা বিনামূল্যে পেত তাদের কেউ কেউ ফুটপাথে সের দরে বিক্রি করে দিত, তারপর আমরা কিনতে পেতাম। তাই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কত বই যে আমার কাছে ছিল! আমি ভার্সিটিতে পড়ার সময়ও অনেক বই কিনেছি। বাড়িতে যেইসব বই ছিল তাদের প্রায় সবই অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে বন্যা, ইঁদুর আর উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে যেইসব বই ছিল তার মধ্য থেকেও লোকজন পড়তে নিয়ে ফেরত দেয়নি এমন হয়েছে। তারপরও রাশিয়ান প্রিন্টের বাইশতেইশটা বই আছে, এইই সান্ত¡না থেকেই এইসব স্মৃতির ফাঁদ বসালাম।
বয়োঃসন্ধির সময় আমার সব থেকে প্রিয় লেখক ছিলেন রসময় গুপ্ত। ইনি একজন গোপন-লেখক বা অনেক লেখকের সম্মিলিত রূপ ছিলেন। ইনি লিখতেন পাতলা সব বই বা পুস্তিকা যেইগুলি বাঙলা চটি বই নামেও পরিচিত ছিল। কিছু ছিল চাররং সচিত্র। এইগুলিতে মূলত নারীপুরুষের যৌনসঙ্গমের বর্ণনা থাকত ছোটো ছোটো কাহিনিতে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ ব্যাসের নামে যেমন কালে কালে অজস্র কবি মহাভারতকে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনই রসময় গুপ্তের নামেও অনেক গুপ্ত-লেখক তার চটিসম্রাজ্যকে ভরপুর করেছেন। ওইসব পড়তাম রাসেলের কাছ থেকে নিয়ে। তার বাড়ির বসার ঘরের ওয়ালমেটের পেছনে গুঁজে রাখা এইসব পরম পুস্তিকা আমি আবিস্কার করেছিলাম যখন প্রাইমারি ইশকুল শেষ করে সিক্সে ভর্তি হই।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গল্পগুচ্ছ’ ছোটোবেলায় আমার খুবই প্রিয় বইগুলির একটি ছিল। আমি হৈমন্তী আর সমাপ্তির প্রেমে পড়েছিলাম। অনেকদিন পর শাস্তি গল্পটা আবার পড়ে চন্দরাকে নতুনভাবে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। তখন চন্দরা রাগ-ক্ষোভের ওপরে চলে গেছে, তখন আর রাগ কিংবা প্রতিবাদ করে কোনো লাভও নেই। রাগ থাকলে সে ভাসুরের দোষ নিজের মাথায় নিত না, কখনো। তার বয়স ১৭ কিংবা ১৮। সে স্বামীকে ভালোবাসত। সেই স্বামী যখন বলতে পারে বউ হারালে বউ পাব, কিন্তু ভাই হারালে ভাই পাব না। ছিদামের এই স্বার্থপর বাক্য শুনে সে প্রথমে পাথর হয়, পরে তা অভিমানে রূপ নেয়, এবং আত্মবিধ্বংসী হয়েই খুনের দায় নিজের ঘাড়ে নেয়। চন্দরার ‘মরণ’ শব্দটি উচ্চারণের ভঙ্গি গল্প পড়ে আমি যা কল্পনা করি তাতে মনে হয় এই শব্দে লুকিয়ে ছিল অভিমান। আর তা তার অসহায় স্বামীর প্রতি যে ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বউকে জলাঞ্জলি দেয়। আর এই অভিমান থেকেই চন্দরা সবখানে বলে খুনটা সে নিজেই করেছে।
নাইন-টেনে সমরেশ মজুমদারের ‘সাতকাহন’ পড়তে পড়তে দীপাবলিকে নারীই মনে হয়েছে। সে নিজের চেষ্টায় আইসিএস পাশ করার পর, সরকারের প্রশাসনিক পদে দীর্ঘদিন চাকরি করার করে নানামুখি সমস্যা ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে পথ চলতে চলতে একসময় হোছট খেয়ে পড়ে। আর সব ছেড়ে ঠাকুর মা মনোরমার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে, তখন তাকে আমার নারী মনে হয়েছে। আরেকটা বই হুমায়ুন আজাদের ‘নারী’। যার বই পড়ার অভ্যাস আছে সে কি বইটার মতো সহজ একটা বই পড়তে পারে না? আর বইটিকে আমি খুবি গুরুত্বপূর্ণ বই মনে করি, সিমোন দ্য বোভোয়ারের ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’-এর পর। এবং এই বইটিকে আমি প্রতিটি নারী, যে নারী হয়ে জন্ম নেয় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে তাদের জন্য অবশ্য পাঠ্য করি। কেননা এটি তার নিজেকে চিনতে শেখায়, তার অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। নারী নয়, মানুষ হিসেবে তার ঔচিত্যবোধকে জাগ্রত করে। তার ‘আমার অবিশ্বাস’ আরেকটা বই আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। জীবনানন্দ দাশের ‘মাল্যবান’ উপন্যাস পড়ে মনে হয়েছিল উৎপলা চাইলেই মাল্যবানের চোখের আড়ালে সমরেশকে নিতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি, সে যা করেছে সামনেই করেছে। এটা তার সততা নয়, এটা নিষ্ঠুরতা। এবং ইচ্ছাকৃত। সে আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর নারী হতে চেয়েছিল কি না আমি জানি না, মাল্যবানও জানত না।
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগ পর্যন্ত আমি কয়েক হাজার বই পড়েছি, যখন যা পেয়েছি, তাই-ই পড়েছি, বাছবিচার করিনি। কোনো কিছুই বিফলে যায় না। তবে ছোটোবেলা থেকেই যদি ধরে ধরে কাজটা করতে পারতাম আরও কিছু প্রয়োজনীয় অনেক বই আগে থেকে পড়া হয়ে যেত, ফলে আরও সময় পেতাম আরও ভালো কিছু বই পড়বার। আমার ওইসব নিয়ে আফসোস নেই। সেশনজটের কারণে বাড়তি ৪ বছর আমার জন্য আশীর্বাদ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমি যেটা করতে পেরেছি, সব বেছে বেছে বই পড়তে পেরেছি। কারণ এখানে সেই সুযোগ ছিল পড়ুয়া বন্ধুবান্ধব ছিল, প্রিয় শিক্ষকরা ছিলেন। তাদের সঙ্গে পড়াশোনা নিয়ে বলার সুযোগ ছিল। ফলে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ বছরে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো বইগুলির মধ্য থেকে অনেক বই পড়তে পেরেছি। এবং আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি বই আমি পড়েছি সেই সময়গুলিতে। ওরিয়েন্টাল আর ওয়েস্টার্ন অ্যাস্থেথিক্স, আর্টের মতবাদিক আন্দোলনগুলি আমাদের সিলেবাসেই ছিল। তারপর মানুষের ইতিহাস, পুরাণ, পৃথিবীর ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস, দর্শনের ইতিহাস, রাজনীতির ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান। নানা থিউরি, মডার্ন থিউরিগুলি, ফ্রয়েড, গুস্তাভ ইয়ুং, মর্গান, লেভি স্ত্রাউস, ভাষাতত্ত্ব, ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর, নোয়াম চমস্কি, ফ্রাঙ্কফুট স্কুল অব থট, অ্যান্থনিও গ্রামশি, নিৎশে, ওরিয়েন্টালিজম, উত্তর-কাঠামোবাদ, ডিকনস্ট্রাকশন থিউরি, ফেমিনিস্ট থিউরি, কুইয়ার থিউরির জুডিথ বাটলার পর্যন্ত ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাইমারি জ্ঞান আমি সেই কবছরেই পেয়েছি। ফুকোর ‘যৌনতার ইতিহাসের ভ‚মিকা’ আমরা ফটোকপি করে পড়েছি ওইসময়। জিএইচ হাবীব স্যার অনুবাদ করলেন রোঁলা বার্থের ‘রচয়িতার মৃত্যু’। আর নিজামভাইয়ের বাসায় তো প্রয়োজনীয় সব বইয়ের পাহাড় ছিল। আমার ছোটো সাইড ব্যাগে সবসময় কোনো কোনো বই থাকত। আমাদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ছিল প্রায় ৩ লাখ বই। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সেমিনার লাইব্রেরিতেই ছিল হাজার পাঁচেক বই। লাইব্রেরিতে বসে ওই অর্থে আমি বই পড়িনি। তবে অনেক বই ঘাটাঘাটি করেছি, খুলে খুলে দেখেছি। আমার এইই করতেই ভালো লাগত। কখনো কোনো বই দরকার মনে করলে ফটোকপি করে নিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরগুলিতে আমি সব পড়ে ফেলেছিলাম, সব জ্ঞান বাগিয়ে নিয়েছিলাম, তা কিন্তু কখনোই নয়। ওই সময়গুলিতে আমি প্রাইমারি সূত্রগুলি ধরেছিলাম, কীভাবে কী পড়তে হবে, কতটা পড়তে হবে ইত্যাকার বিষয়।
২০১০ সালের পর থেকে খুবই কম বইপত্র পড়তে পারি, নানা কাজে কর্মে জড়িয়ে গেছি, অভ্যাসও প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, তারপরও প্রতিদিন একপৃষ্ঠা, এক প্যারাগ্রাফ বা কোনো বই থেকে একটা কবিতা হলেও পড়া হয়। ১০ সালের আগে যা পড়েছিলাম তাও কিছু মনে নেই। আমি যা পড়ি তার প্রায় সবই ভুলে যাই। তবে তার নির্যাসটা নিশ্চয়ই মাথার ভেতর থেকে যায়, যা সকল সময় কথা বলার, লেখার, বোঝার জ্বালানি হিসেবে কাজ করে।
এতক্ষণ তো কেবল বললাম বই পড়বার কথা। এখন একটু পড়া আর না পড়া নিয়ে দুটো কথা বলি।
বই না পড়েও যথার্থ মানুষ হওয়া যায়। বই পড়েন নাই এমন যথাঅর্থে মানুষও পৃথিবীতে ছিলেন, আছেন আর থাকবেন। আবার বই পড়েও অনেকে মানুষ হতে পারেন না। পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো অপরাধীর মধ্যেও বড়ো বড়ো বইপড়ুয়া ছিলেন। এমনকি মূর্খও ছিলেন, আছেন। নিরক্ষর কিংবা অশিক্ষিত মাত্রই মূর্খ নয়। মূর্খ যে, সে দশটা পিএইচডি কিংবা দশ হাজার বই পড়লেও মূর্খই থেকে যায়।
মানুষকে যথাঅর্থে মানবিক মানুষ করে মানুষের বোধবুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান, সর্বোপরি জ্ঞান। আর মূলত স্বজ্ঞাই জ্ঞান লাভের পূর্বশর্ত। স্বজ্ঞা না থাকলে বই পড়েও কোনো জ্ঞান লাভ হয় না। বড়োজোর সাধারণ জ্ঞান লাভ হতে পারে। সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা পাশের জন্য লাগে, আর কোনো কাজে লাগে না। স্বজ্ঞা হচ্ছে এক প্রকার সহজাত প্রতিভা। প্রতিভা প্রকট হয় তাকে পরতে পরতে খুলে দেবার মধ্য দিয়ে। ছুরিকে যেমন ফেলে রাখলে ছুরির গায়ে জং ধরে যায়, কিছুই কাটা যায় না, তেমনই প্রতিভাকেও খুলে না দিলে অচল হয়ে পড়ে রয়। প্রতিভাকে এমনি এমনি খোলা যায় না, তার জন্যও চাবি লাগে। আর সেই চাবির নামই বই।

- মূলত লেখেন ও আঁকেন। জন্ম : ২৪ আগস্ট ১৯৮১, চকরিয়া, কক্সবাজার, বাঙলাদেশ। পড়াশোনা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলায় স্নাতকোত্তর। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৮টি।