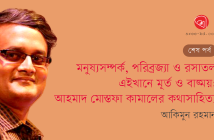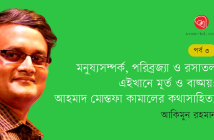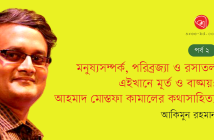খ্রিষ্টের রক্ত তখনও করবী ফুলের মতো লাল হয়ে জ্বলে ওঠেনি। মৃত্যু তার ঊরু বিস্তার করেছে লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, কোলকাতা অথবা ঢাকায়। কবিতার কয়েকটি পঙক্তিতে লোরকা নিজের ভবিতব্য দেখতে পেলেন স্পেনে— তখন ১৯৪২ সাল; রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থানের পথে পথে পড়ে আছে সাহিত্যের নৈশবিজ্ঞপ্তি, ইতিহাস প্রবেশ করছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নিদারুণ মন্তাজে। আর কিছুদিন বাদেই ইউরোপের ভূগোল থেকে মুছে যাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন— এদিকে পূর্ব বাংলা জ্বলছে, ভারতবর্ষে দেখা দিচ্ছে এশিয়ার মুক্তিসূর্য— অথচ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে মানুষ, জ্বলছে কোলকাতা, নোয়াখালি, পাঞ্জাব আর বিহার— প্রাচ্যে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছেন মাহাত্মা গান্ধী— আবহে বেজে চলছে রবিঠাকুরের ‘একলা চলো রে…’ আর পাশ্চাত্যে আলবেয়ার কাম্যু লিখে চলেছেন The Rebel (L’Homme révolté, 1951)— ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ছে প্রথাগত বিপ্লব ব্যবস্থায় মানুষের চিরায়ত বিশ্বাস। মানুষের ইতিহাস যদি মনীষার ক্রম-উদ্বোধনের ইতিবৃত্ত হয়, তবে সংস্কৃতির তত্ত্বায়নটুকুই প্রমাণ করে উনিশ ও কুড়ি শতক কেনো প্রগতির অনন্য সম্পদ। এই দুটো আলোকিত শতাব্দী জুড়ে মুহুর্মুহু উড়েছে রাজনৈতিক মতবাদের অবিনশ্বর ভ্রূণসমগ্রের ফানুস— তাদের কিছু ব্যাপ্তি লাভ করেছে, কিছুবা মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রত্যক্ষায়নের দিকে। কিন্তু শতাব্দীর মার্জিনে তোলা ছিল সবই; বস্তুত এই দুটি শতক প্রণয়কূজন ও বাজারের কোলাহলকে যুগপৎ ধারণ করে গেছে।
সাহিত্য ও রাজনীতির দাম্পত্য সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই। তবে এই সরল বাক্য আদতে সরল নয়— কেননা, মানুষের চিন্তার স্থাপত্যে সাহিত্য ও রাজনীতির সংজ্ঞায়ন যুগে যুগেই ভিন্ন।
সাহিত্য ও রাজনীতির দাম্পত্য সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই। তবে এই সরল বাক্য আদতে সরল নয়— কেননা, মানুষের চিন্তার স্থাপত্যে সাহিত্য ও রাজনীতির সংজ্ঞায়ন যুগে যুগেই ভিন্ন। ‘সাহিত্যে রাজনীতি’, ‘রাজনীতির সাহিত্য’ বা ‘রাজনৈতিক সাহিত্য’ বললে আলোচনার বিষয় ও বাস্তবতাকে খানিক ছোটো করে আনা যায় বটে; কিন্তু তাতে আলোচনাটি ঠিকঠাক মতো হয় না বলেই আমি মনে করি। কারণ, সভ্যতার আদি পর্বে মানুষ মূলত তার চিন্তার সূত্রে শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি ইত্যাদির অবয়ব দান করেছে। সুতরাং মানুষের চিন্তার বিবর্তনকে যদি প্রেক্ষণে রাখা যায় তবে এটা স্পষ্ট হয় যে, মানুষ মূলত তার চিন্তার চিৎকারে পক্ষ অবলম্বন করেছে বা পক্ষ পাল্টেছে। এই বিবর্তনের ধারা আবার সভ্যতার বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ভিন্ন। প্রাচীন গ্রীক, রোমান বা ভারতে মানুষের চিন্তার যে অবমুক্তি ঘটেছে তার সঙ্গে দর্শনের সম্যক সম্পর্ক বিরাজমান। এখান থেকে রাজনীতি, এমনকি সাহিত্যেরও উৎস অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ফলে উনিশ বা কুড়ি শতকে মানুষের সৃষ্টিমুখরতার যে দ্বান্দ্বিক ও দিগ্বিজয়ী উত্থান আমরা দেখতে পাই, তাকে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের মতো ছাঁচে ফেলা যায় না। শিল্পায়ন ও নগরায়নের জায়মান নাগরিকতা আমাদের নিকটবর্তী দুটি শতককে বিস্ময়করভাবে প্রভাবিত ও প্রতারিত করেছে। ফলে তার সমীকরণ যতটা জটিল, ততটাই স্পষ্ট। কেবল রাজনীতিকে ধরে আলোচনা করলে এই জট সহজে খুলবার নয়; বরং রাজনৈতিক মতবাদ এক্ষেত্রে আমাদের একটি উৎসমুখ দেখাতে পারে। আরেকটু গভীরে গেলে আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারস্থ হতে হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধারাতেই আলোচ্য বিষয়ের তদন্ত ও নবসমীক্ষা সম্ভব।
রাজনৈতিক দর্শন বা রূপান্তরের রহস্য
রাজনৈতিক জ্ঞানের ব্যাপারে মূল তাত্ত্বিক দায়টা হলো রাজনৈতিক দর্শনের। এ হলো রাজনীতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক প্রস্তাবাদির নির্দিষ্ট এক-একটি সমষ্টি। মানুষের আত্মস্থ জ্ঞান প্রণালীর সঙ্গে মূল্যবিদ্যার (axiology) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগে তৈরি হয় দর্শনের নন্দনতত্ত্ব। যুগের সামাজিক সম্পর্ক বিবেচনায় এই নন্দনতত্ত্বের কিছুটা টিকে থাকে আবার কিছুটা ঝরে গেলেও একেবারে বিলীন হয়ে যায় না। এই দর্শনের ভিত্তিভূমি থেকেই জন্ম নেয় সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক জ্ঞান এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক মতবাদ। এতে পুঞ্জীভূতরূপে প্রকাশ পায় রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য, প্রবণতা, আদর্শ এবং নির্দিষ্ট এক-একটি সামাজিক অবস্থান এবং তার মূল্যায়ন। রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাস কালানুক্রমিক হলেও রাজনৈতিক মতবাদ ভৌগলিকতাতেও ব্যাপ্ত। এর কারণ হলো রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটেছে সুনির্দিষ্ট কিছু সামাজিক-নরকৌলিক জনগোষ্ঠীর ভূমিতে, পরস্পর থেকে যথেষ্ট পৃথক সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক অঞ্চলের পরিসীমার মধ্যে। পশ্চিমের পণ্ডিতরা দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক দর্শনের যে বিবর্তনকে ইউরোপকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রাজনৈতিক মতবাদে পরিণত করে গেছেন, মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ তা অগ্রাহ্য করেছে।
রাজনৈতিক তত্ত্ব বা মতবাদ বস্তুত নির্মাণের একটি উপায় মাত্র— এতে ঘনীভূত জ্ঞানের সারার্থ প্রতিফলিত হয় বাস্তবতা অনুযায়ী। কিন্তু দর্শন তার অনন্যতার ছাপেই স্বকীয় এবং গভীরভাবে উপলব্ধ। ফলে মতবাদ বা তত্ত্বের বদল ঘটতে পারে; কিন্তু দর্শনের উপস্থিতি থেকে যায়— সেটা অমানবিক দর্শন হলেও থেকে যায়। এ কারণেই হিটলার বা মুসোলিনীর রাজনৈতিক মতবাদের চর্চা বিশ্বজুড়ে নিন্দিত হলেও জাতীয়তাবাদী সমাজতত্ত্ব বা নীটশের দর্শনচর্চা সারা পৃথিবীতেই অব্যাহত আছে।
এখন প্রশ্ন হলো— সাহিত্য তুমি কোন দিকে চলো? দর্শন না রাজনৈতিক মতবাদের পথে? এই একটি প্রশ্নের মাধ্যমেই বিশ্ব সাহিত্যের ধারা উপধারাগুলোতে কিছু সংশয়বাদী বক্তব্য সেঁটে দেয়া যেতে পারে। কারণ আমরা চাইলেও আলোচনাটি আর সরলরেখায় এগুবে না। আমাদের মনে পড়ে যাবে ন্যুট হ্যামসনের কথা— শারদীয় নক্ষত্রের তলে শুয়ে থাকা এই বিষণ্ন কবিকেই আমরা খুঁজে পাই হিটলার আর গোয়েবলসের দরবারে। নরওয়ের ছোট্ট গ্রামে আসা এক আগুন্তকের গল্পে যিনি মথিত করে তুলেছিলেন গোটা বিশ শতকের কথাসাহিত্যকে, তাঁর হাতেই আমরা দেখতে পাই হলোকাস্টের রক্ত। যে কলমে তিনি Mysteries (Mysterier, 1892) লিখেছিলেন, সে কলমেই হিটলারকে অভিহিত করলেন a warrior for mankind শিরোনামে। কিংবা The Spirit of Romance (1910)-এ কবির কলমে প্রায় কবিতার মতোই সাহিত্যের খুঁটিনাটি পড়তে পড়তে হঠাৎই ইতিহাসের ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠি। আমাদের মন আওড়ে চলে অনন্ত পয়ারের কথকতা “And the days are not full enough/ and the nights are not full enough…” অথচ আমাদের মগজ আর বিবেক এসে ধাক্কা খায় রেডিও রোমের সেই বেতার তরঙ্গে— Ezra Pound says, “You let in the Jew and the Jew rotted your Empire, and you yourselves are doomed by the Jew”.
আমাদের অনুভূতি প্রতারিত হয়। ভালোলাগার সারবত্তা আটকে পড়ে অপরাধবোধের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। বার্নাড শ’র Apple Cart (1928) পড়তে পড়তে আমরা বিস্মিত হই এই ভেবে যে, এই মানুষটিই কি না নাটকটি লেখার মাত্র পাঁচ বছর পরেই ইউক্রেনে স্তালিনের চালানো ভয়াবহ জেনোসাইডকে সমর্থন করেছিলেন? জন স্টেইনব্যাকের শেষ উপন্যাস The Winter of our Discontent (1961) পড়লে আজও ইথান এলেনের জন্য আমাদের বিষাদ জাগে, অথচ এই স্টেইনব্যাকই ভিয়েতনামে জেনোসাইড চালানো মার্কিন সৈন্যদের নিয়ে আবেগমথিত কলাম লিখেছেন খবরের কাগজে! এমন কতো উদাহরণই না দেয়া যায়! আল মাহমুদের সোনালী কাবিনের (১৯৭৩) অনন্যতার সঙ্গে তার পরবর্তী জীবনের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দর্শনকে মেলানো যায়?
এভাবেই রাজনীতি সাহিত্যের কৌমার্য মোচন করে। নিহত আদর্শ-শয্যায় ঘটে অহল্যার শাপমুক্তি। পাঠকদের মধ্যে কে আছেন যিনি এই উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার বিশৃঙ্খলায় আক্রান্ত হন না?
স্বপ্নে-পাওয়া বৈকুণ্ঠধাম
সাহিত্যের অশ্বারোহে রাজনীতির আলোক দ্যুলোকের দিগ্বিজয়ী গান শুনতে হলে কান পাততে হবে ফরাসি সাহিত্যের ভুবনে। নিস্পন্দ নিচোল সেখানে দুলে উঠেছে মানুষ ও সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবনবোধ— যা যুগপৎ সমবক্ষ ও গভীর, যৌবনের বরমাল্য অথচ সান্ত্বনার অক্লম উৎসার। মধ্যযুগের ফরাসি সাহিত্যেই জীবনাচরণের রাজনৈতিক ভেদ-প্রভেদ উচ্চকিত হতে দেখি।
মাত্র আট বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় এমিল জোলার দুটো অসামান্য উপন্যাস— The Dream Shop (L’Assommoir, 1877) এবং Germinal (1885)| বস্তুত এই দুটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কেবল এমিল জোলারই নয়, গোটা ফরাসি সাহিত্যের তৎকালীন কণ্ঠস্বর চিনতে পারা যায়। শ্রমিক শ্রেণির মনোচেতনাতে শিক্ষা-সচেতনতার অভাব এই উপন্যাসদ্বয়ের মূলভাষ্য হলেও আমরা দেখি মদ্যপানকে জোলা ব্যবহার করেছিলেন আধিপত্যবাদের একটি প্রতীক হিসেবে। তবে জোলার উপন্যাসে সমাজতাত্ত্বিকের মতোন একটি সমাধানের উৎসমুখ ভেসে থাকতো, যাকে পরবর্তীতে ফরাসির সমাজতান্ত্রিক লেখকরা বাড়াবাড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। তবে ফরাসি সাহিত্যের ধারা বদলে সোভিয়েত বিপ্লবের যে প্রভাবের কথা বিভিন্ন সময়ে মার্কিন সমালোচকরা বলে গেছেন— তাতে ফরাসি চিন্তাকে ছোটো করে দেখার একটি প্রবণতা ছিল।
বস্তুত ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেয়ে ফরাসি সাহিত্যে বিরাজমান বিপ্লবের পটভূমি খানিকটা নয়, অনেকখানিই ভিন্ন। আমার এই বক্তব্যের পক্ষে সপ্রমাণ যুক্তি হলো হেনরি বারবুসের Under Fire (Le Feu, 1916)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা বা চরিত্র নির্মাণের প্রেক্ষাপট এই উপন্যাসে লক্ষ্যণীয়— তা তৎকালীন যে কোনো উপন্যাসের চেয়ে আলাদা, রাশিয়ার চেয়ে তো বটেই। বারবুস নিজে ফরাসি পদাতিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন, কিন্তু সেনাদলের ভেতরে তিনি শ্রমিক শ্রেণির যে দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেছিলেন, তাতে সাম্যের এক নবতর সংজ্ঞা নিহিত ছিল। এই সংজ্ঞা অবশ্য আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল তাঁর Clarté উপন্যাসে, যেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন— আধিপত্যবাদী যে কোনো যুদ্ধই যুদ্ধাপরাধ। ততদিনে অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। তিনি ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি মস্কোতে চলে যান, বিয়ে করেন এবং বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন। Clarté উপন্যাসটি যেহেতু তার পর প্রকাশিত হয়েছে, তাই অনেকেই মনে করেন, তিনি রাশিয়ার বিপ্লব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এটি লিখেছিলেন। অনেকের কথা বাদই দিলাম, স্বয়ং লেনিনই বলেছিলেন, উপন্যাসটি ফরাসি সরকার নিষিদ্ধ করতে চায়। কিন্তু আদতে ঘটনা তা ছিল না। বারবুসের তীব্র রাজনৈতিক মননবোধ রাশিয়ার বিপ্লব-পরবর্তী শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। এমনকি স্তালিনের আত্মজীবনী (Stalin: A New World Seen Through the Man, 1936) লিখলেও তার ভূমিকাতে তিনি স্পষ্ট করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান। যদিও তীব্র সমালোচনায় বারবুস আগেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন।
ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সংযোগ ঘটেছে দুভাবে— প্রথমত, রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাবক হিশেবে (দর্শন ও কথাসাহিত্য), দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিমানুষের অনুভব-সত্তার রাজনীতিকীকরণ (ছোটোগল্প ও কবিতা)।
ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সংযোগ ঘটেছে দুভাবে— প্রথমত, রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাবক হিশেবে (দর্শন ও কথাসাহিত্য), দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিমানুষের অনুভব-সত্তার রাজনীতিকীকরণ (ছোটোগল্প ও কবিতা)।
ফরাসি দর্শন ও কথাসাহিত্যে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির একটি বড়ো প্রভাব ছিল। বলাই বাহুল্য, তাতে রাজনৈতিক উদ্বোধনের সুর ছিল স্পষ্ট। লুইস অ্যারাগনের সাহিত্যযাত্রার প্রথম দিকে যে নিরীক্ষাধর্মী কবিতাগুলো আমরা পাই, তাতে সোভিয়েক বিপ্লবের সুর উচ্চকিত। The Bells of Basel (Les Cloches de Bâle, 1934) এবং The Finest Districts (Les Beaux Quartiers, 1936) গ্রন্থ দুটিতে আমরা তাঁর তীর্যক মন্তব্য পাই পেটিবুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে। এমনকি আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতিকে কী সাহসীভাবে তিনি আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তাতে সোভিয়েত বিপ্লবের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের আমলাতান্ত্রিক সংকোচন নীতি তাঁর চোখে পড়েনি। ফলে চার খণ্ডে The Communists (Les Communistes, 1949-1951) লিখলেও আমার বিচারে রাজনৈতিকভাবে তাঁকে সঠিক বলতে পারি না, কেননা তিনি রাজনীতিকে মতবাদের স্থানাঙ্ক থেকে বিবেচনা করেছিলেন, আদর্শকের প্রেক্ষাপট থেকে নয়। একই কথা পল নিজান ও জঁ-পল-সর্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ কারণেই এত প্রভাবশালী কথাসাহিত্যিক থাকলেও ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর ফরাসি সাহিত্যের বাঁক বদলে যায়। তাতে পাশ্চাত্য, বিশেষত মার্কিনবিরোধী মতবাদ ও দর্শন সাহিত্যিক পদবাচ্য হিসেবেই অধিষ্ঠিত হয়— কোনো দলীয় বা মতবাদকেন্দ্রীক নয়।
কিন্তু ফরাসি কবিতা ব্যক্তিমানুষের রাজনৈতিক মানসকে এমন নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছে যে, গোটা বিশ্ব সাহিত্য এখানে হাঁটুমুড়ে বসতে বাধ্য। ১৮৫৭ সালে শার্ল ব্যোদলেয়ারের প্রথম কবিতার বইটি প্রকাশ করে অগোঁস্তে পিউ মাল্যাসি বিশ্বকে উপহার দিলেন আধুনিকতার এক নন্দনভাষ্য— যাতে ব্যক্তি জীবনের অণু-পরমুণুতে লেপ্টে থাকা রাজনৈতিক ইতিহাসের হদিশ পাওয়া যায়। The Flowers of Evil (Les Fleurs du mal) এর প্রথম সংস্করণের একশোটি কবিতা বদলে দিলো সাহিত্যের শরীরে রাজনীতির চুম্বনরেখা। ব্যোদলেয়ার সম্পর্কে আঁঁর্তুর র্যাঁবো বলেছিলেন, ‘প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা’— এবং স্বীকার্য, অজাতশ্মশ্রু র্যাঁবোর এই সংলাপ অত্যুক্তি ছিল না। ব্যোদলেয়ারের চিন্ময় সত্তা, হেমন্তের ঝড়ো হাওয়ার মতো বয়ে যাওয়া যৌবনকুঞ্জ আত্মার অনাবরণ উন্মোচনে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছে— মানুষের আত্ম-অনুসন্ধান, দুঃখ, রোগ, মত্ততা, এমনকি ইন্দ্রিয়সমূহের অতীন্দ্রিয় বিনিময়ও রাজনৈতিক। এই বক্তব্য আমাদের কাছে নতুন— এমনকি, রাশিয়া ও ফরাসি বিপ্লবের পরও এই বক্তব্য আমাদের কাছে নতুনই থেকে যায়। কেননা, ততক্ষণে ব্যোদলেয়ারের আশ্চর্য মেঘমালা পৌঁছে গেছে যুবক মলার্মের কলমে, ভের্লেনের অলৌকিক শুদ্ধতায় আর আঁঁন্দ্রে জীদের ভবিষ্যৎ সংলাপে। সত্যি বলতে, গোটা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ছয়টি দশক পৃথিবী নানা আগুনে পুড়লেও বারবার তাকে শরনাপন্ন হতে হয়েছে ব্যোদলেয়ারের কাছে— রাজনৈতিক কী সামাজিক মহত্ত্বে, মাধুর্যে বা দ্বিচারিতায়। পৃথিবী বুঝে গেছে টেনিসন থেকে সুইনবার্ন পর্যন্ত কবিরা কবিতাতে যে সুরকে প্রাধান্য দিয়ে গেছেন, তাতে পীতাভ পাংশুতা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। রাষ্ট্রবিপ্লবের পারম্পর্যে ক্ষত-বিক্ষত পৃথিবী ততদিনে জেনে গেছে মন্ময় ভঙ্গি, জ্ঞানের ভার কিংবা হিতৈষণার জঞ্জালে যুদ্ধক্ষত মানুষের কিছু আসে যায় না। ইংল্যান্ডের ব্লেইকি, কীটস, কোলরিজ; জার্মানির নোভালিস বা হ্যোল্ডার্লিন; ফ্রান্সের নেভ্যাল বা গোঁতিয়ে; আমেরিকার পো কিংবা হুইটম্যান; বাঙলার মধুসূদন কী রবীন্দ্রনাথ— কেউই দুটো বিশ্বযুদ্ধ থামাতে পারেননি।
তাহলে কেনো পৃথিবী ব্যোদলেয়ারকে কাঠগড়াতে দাঁড় করাবে না? কারণ, ব্যোদলেয়ার তো জানতেন— কবিতার সবটুকুই বিষাদসাপেক্ষ, এমনকি প্রেমের পূর্ণতাও; মৃত্যু আরও খানিকটা জীবন বৈ কিছু নয়। পৃথিবীর সাহিত্য এই ব্যোদলেয়ারের হাতেই রাজনৈতিক ভাষাজ্ঞান পেলো— এই বক্তব্য অন্তত আমার বিচারে সত্য।
বিদীর্ণ আত্মা, নির্বেদের বাঁধন
সাহিত্যের রাজনৈতিক ভাষাতাত্ত্বিক শার্ল ব্যোদলেয়ার— এ কথা একটু আগেও বলেছি; কিন্তু রাজনীতির রূপান্তরকামী দর্শনে ফরাসিরা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এর একটি কারণ হতে পারে ব্যোদলেয়ার-উত্তর ফরাসি সাহিত্য দীর্ঘ একটি সময় ধরে তাঁকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে গেছে, যেমন বাঙলা ভাষায় ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের সময়ে। ফলে রাজনীতির তটরেখায় সংস্কৃতির বিকাশধারা খুঁজে দেখতে হলে অনস্বীকার্যভাবেই রাশিয়ার সাহিত্যের চোখে চোখ রাখতে হবে।
বলশেভিক বিপ্লবকে এই সাহিত্যের বাঁক বদলের মূলকেন্দ্র ধরা যেতে পারে। আমরা যদি ইতিহাসনিষ্ঠ হই তবে বুঝতে পারবো— রাশিয়ার সাহিত্য আমাদের রাজনৈতিক ব্যাকরণ উপহার দিয়ে গেছে। ব্যোদলেয়ার যখন ‘পশুর মতো ঘুম’ চোখে নিয়ে সভ্যতার ঘানি টেনে যাওয়া মানুষের কাছে নিবেদন করেন ‘সময়ের মন্থরতা’, তখন তাতে নথিভুক্ত হয় রাজনৈতিক আত্মকরুণা— অর্থাৎ, তিনি ভাষা প্রতিষ্ঠা করেছেন তাকে করুণা করবেন বলেই। কিন্তু মায়াকোভস্কির ‘পাৎলুনপরা মেঘ’ পড়তে গিয়ে আমরা বুঝি, সাহিত্যে রাজনৈতিক ভাষ্যের চক্ষুদান পর্ব সমাপ্ত হলো। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে আছে ১৯০৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লবের ভূমিগর্ভে— সুতরাং, সেন্ট পিটার্সবার্গে লেনিন এবং ট্রটস্কি যখন পলাতক অবস্থায় আছেন, তখন সাহিত্যের বাঁক বদলও সেখানে নিহিত ছিল সঙ্গোপনে। কে জানতো, সেখানে লুকিয়ে থাকা ম্যাক্সিম গোর্কিই নির্মাণ করবেন এমন এক মায়ের চরিত্র যিনি মায়াকোভস্কিকে বর দিবেন কিংবা ভাগ্য বদল করবেন পুশকিনের সাথে!
কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হচ্ছে What is to be done? নামে একটি অনুল্লেখিত উপন্যাস, যার হাত ধরে রাশিয়ার সাহিত্যের সঙ্গে গোটা বিশ্ব সাহিত্য নিজের অজান্তেই প্রবেশ করেছিল রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতীকধর্মী বিপ্লবে। নিকোলাই চেরেনাইশিভোস্কির লেখা এই উপন্যাসটি নিয়ে ১৯০২ সালে লেনিন নিজে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যার শিরোনাম ছিলো The Twin Revolution। কিন্তু রাজনীতির অক্ষবদল হলেও সাহিত্যের সত্যবদল হয় না। ফলে লেনিন নিজেই এই ধারার উপন্যাসের বিষাদগার গেয়েছেন তাঁর শাসনামলের একেবারে শেষ দিকে। স্তালিন তো এই ধারার ঔপন্যাসিকদের ধরে জেলেও পুরেছেন।
রাশিয়ার সাহিত্য যেমন রাজনৈতিক সাহিত্যের অক্ষরলিপি তৈরি করেছে, তেমনি তাকে রাষ্ট্রীয়ও করে তুলেছে। ফলে দাপ্তরিক সাহিত্য জন্ম নিয়েছে কালে কালে। এটিও বৃহৎ বিচারে রাজনৈতিক সাহিত্যই— কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর পছন্দমতো সাহিত্য। পরবর্তীতে পৃথিবীর সব ভাষাতেই এই সরকারি সাহিত্যের নজির আমরা পেয়েছি। কিংবা বলা যেতে পারে, রাজা-রাজরার যুগের দরবারি সাহিত্য বা সভাকবির আদলে আমরা সাহিত্যসভার নমুনা ফিরে পেয়েছি।
তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাশিয়ার সাহিত্যের কাছে গোটা পৃথিবীকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, কেননা সাহিত্যের রাজনৈতিক সীমা-পরিসীমা বা বলা যেতে পারে রাজনীতিকে সাহিত্যের উপাদান করে তোলার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁরা করেছেন। স্বয়ং লেনিন তাঁর রচনাসমগ্রে ১৫৩টি প্রবন্ধ রেখেছেন কেবল সাহিত্য ও বিপ্লবের সমন্বয় ও ভাষার বিনিময়-ক্রিয়ার রূপরেখা নির্মাণে। এই ১৫৩টি প্রবন্ধে কিন্তু চলচ্চিত্র আলোচিত হয়নি, কেবলই সাহিত্য।
১৯২৩ সালে ট্রটস্কি যখন Literature and Revolution শিরোনামে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তখন আমরা বুঝতে পারি, সাহিত্যের রাজনীতি সাহিত্যের ভেতরেও ক্রিয়াশীল থাকে। কারণ এই গ্রন্থে ট্রটস্কি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন যে, ১৯০৫-১৯১৭ অব্দি লেখা রাশিয়ার সকল সাহিত্যই ব্যক্তিবাদের (Individualism) জয়গান গেয়েছে; তিনি সাহিত্যে সমষ্টির জয়গান শুনতে চান।
ক্ষমতা কথা বললে যেমন তার পারিতোষরা আরও জোরে কথা বলে, তেমনি ক্ষমতা কথা বললেই কোথাও-না-কোথাও বিপ্লবও কথা বলে। সুতরাং ১৯২৪ সালেই প্রকাশিত হয় ইয়াভগ্যানি এভিনোভিচ জ্যামায়তিনের সুবিখ্যাত উপন্যাস We এবং আলোড়ন ফেলে দেয় সারা পৃথিবীতে, বিশেষত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে— কেননা, ডায়াসপোরা সাহিত্য হিশেবে এই উপন্যাসটি তখন প্রায় কিংবদন্তীর মতো। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে বসে লেখক এই উপন্যাসটি লিখেছেন এবং এটি প্রকাশিতও হয়েছিল নিউ ইয়র্ক থেকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বহুকাল পরে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার অবমুক্ত করা দলিল থেকে জানা যায়, এই উপন্যাসটির প্রায় কয়েক হাজার কপি কিনে নিয়েছিল তৎকালীন মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে এই বইটি তাদের গুরুত্বপূর্ণ রসদ যুগিয়েছিল।
অক্ষরমালার তপোক্লিষ্ট মহিমা
১৯৩৮ সাল। স্পেনে গৃহযুদ্ধ চলছে। ইয়েল রিভিউতে জার্মান ঔপন্যাসিক থমাস ম্যানের he Magic Mountain (Der Zauberberg, 1924) উপন্যাস থেকে একটি বাক্য ছাপানো হলো— In our time the destiny of man presents its meanings in political terms. এই বাক্যটিকে ঘিরেই আবর্তিত হলো পৃথিবীর অসামান্যতম কবিতাগুলোর একটি— Politics, ডাব্লিউ বি ইয়েটসের লেখা এই কবিতার প্রতিটি ছত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে সাহিত্যের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। বিপরীতমুখীতার মেজাজেই ইয়েটস তুলে ধরেছিলেন সাহিত্য আর রাজনীতির নিজস্ব ভুবন এবং তাদের মোহনা। ব্যক্তিগত বিবেচনায় আমি মনে করি, এই কবিতাটি সাহিত্যের রাজনৈতিক দর্শন আলোচনার মূল টেক্সট, যেমন রাজনীতির সাহিত্যিক আলোচনার জন্য আমাদের দ্বারস্থ হতে হবে মায়াকোভস্কি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা আলবেয়ার কামুর কাছে।
সাহিত্য আর রাজনীতির সম্পর্ক বা সংযোগ নির্ণয়ে ইংরেজি সাহিত্য বহুকাল আগেই একটি প্রশ্ন তুলেছিল— প্রধানমন্ত্রী আর ম্যান বুকার জয়ী সাহিত্যিকের কাজ কি এক? উত্তরও দিয়েছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের বাঘা বাঘা সাহিত্যিকেরা। মোটা দাগে তাঁদের বক্তব্য ছিল, ‘সাহিত্য’ এবং ‘রাজনীতি’ সমাজ ও মানুষের ভিন্ন ভিন্ন স্তর সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত দিয়ে থাকে। সাহিত্য যতখানি সিদ্ধান্ত নেয়, তা সাহিত্যের অঙ্গন ও প্রয়োজন থেকে; কিন্তু রাজনীতি আরও বেশি সমাজঘনিষ্ঠ। সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যিকদের একটি বড়ো অংশ মনে করতেন, সাহিত্য সমাজের প্রবণতাকে পর্যবেক্ষণ করে মাত্র। কিন্তু গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এসে এই মতামত আর হালে পানি পায়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই গোটা পৃথিবীতে সাহিত্যের ধারণা বদলাতে থাকে। বিশেষত ফরাসি ও রাশিয়ার সাহিত্যের বিপুল অথচ সূক্ষ্ম বিস্তৃতি ইংরেজি সাহিত্যের ধারণায় বড়োসরো আঘাত হানে। ফলে ডাব্লিউ. বি ইয়েটসের মতো সাহিত্যিকরা রাজনীতির উপরিতলে নয়, বরং মর্মমূলে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। তখন থেকেই রাজনৈতিক বাতাবরণে মানুষের জীবনের অনুপুঙ্খ পরিবর্তনগুলো ইংরেজি সাহিত্যের ভাষা নির্মাণে ব্যবহূত হতে থাকে। ফলে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্রায় ইংরেজি সাহিত্যে রাজনৈতিক প্রভাব বা রাজনীতিতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব বিশ্লেষিত হতে পারে।
রাজনৈতিক সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্য দিয়ে রাজনীতির প্রপঞ্চগুলোকে তুলে আনাই ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান কৃতিত্ব। রাজনীতি বলতে বৃহৎ অর্থে যদি ক্ষমতা বা সামাজিক কর্তৃত্বের বিনির্মাণ বোঝায়, তবে ইংরেজি সাহিত্যে তার সূচনা সেই শেক্সপিয়রের সময় থেকেই। শেক্সপিয়রের সাহিত্যে ঐতিহাসিক ও রোমান ধাঁচের যে কাহিনিনির্মাণ দেখি, দ্বন্দ্বের যে রাজনৈতিক পরিকাঠামো দেখি— তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইংরেজি সাহিত্যের রাজনৈতিক যাত্রা নিদেনপক্ষে পাঁচশ বছর আগে। ট্র্যাজিডির অন্তরালে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের সুরটুকু বাদ দিলে আর কী-ই-বা অবশিষ্ট থাকে ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার, হ্যামলেট বা ওথেলোতে? এমনকি হেনরি দ্য ফোর্থের সেকেন্ড পার্টে প্রতিনিধিত্বশীল যে সামাজিক কাঠামো দেখতে পাই, তারও কেন্দ্রে রয়েছে রাজনৈতিক বিবর্তন। না হলে ফলস্টাফকে আমাদের এত মনে পড়ে কেনো?
শেক্সপিয়র বা সারভান্তেস থেকে শুরু করে আজ অবধি ইংরেজি সাহিত্যের বিকাশে রাজনীতি উপস্থিত ছিল— কখনও প্রবলভাবে, কখনও মৃদু ঢঙে; কখনও মোটা দাগে, কখনও সূক্ষ্ম বোধে। কিন্তু রাজনীতির জটিল দ্বন্দ্ব সপ্তদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে যতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে— কুড়ি শতকের আলোকবর্তিকাকে মনে রেখেই বলছি— অন্য শতকগুলোতে এই স্বতঃস্ফূর্ততা অনুপস্থিত। কে আছেন যিনি জন মিলটনের Paradise Lost (1667) বা জন ড্রাইডেনের Absalom and Achitophel (1681)– এর রাজনৈতিক জটিল আবর্তকে ভুলে যাবেন? জনাথন সুইফটের Gulliver’s Travels (1726)- এর মতো এতটা স্পষ্টভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক সংঘাত আর কোন সাহিত্যে উঠে এসেছে? এই তুলনায় বরং অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুটা খনিক ধোঁয়াশাপূর্ণ মনে হয়। যদিও তখন ইংরেজি সাহিত্যের আকাশে শেলী-ওয়ার্ডঅর্থ-বাইরন সূর্যত্রয় একসঙ্গে উঠছেন। এই সময়ে তাঁদের কবিতা অরাজনৈতিক ছিল, সে কথা বলছি না; তবে রাজনীতির উপস্থিতি ছিল অনেকটা মায়ামেদুরের মতোন। বরং এই সময়ে কথাসাহিত্য এক প্রবল বিপ্লব এনে দিয়েছিল ইংরেজি সাহিত্যে। ১৮৪০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে গোটা যুক্তরাজ্যেCondition of England নামে একটি বাক্যাংশই জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তৎকালীন ইংরেজি কথাসাহিত্যিকরা। শিল্পায়ন ও নগরায়নের দরুণ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা ব্রিটিশ মুল্লুকে যে দারিদ্র্য, নীতিহীনতা, শোষণ, পুঁজির বিকাশ আর অমানবিকতা ছড়িয়ে পড়েছে, তা নিয়ে তখন সোচ্চার হয়েছিলেন ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক থমাস কার্লি, এলিজাবেথ গ্যাসেল, বেঞ্জামিন ডিস্যালি, চার্লস ডিকেন্স, জন রুসকিন, চার্লস কিংসলে প্রমুখ।
এরপরের ধাপটি গুরুত্বপূর্ণ। দিকে দিকে ব্রিটিশ রাজত্বের বিষয়ে স্বয়ং ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীরাই আপত্তি তুলছেন। অন্যদিকে ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে ইউরোপীয় রেনেসাঁর আলোকোৎসব। আধিপত্যবাদবিরোধী সাহিত্যের ইশতেহার হাতে ইউরোপের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্ব সাহিত্যের মঞ্চে। পোল্যান্ডের সংগ্রাম আর বিষাদের স্বরলিপি হাতে একা জোসেফ কনরাডই নিয়ে এলেন তিনটি অনবদ্য সৃষ্টি— Heart of Darkness (1899), Nostromo: A Tale of the Seaboard (1904) এবং Under Western Eyes (1911)। গোটা পৃথিবী জেনে গেলো অন্ধকারকে আঘাত করেই আলোর পথ ধরতে হবে। শুরু হলো স্পেনের গৃহযুদ্ধ। রাজনীতির আগুনে শুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো সাহিত্যের অক্ষরমালা। সেই অক্ষরের রক্তজবায় বদলে যেতে লাগলো দুনিয়াব্যাপি রাজনীতির ইশতেহার।
মা তোর বদনখানি মলিন হলে
যদি নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞায়নের সঙ্গে জাতীয়তাবোধের বিকাশের ধারাকে যুক্ত করি, তবে স্বীকার করতেই হবে বাঙলা সাহিত্যে রাজনীতির প্রতিফলন একেবারে শুরু থেকেই। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে, ভাষা হিশেবে বাঙলার বিকাশের সঙ্গেই একটি রাজনৈতিক চেতনা জড়িয়ে আছে। আদি ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভাষার উদ্ভব হলেও, তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনীতির চেয়ে নৃতাত্ত্বিক ভূমিকা বেশি ছিল। কিন্তু বাঙলা ভাষা যতখানি স্বয়ম্ভূ, ততখানি স্বাধীনতা সে পায়নি। এর বেশ কিছু কারণ আছে। প্রথমত বাঙলাকে চলতে হয়েছে একটি ব্রাত্য জাতিগোষ্ঠীর মুখের ভাষা হিশেবে। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে আপাত বিকাশহীন একটি জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা হিশেবে চিহ্নিত হয়েছে বাঙলা। তাকে দেয়া হয়েছে ‘অনার্যের মর্যাদা’। এমন নিদারুণ ভাগ্য ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ বা চিনা ভাষার বরণ করতে হয়নি। ঔপনিবেশিক আধিপত্য তাদের ওপর বিরাজমান থাকলেও ভাষা হিশেবে তাদের নিজস্ব বিকাশ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।
কিন্তু বাঙলা যেন আঁঁতুরঘরেই অবাঞ্ছিত এবং তাকে বাঞ্ছিত পদবাচ্য না করার প্রক্রিয়াটিও রাজনৈতিক। এ কারণেই বাঙলা ভাষারই একটি নিজস্ব রাজনৈতিক বিকাশ আছে, যেটা অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও আয়ারল্যান্ডের আদিবাসীদের ভাষা বাদ দিলে, অন্য ভাষার ক্ষেত্রে খুব একটা চোখে পড়ে না। এখানেই বাঙলা ভাষার নিজস্ব ভিত রচিত হয়ে গেছে এবং কালের বিবর্তনে বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই ভিত আরও শক্ত হয়েছে।
সংস্কৃত ভাষা থেকে জন্ম হলেও এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যপট সংস্কৃতকে বাঙলার বিমাতা হিশেবেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফলে ব্যাকরণ বা ব্যুৎপত্তিগত সম্বন্ধ থাকলেও আদতে সংস্কৃত ও বাঙলার মাঝখানে একটি শ্রেণিবৈষম্যের হাইফেন রয়ে গেছে। এই সুযোগ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী গ্রহণ করেছে। ফলে বার্মিজ, পর্তুগিজ, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, চিনা ভাষার শব্দ-হরফ-ব্যাকরণ এতে নাক গলাবার সুযোগ পেয়েছে।
কিন্তু বাঙলা যেহেতু নদীবর্তী জনগোষ্ঠীর ভাষা, তাই চরিত্রগতভাবে সে মিথষ্ক্রিয়ার ধারাতে পথ চলেছে। অন্য ভাষা, এমনকি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তার মতান্তর ঘটলেও মনান্তর হয়নি কখনোই। এ কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যের সলতেখানি না পাকিয়ে বাঙলা সাহিত্যের প্রদীপ জ্বালতে গেলে আলো ঠিক মতো পাওয়া যায় না। একদা যে রাজনীতি জাত্যাভিমানের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল দুই ভাষার বনভূমিতে, কালের বিবর্তনে আজ সেটা পরম্পরার মনোভূমি। তাই বাঙলা সাহিত্যের আয়নায় রাজনীতির অবয়ব দেখতে গেলে সংস্কৃতি সাহিত্যের আলোটা খানিক জ্বেলে নেয়া প্রয়োজন।
সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে আমরা রাজনীতির তুমুল গাঢ় সমাচার খুঁজে পাই। যেহেতু ‘দৃশ্য’ ও ‘শ্রব্য’— এ দুটি প্রধান শ্রেণিতে সংস্কৃত সাহিত্য তার ভুবন বিস্তার করেছে— সেহেতু সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য থেকেই এর উৎস খুঁজে বের করাটা যুক্তি সংগত। এই পথে হাঁটলে আমরা দেখতে পাই, সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের সূচনাই খানিকটা রাজনৈতিক, কেননা নাট্যতত্ত্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্রের সংকলিয়তা ভরতমুণি বলেছেন— বেদ-উপবেদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ললিতাত্মক নাট্যবেদের স্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মা। তাহলে প্রশ্ন থেকেই যায়, বেদ-উপবেদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলে তা কি ‘ললিতাত্মক’ হবে না? কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মা যদি সৃষ্টি না করেন, তবে কি তা ‘ললিতাত্মক’ হবে না? ভরতমুণি বোধ করি এই সূক্ষ্ম রাজনৈতিক পর্দা নির্মাণের মাধ্যমেই সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সংজ্ঞায়ন করেছিলেন, কেননা তিনি নিজেও জানতেন পঞ্চমবেদের যে ধারণা তিনি দিয়ে যাচ্ছেন, তা ভাঙার ধনুর্ভঙ্গ পণ নিয়ে এই মর্ত্যলোকে জন্ম নেবেন অবিনশ্বর অনন্য সংস্কৃত নাট্যকার ভাস। নাটকের রাজনৈতিক দৃশ্যায়ন যে অমরতার নির্বিকল্প অংশ হয়ে উঠতে পারে, ভাস ছাড়া আর কে এই পৃথিবীকে তা শিখিয়ে গেছেন?
গোটা সংস্কৃত সাহিত্য আমার পড়া নেই, তাই তার বিচার করা আমার জন্য ধৃষ্টতা; তবে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের একজন মনোযোগী কিন্তু খাবি-খাওয়া শিক্ষার্থী হিশেবে বলতে পারি— সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে রাজনীতির যে বিবিধ ধারা দেখতে পাই, তা বাঙলা নাটকেও অনুপস্থিত। যদিও এর প্রধান আকর হলো মহাভারত ও রামায়ণ। অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু হয় রামায়ণকেন্দ্রীক (যেমন: ভাসের প্রতিমা, অভিষেক ইত্যাদি), না হয় মহাভারতকেন্দ্রীক (যেমন: ভাসের কর্ণভারম, উরূভঙ্গম্ ইত্যাদি)। তবে লোকবৃত্তান্তমূলক (যেমন: শুদ্রকের মৃচ্ছকটিক, ভাসের প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ বা স্বপ্নবাসবদত্তম্) আর পুরাণইতিহাসকেন্দ্রীক (যেমন: বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস) নাটকও আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সংস্কৃত নাটকের মূল রস যাই হোক না কেনো, কোথাও না কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে একটি রাজনৈতিক স্তরবিন্যাস থাকে। তাতে রাজনৈতিক প্রবাহ হয়তো লঘুছন্দে রয়েছে, কিন্তু মূল রস আস্বাদনে ওই রাজনীতিটুকু বোঝা জরুরি। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের ছত্রে ছত্রে উদয়ন-বাসবদত্তার অমোঘ প্রেমের বর্ণচ্ছটা। কিন্তু রাণী বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর হাতে ন্যস্ত করার বিষয়ে যৌগন্ধনারায়ণের যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কাজ করেছিল, তা অনুচ্চারিত থাকলেও ঐতিহাসিক। ‘ততঃ প্রতিষ্ঠিতে স্বামিনি তত্র ভবতীমুপনয়তো…’ পদ্মাবতীর এই সাক্ষ্যসুলভ সংলাপটি হয়তো মধুসূদনের কল্যাণে বাঙলা সাহিত্যেও জনপ্রিয় কিন্তু এই সাক্ষ্যেই কি উদয়ন রাজ্যের নিগূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি আমরা টের পাই না? এ কথা ঠিক, সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে রাজনীতির প্রতিফলন খুঁজতে গেলে ঘড়ির বয়স্ক কারিগরের মতো অনুসন্ধান করতে হয়। বাঙলায় যেমন রাজনৈতিক নাটকের আলাদা মেজাজ, আলাদা মনন; এমনকি গ্রীক বা ইংরেজিতেও— সংস্কৃতে তেমনটা নয়। একমাত্র শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকটিতে আমরা সরাসরি রাজনৈতিক দৃশ্যায়ন দেখতে পাই। উজ্জ্বয়িনী রাজ্যের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দিয়ে যে আখ্যানের শুরু তার পরতে পরতে রাজনৈতিক সংলাপ, গণবিপ্লব আর স্বৈরাচারের পতন এবং একমাত্র সংস্কৃত নাটক, যাতে শ্রেণি বৈষম্য ভেসে যায় বিদ্রোহের জোয়ারে।
মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত নাটকের একটি ব্যাতিক্রমধর্মী উদাহরণ। কারণ এতখানি উদারনৈতিকভাবে বিদ্রোহের দৃশ্য রচনা শূদ্রক নিজেও তাঁর পরবর্তী নাটকগুলোতে রাখেননি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাঁর এই নাটকটিই বাঙলা ভাষার সাহিত্যের পক্ষে একটি বড়ো দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা মধুসূদন আর বিদ্যাসাগরের পারস্পরিক পত্রাবলি থেকে জানতে পারি, বাঙলায় নাটক রচনার বিষয়ে বিদ্যাসাগর মশাই মধুসূদন দত্তকে মৃচ্ছকটিকের চারুদত্তের উদাহরণ দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরপ্রতিম ইঙ্গিত বুঝে নিয়েছিলেন মধুসূদন, রচনা করেছিলেন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক কৃষ্ণকুমারী— বাঙলা নাটকে নথিভুক্ত হলো নারীর দীর্ঘশ্বাসজনিত রোম্যান্টিকতা।
কিন্তু কৃষ্ণকুমারী লেখার মাত্র দু বছর আগেই বাঙলা নাট্য সাহিত্যের রাজনৈতিক দীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গেছে। ১৮৫৯ সালে দীনবন্ধু মিত্র লিখে ফেলেছেন নীলদর্পন, অর্থাৎ বাঙলা ভাষা তাঁর সমূহ শব্দভাণ্ডার আর রসসমগ্র নিয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের রূপরেখায় টিপসই দিলো। এই একটি দস্তখতেই বদলে গেলো বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রায়োগিক চরিত্র। সংস্কৃত ব্রিটিশ শাসনামলে কেবল অসাড় আভিজাত্যটুকুই ধরে রেখেছিল। তারও আগে এই ভাষা ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিচায়ক— অর্থাৎ শ্রেষ্ঠশ্রেণিভুক্তির নামাবলী। বাঙলা তখন ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত— সমাজপতিদের তৈরি করে দেয়া দেয়ালের ওপারের বাসিন্দাদের মুখের ভাষা। কিন্তু এই একটি ভাষাই প্রথম শ্রেণি আভিজাত্যের বদলে মাতৃত্বের অহংকারকে ধারণ করে— বিদ্যাসাগর, দেবেন ঠাকুর, রামমোহন রায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো মনীষীদের ‘মায়ের ভাষা’ হয়ে ওঠে বাঙলা। সংস্কৃততে ‘বাঙলাভাষীরা’ ছিলেন ব্রাত্য; কিন্তু বাঙলায় কোনো ব্রাত্য নেই— কেননা, মায়ের কাছে কোনো সন্তানই তো ব্রাত্য হতে পারে না।
কিন্তু শৌর্যে-সাহসে এই বাঙলাই হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ রাজের প্রধান প্রতিপক্ষ। ইংরেজি শিখে বাঙালি যখন আধপাকা সাহেবী কায়দা রপ্ত করতে ব্যস্ত, তখন স্বয়ং ইংরেজদেরই কেউ কেউ মজে গেছেন বাঙলা ভাষার মাধুর্যে। এখানেই ভাষা হিশেবে বাঙলার সৌন্দর্য যে, স্নেহের আঁঁচল বিছিয়ে সে তাবৎ ভাষাভাষীদের ভালোবাসা দিতে পেরেছে। ফলে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বাঙলা গদ্যভাষার অবিন্যস্ত পয়ারে বিদ্যাসাগর বেঁধে দিলেন সুরের বিন্যাস— বাঙলা বিরামচিহ্ন— তিষ্ঠ ক্ষণকাল। মধুসূদন তাতে ঘোষণা করলেন অমিত্রাক্ষরের জয়গান। বাঙলা ভাষায় যেদিন রচিত হলো মেঘনাদবধ কাব্য, সেদিনই প্রমাণিত হলো— এ ভাষাতেই মানুষের স্বর্গাভিযান সম্ভব। মেঘনাদের মৃত্যু প্রকৃত প্রস্তাবে চিরায়ত প্রথার বিরুদ্ধে সাহিত্যের এক অনবদ্য রাজনৈতিক বিপ্লব।
এই রাজনৈতিক বিপ্লবে মনীষার বিচ্ছুরণে একের পর এক ইশতেহার রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক না রোম্যান্টিক— এ বিষয়ে আমারও দ্বিধা ছিল বহুকাল। বহু তর্ক, বিবাদ আর ঝগড়া শেষে বর্তমানে আমার ধারণা জন্মেছে— তিনি রাজনৈতিকভাবে রোম্যান্টিক। সাহিত্যের দর্পণকে তিনি এমনভাবে প্রস্তুত করেছেন, যাতে রাজনীতি তার সুরে-অসুরে ধরা পড়ে। ফলে বাঙলা সাহিত্যের রবীন্দ্রযুগ তীব্রভাবে রাজনৈতিক— এ কথা এককালে আমি স্বীকার না করলেও, আজ করি। কিন্তু সে রাজনীতি মতাদর্শের নয়, দর্শনের। এ কারণেই রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্তঃস্থলে দর্শনের যে জ্যামিতিক রেখা আমরা পাই, সেগুলো কখনোই অক্ষচ্যুত নয় আবার পারস্পরিক ছেদ-সম্পর্কিতও নয়। স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রতিটি রেখা তাদের নিজস্ব নিখিলে নিটোল।
কিন্তু এই অনন্যতায় ঘেরা রবীন্দ্রযুগেই আমরা দেখি কী বিপুল ঐশ্বর্যমালায় রচিত হচ্ছে সাহিত্যের রাজনৈতিক অভিজ্ঞান। তিরিশের দশকের কবিতায় রাজনীতি হয়ে উঠছে উদ্বোধনের মহামন্ত্র— এবং এই রাজনীতি সুস্পষ্ট দুটো ধারায় বিভক্ত। এক ধারাতে চিহ্নিত হয়েছে রাজনৈতিক গতিপথ— রাশিয়া, ফরাসি ও চিনের বিপ্লব তাতে সময়ানুক্রমিক সংলাপ যোগ করেছে এবং এই ধারার হাত ধরেই নির্মিত হয়েছে স্বাধীন ভারতের প্রবেশদ্বার। স্বীকারে দ্বিধা নেই, এই ধারার যাত্রাপথে আছে মন্বন্তর, দাঙ্গা আর শবাচ্ছন্ন অন্ধকারসমগ্র। স্বাধীনতার প্রতিটি স্লোগান যে দেশভাগের যন্ত্রণা হয়ে ফিরে আসবে— বিষ্ণু দে তা জানতেন না? সুভাষ মুখুয্যে? কিংবা বাড়ুয্যে বাড়ির মানিক বা তারাশঙ্কর?
দ্বিতীয় যে ধারাটি, তার মূল অভিসন্দর্ভ ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষের টুকরো টুকরো স্বাধীনতা। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু মানুষ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কারও নাম ছিঁড়ে গেছে, কারও দেশ ভেঙে গেছে, কেউ ধর্মের নামে মরে পড়ে আছে… এই ব্যর্থ, বিষণ্ন, বিদীর্ণ অথচ স্বাধীন মানুষের মনস্তত্ত্ব হয়ে উঠেছিল আরেকটি ধারার সাহিত্য।
যে সূর্যোদয়ে বিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছিল, তার আলো বাঙলা সাহিত্যকেও এক নবধারায় উন্নীত করলো। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ যেমন বাঙালির ইতিহাসে এক মর্মন্তুদ অধ্যায়; তেমনি এই ভাঙনের বিরুদ্ধেই বাঙলা সাহিত্যে দাদরা তালে রচিত হয়েছিল ঐকতানের সুর। ১৯০৫ সালে একদিকে বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক অভিঘাত; অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যূথবন্ধনের সাহিত্যিক অভিঘাত— অর্থাৎ এই প্রথম বাঙলা সাহিত্য রাজনৈতিকভাবে রাজনীতির ভুল সিদ্ধান্তকে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
‘আমার সোনার বাংলা/ আমি তোমায় ভালোবাসি’— এই সঙ্গীত বাঙলা সাহিত্যের রাজনৈতিক ইশতেহার। প্রতিটি পঙক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁকে দিয়েছেন স্বদেশ ও স্বজাতির আত্মিক সম্পর্ক এবং সুর হিশেবে গ্রহণ করেছেন তৎকালীন পূর্ব-বাঙলার (বর্তমান বাঙলাদেশ) এক বাউল সুরকে। কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে ‘মা’-কে প্রতিষ্ঠা করেছেন, গগন হরকরা সুরে সেখানে নৈবেদ্য সাজিয়েছেন; এবং কী অলৌকিক সমাপতন— এই সঙ্গীতটিই হয়ে উঠলো বাঙালির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল উদ্ধারের মন্ত্র। পৃথিবীর অনন্য সংগ্রাম মহাকাব্যিক মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত হলো এটি। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, বাঙলাকে বেঁধে রাখবে সুর— তাই যে ভাঙনের নিদারুণ সময়ে প্রতিবাদস্বরূপ এই গান তিনি রচনা করেছিলেন, তা-ই মুক্ত হলো স্বাধীন বাঙলার আকাশে। সেই থেকে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কে ‘মা’ একটি মেটাফোর হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ‘মা’ কিংবা ‘মাতৃত্ববোধ’ বাঙালির আত্মজাগরণের আয়নায় এক বিপুল প্রেরণা হয়ে ধরা দেয়।
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ সময়কে সাহিত্যের আকর করে তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, রজনীকান্ত সেন, গোবিন্দচন্দ্র রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সতীনাথ ভাদুড়ীসহ আরও অনেকে। প্রত্যেকের সৃজনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীতা করেছেন স্বদেশবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে; জাতি হিশেবে ইংরেজদের সমালোচনা তাঁরা করেননি, বরং ব্রিটিশদের অত্যাচারী মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করেছেন। এখানে এই বিষয়টি বলে রাখা ভালো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা পোলিশ সাহিত্যের চারভাগের একভাগ পাওয়া যাবে, যাতে নাৎসীদের অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে জার্মান জাতিকে অপমান করা হয়েছে। কিন্তু একটি পরাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও তৎকালীন বাঙলা সাহিত্যিকরা এটা করেননি। এখানেই ভাষার স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার জোর।
আগে একবার বলেছি, বাঙলা সাহিত্যের গতিপথ আমার বিচারে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমীকরণের অনুগামী। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের যে উদারনৈতিক ধারণা এসেছে, তা পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবোধ ধারণা থেকে ভিন্ন। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ বাঙলা সাহিত্যের রাজনৈতিক প্রকাশ। ‘দেশাত্মবোধ’ এই ভাষার সাহিত্যে যেভাবে প্রোথিত হয়েছে, তার সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে সংগ্রামের আখ্যান— কেননা, ভাষা হিশেবে বাঙলাকেও সংগ্রামের মাধ্যমেই তার জায়গা করে নিতে হয়েছে। ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যেমন বাঙলা সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে উঠেছিল, তেমনি এই স্বাধীনতা ও তার স্বরূপের প্রকাশও ক্রমেই স্বাধীনতার বিষয় হয়ে উঠতে থাকে।
এই বিকাশমান পর্দায় ১৯৪৭ সালের দেশভাগ একটি বড়ো ফাটল। সেই ফাটল দিয়ে রক্তধারার মতো গড়িয়ে যাচ্ছে সাহিত্যের দ্বন্দ্বমুখরতা। ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা বা দর্শন প্রভাব রেখেছে সাহিত্যের জাগরণে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের ক্রমবিবর্তিত রূপ যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পাই; কিংবা করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখেন— ‘অয়ি মা ভরণি, অমৃতস্তনি ধরণি/ ত্রিভুবন-মনোহারিণি… নমো নমো মম জননী’— আমরা তাতে তীব্র স্বদেশিকতার এক প্রেমময় রূপ খুঁজে পাই। অবনীন্দ্রনাথ যেমন সৌন্দর্যের রীতি ও ঢঙে মনের বিদ্রোহকে প্রকাশ করেছেন, তেমনি এক প্রশান্তিময় রচনারীতি তখনও রাজনৈতিক বক্তব্যকে ধারণ করেছে। এই ধারায় অবশ্য ভারতী পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল।
মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন যখন ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে, বলাই বাহুল্য, তাতে মহাত্মা গান্ধী আর খুব বেশি প্রাসঙ্গিক থাকছেন না। ফলে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে ইংরেজবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সুস্পষ্ট কয়েকটি বিভেদরেখা পাওয়া যায়। ইংরেজবিরোধীতা যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামের দিকেই চূড়ান্তভাবে ধাবিত হবে— এ কথা অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা কংগ্রেসের চেয়েও ভালো বুঝেছিলেন। ফলে বাঙলা সাহিত্যের স্রোতরেখাও বিভক্ত হয়ে গেলো। চিন বা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক কাঠামো তখন ভারতবর্ষের তরুণ বিপ্লবীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছেন পথের দাবি, যার মূল চরিত্র সব্যসাচী তৈরি হয়েছে বিপ্লবী এম এন রায়ের আবহে। তবে ১৯৪০ সালের পর যেহেতু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাষা বদলে যেতে থাকে, মহাত্মা গান্ধী বা পণ্ডিত নেহেরু যেহেতু আর এককভাবে ভারতীয় রাজনীতির দিকপাল হিশেবে রইলেন না; সেহেতু বাঙলা সাহিত্যেও একটি প্রবল ঝাঁকুনি তৈরি হয়। একজন সামান্য কলমচি হিশেবে আমি যদি খানিকটা সাহস দেখিয়ে বলি যে, ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আবির্ভাব এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী (১৯৪৫) উপন্যাস একই সূত্রে গাঁথা— তবে পাঠক আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন নিশ্চয়ই। যদিও জাগরী উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ছিল ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, কিন্তু গান্ধী প্রণীত রাজনৈতিক বৃত্তে থেকেই তিনি সুভাষ বসুর চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন।
পূর্ব বাঙলাও তখন জ্বলছে। একে একে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নেমে আসছে নানা ধরনের নিপীড়ন আর অত্যাচার। সে সময়ে বরিশালে বসে গঙ্গাচরণ নাগের মতো একনিষ্ঠ স্বদেশীকর্মী লিখে ফেললেন রাখী-কঙ্কন। এই উপন্যাসের মাধ্যমেই আমরা স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব-বঙ্গীয় চিত্রটি পাই।
১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব উদ্বোধন আমরা লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থানের পর দৃশ্যতই বাঙলা সাহিত্যের অক্ষবদল ঘটে। বাঙলার লক্ষ-কোটি মানুষের মতো উদ্বাস্তু হয় বাঙলা সাহিত্য। ফলে সাতচল্লিশ-উত্তর বাঙলা সাহিত্য সচেতনভাবেই স্বয়ম্ভূ, বেপোরোয়া, ঘরছাড়া, বিপ্লবী এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহীও। দেশভাগের মাত্র এক বছর পরে বাঙলা সাহিত্যের আপাত নিরাপদ কবি হিশেবে পরিচিত জীবনানন্দ দাশ লিখলেন জলপাইহাটি (১৯৪৮) উপন্যাসটি। এক প্রবল-প্রমত্তা হূদয়াকাশ যেনো নিঙড়ে বেরিয়ে এলো বাঙলা সাহিত্যের উঠোনে। এই হূদয়াকাশের রক্তাক্ত আলোতেই পরবর্তী প্রায় এক দশক ধরে নির্মিত হয়েছে বাঙলা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ভাষ্য— উদ্বাস্তু ভাষ্য, ঘর হারানোর কণ্ঠস্বর যাতে গোপনে নথিভুক্ত হয়েছে রক্তে আর পূর্ণিমায়, বিষাদ আর ব্যবচ্ছেদে। কেবল বুড়ি ছোঁয়ার মতো করে যদি ছুঁয়েও যেতে চাই, তবুও মনে পড়বে প্রবোধকুমার সান্যালের হাসুবানু (১৯৪৮), অবিনাশ সাহার প্রাণগঙ্গা (১৯৪৯), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১) ও সার্বজনীন (১৯৫২), সাবিত্রী রায়ের স্বরলিপি (১৯৫২), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাঝি (১৯৫৫), আবু ইসহাকের সূর্যদীঘল বাড়ি (১৯৫৫), আবুল ফজলের রাঙাপ্রভাত (১৯৫৭), প্রতিভা বসুর সমুদ্রহূদয় (১৯৫৯), অমিয়ভূষণের গড় শ্রীখণ্ড (১৩৬০ বঙ্গাব্দে পূর্বাশা পত্রিকাতে প্রকাশিত) ইত্যাদি। তবে অজিত দাসের ভাগফল (১৯৫৬) আর অমরেন্দ্র ঘোষের ভাঙছে শুধু ভাঙছে (১৯৫১) উপন্যাস দুটিকে সাতচল্লিশ-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গভিত্তিক পার্টিশন সাহিত্যের সূচনাবিন্দু বলা যেতে পারে।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ইতিহাসের যে কোনো বিচারেই একটি অবিনশ্বর ঘটনা— সাহিত্যের জন্য তো বটেই। এই একটি ঘটনা থেকেই আমরা পৃথিবীর তাবৎ ভাষার সঙ্গে বাঙলা ভাষার রাজনৈতিক পার্থক্যটি খুঁজে পাই। সাহিত্য সাধনার জন্য রাষ্ট্রভাষা গুরুত্বপূর্ণ নয়; কিংবা বলা যেতে পারে— রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনার জন্যও সাহিত্যিক ভাষা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদের চিহ্ন হিশেবে ‘ভাষা’র উদ্বোধন যে কোনো জাতির স্বাধীনতার পূর্বশর্ত। এখানেই আলোচনাটির সারবত্তা বোঝা যায় যে, কেনো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে তৎকালীন সাহিত্যের সামগ্রিক সত্তায় এক ব্যাপক ঢেউ জাগে— এই ঢেউয়ের রাজনৈতিক চরিত্র অবশ্য চট্ করে ধরে ফেলা যাবে না। এটা বুঝতে হলে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা না করার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর যতো রকমের অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র রয়েছে তা বিবেচনায় আনতে হবে।
দীর্ঘ সময় ধরে যে সংস্কৃত ভাষার সামনে বাঙলাকে ব্রাত্য বানিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই ভাষাকেই রাজনৈতিক প্রয়োজনে সংস্কৃত ভাষার দোসর বানানো হলো। ফলে শুরু হলো বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ‘ইসলামি জিহাদ’। ভাষা হিশেবে বাঙলার জন্য এটি সম্ভবত অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য যে, তাকে ইসলাম ও হিন্দু— উভয় ধর্মের ষড়যন্ত্রকেই মোকাবেলা করতে হয়েছে। আদিপর্বে হিন্দু ধর্মের পুরোহিতরা একে ব্রাত্য ভাষা বলে দূরে ঠেলেছে, পাকিস্তান আমলে মোল্লা-মৌলবিরা একে হিন্দুয়ানি ভাষা বলে দূরে ঠেলেছে। ফলে ভাষাতাত্ত্বিকরা যদি অনুমতি দেন তো আমি সবিনয়ে জানাতে চাই— বাঙলা ভাষা এত ষড়যন্ত্রের পরও সর্বক্ষেত্রে তার ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে। দাড়ি-টুপি-পৈতার সংকীর্ণ উঠোন ছেড়ে বাঙলা মানবমুক্তির আকাশে ডানা মেলেছে।
কিন্তু সাহিত্য যেহেতু ভাষার মতো শক্তিশালী নয়, সেহেতু রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাতে সে আক্রান্ত হয়। ফলে পাকিস্তান আমলে যেমন, তেমনি স্বাধীন বাঙলাদেশেও আমরা দেখি সাহিত্য পরাজিত হয়। মৌলবাদেরও সাহিত্য হয়, সাম্প্রদায়িক অপোগণ্ডরাও কবিতা-গল্প-উপন্যাস লেখে এবং সভ্যতার দেয়ালে বাঁধিয়ে রাখার মতো ইতরদের আত্মজীবনীও সাহিত্যনামা হিশেবে প্রচারিত হয়। এখানেই বোধ করি সাহিত্য তার ভাষার সত্তা থেকে বিচ্যুত হয়। ফলে এই লেখাটি যে প্রশ্ন থেকে শুরু করেছিলাম, অসামান্য সব লেখকরাও কীভাবে গণহত্যা বা সাম্প্রদায়িকতার সাফাই গান— এতক্ষণে তার উত্তরটি সম্ভবত পাওয়া গেলো। মূল কথাটি হলো— ভাষা রাজনৈতিক দর্শনের পথে হাঁটে, কিন্তু সাহিত্য মাঝে মাঝে পা ফসকে মতবাদের রাস্তায় চলে যায়। ভাষা শুদ্ধ, ফলে তাকে অনুসরণ করা সাহিত্যও পথভ্রষ্ট হয় না; কিন্তু যে সাহিত্য তার মূল ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে অনুসরণ করে না, তার স্খলন ঘটতে বাধ্য।
এই অনুসরণ অর্থ ভাষাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ করে তার পথরেখা অবলোকন করা। পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ মানে ভাষার দর্শনগত উদ্বোধন ও বিকাশের সংগ্রামকে পাঠ করা। রবীন্দ্রনাথের অসামান্যতা এ কারণে নয় যে তিনি কলোত্তীর্ণ রচনাসম্ভার রেখে গেছেন; বরং এই একটি মাত্র কারণে যে, বাঙলা ভাষার আত্মমর্যাদাবোধকে তিনি আজীবন ধারণ করেছেন, আর এজন্যই তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইংরেজদের দেয়া ‘নাইট’ উপাধি বর্জন করেছিলেন। শ্যামা সঙ্গীত, দেশের গান, ইসলামি ভাবাদর্শের গান-কবিতা রচনা করেছেন বলেই কাজী নজরুল ইসলাম অসাম্প্রদায়িক— ব্যাপারটা তেমন নয়; বরং তাঁর আকাশমুখী প্রতিভায় বাঙলা ভাষার অসাম্প্রদায়িক চরিত্রটি ধরা পড়েছে, তিনি তারই অনুগামী থেকেছেন তাঁর সাহিত্যে।
কোনো একটি ভাষার অক্ষরে লিখলেই সে ভাষার সাহিত্য হয়ে ওঠে না— যেমন মধুসূদন দত্তের ইংরেজি সাহিত্য হয়নি। আবার কোনো একটি ভাষা কারও মাতৃভাষা হলেও তিনি সে ভাষাতে সাহিত্যচর্চা করতে পারেন না— অসংখ্য বাক্য রচনা করতে পারেন হয়তো, কিন্তু তাতে সাহিত্য রচিত হয় না। কোনো একটি ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে হলে সেই ভাষার বিকাশপর্বটি জানা চাই। তার গড়নে-মননে প্রেম রাখা চাই। তার আগুন ও অশ্রুর ঠিকুজি জানা চাই।
এই সত্যটুকুই ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধ নিরূপনে সবচেয়ে কার্যকরী বলে আমি মনে করি। প্রতিটি ভাষার একটি রাজনৈতিক আখ্যান থাকে, থাকতেই হয়— কেননা, রাজনৈতিক বিকাশ ছাড়া ভাষা বিকশিত হতে পারে না। ফলে প্রতিটি ভাষার সাহিত্যেই রাজনীতি অবধারিত। রাজনৈতিক সাহিত্য বলে তাই ‘পার্টিশন সাহিত্য’ বা ‘রোম্যান্টিক সাহিত্য’- এর মতো আলাদা কোনো শাখা হতে পারে না। তাই সাহিত্যে রাজনীতি অবশ্যম্ভাবীভাবে বিদ্যমান— সেই রাজনীতি কোন পক্ষের— সেটা নির্ভর করবে ওই ভাষার রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপর এবং সাহিত্যিক সেই ইতিহাসের কোন দিকটি সম্বন্ধে অবগত বা অনুগত।
অন্ধকারের অনন্ত নক্ষত্রবীথি
এই লেখার শিরোনাম— ‘মদন তাঁতির মুদ্রাদোষ’। মদন তাঁতি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মদন তাঁতিই আমার জানা বিশ্ব সাহিত্যের রাজনৈতিক আবহে নির্মিত একটি কাল্ট— যাঁর কাছে রাজনৈতিক আদর্শ মুকুলিত হয়েছিল কোমলগান্ধারে। দ্বন্দ্ব শাশ্বত— এ কথা কার্ল মার্কস না বললেও আমরা বুঝতে পারতাম; কারণ সম-অসম অসংখ্য দ্বন্দ্বে পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে, সামনের দিকে চাকা ঘুরাচ্ছে সভ্যতা। জনরোষমুখরিত এই পৃথিবীতে রক্তবর্ণ মৃত্তিকায় সাহিত্যের পদাঘাত বা চুম্বন তুলে রাখার সমস্ত দায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য-তন্বী আসলে প্রচ্ছন্ন স্বদেশ— এই বক্তব্য ততখানি রাজনৈতিক, ইতিহাসের প্রণয়-প্রার্থিনীরা যতখানি বাস্তবধৃত। এ কারণেই মানুষের আত্মার বিবরণী চিরকালই রাজনৈতিক এবং তার জটিল কোলাজ আসলে ভাষাতে জীবন্ত। রক্তগোলাপে, গীতিকবিতায় বা ইতিবাচনে সাহিত্য খানিক বিবরণ মাত্র— তৃতীয়ার কাস্তে-সদৃশ চাঁদের তলায় আলোর বিকল্প। সাহিত্য ইতিহাস সৃষ্টি করে না, তাকে পুনর্বিন্যাস করে জীবনে-মহত্ত্বে-তুচ্ছতায় ও গ্লানিতে তাকে চিত্রার্পিত করে মাত্র। ফলে রাজনীতির সঙ্গে তার করবন্ধন আদতে স্রষ্টার আত্মাবলোকন ছাড়া কিছুই নয়।
ভাষার রাজনৈতিক বিকাশ আর সাহিত্যের মতাদর্শজনিত সংঘাত এক নয়। প্রথমটি তাই শাশ্বত— যেন মনীষার কারুবাসনা। আর দ্বিতীয়টি? তাৎক্ষণিকতার ইচ্ছেপূরণ কিংবা মেধাহীন চাঞ্চল্য।

কথাসাহিত্যিক ও ব্লগার। জন্ম ১৯ ফাল্গুন, ১৩৯৩: ০৩ মার্চ, ১৯৮৭, ঢাকায়। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১২ টি।