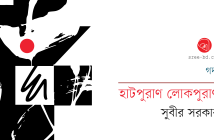কখন কোন ব্রহ্মমুহূর্তে গল্প লেখায় হাতে খড়ি তা সুনির্দিষ্ট করা বলা মুশকিল। তবে মনে আছে লেখালেখির শুরুতে ছিল শিশুতোষ ছড়া চর্চা। দিনে তার দু-চারটা বানানো। কিন্তু অন্ত্যমিলের সে কারবারের পুঁজি অচিরেই ফুরায়ে যায়। তখন গদ্যে নামি। শিশুতোষ গল্পের ঘেরাটোপে ঘুরতে শুরু করি।
তখন সভা-সমিতি আড্ডায় শুনি— ‘তোর লেখা “সাতভাই চম্পা”য় ছাপা হয়নি। তুই আবার কিসের লেখক, অ্যাঁ, যা ছো. . .।’ সভাপতির গুরুগম্ভীর স্বরও কানে আসে— ‘সাতভাই…য়ে কারো লেখা একবার ছাপা হলে তার লেখক হবার সব বাধা কেটে যায়।’
‘সাতভাই চম্পা’ হচ্ছে অধুনা বিলুপ্তির চাদরে মোড়া দৈনিক বাংলা পত্রিকার শিশুতোষ পাতা। আকার-আয়তনে সে চিড়ে-চ্যাপটা, মাত্র আধ পাতাজোড়া তার অবয়ব। কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তিতে বিশাল ও বিপুল। ভুবন না হলেও ঢাকার শিশু-সাহিত্য অঙ্গনজুড়ে তার প্রতাপ।
কিন্তু হিসাব করে দ্যাখি, তখনকার চালু অনেক পত্রপত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হলেও ‘সাতভাই..’য়ের সাথে তাদের কারো কোনো দেখা-সাক্ষাত হয়নি। তাদের হাতের মুঠোয় আমার কোনো লেখা স্থান পায়নি। ওহ! তাহলে আমার লেখক হওয়া এখনো বাকি? কীভাবে তা পূরণ করা যায় তার সুলুক সন্ধানে নামি।
তাদের হাতের মুঠোয় আমার কোনো লেখা স্থান পায়নি। ওহ! তাহলে আমার লেখক হওয়া এখনো বাকি? কীভাবে তা পূরণ করা যায় তার সুলুক সন্ধানে নামি।
শুনি, তাদের বাপ, মানে পাতার সম্পাদক যেমন সাংঘাতিক কড়া তেমনি অসম্ভব জহুরী। কারো লেখা দু-চার লাইন পড়েই বলে দিতে পারেন তার হবে নাকি হবে না। তাই লেখা পছন্দ না হলে এতোটুকু মায়াদয়া দেখান না। সাথে সাথে মুখের উপর ছুড়ে মারেন, রুম থেকে বার করে দেন।
তাঁর নামটাও কেমন সৃষ্টিছাড়া, আদি ও অকৃত্রিম— আফলাতুন। এক শব্দে আগাপাশতলা সব। আগে-পিছে আর কিছু নাই। এ নাম নিয়া তিনি যেমন আলাদা, সর্বসাধারণের বাইরে, কামেও তেমনি, লেখা সম্পাদনার রীতিনীতিতে আর সব শিশুতোষ পাতার সম্পাদকদের থেকে ভিন্নতর। তাই আর সব পত্রিকার পাতার জন্য সপ্তাহের যেকোনো দিন লেখা জমা দেয়া গেলেও ‘সাতভাই চম্পা’য় কেবল সোমবারে, যতদূর মনে পড়ে, সে সুযোগ ঘটে। আর পাতা বার হয় বুধবারে।
তাই এক সোমবার, কলেজের ক্লাস ফাঁকি দিয়া, সকাল ১১টার দিকে দুরুদুরু বক্ষে দৈনিক বাংলা অফিস, পল্টন থেকে মতিঝিলে পা দেবার আগ মুহূর্তে হাতের ডাইনের কোণায় খাড়া বহুতল ভবন, এখন যেখানে যুবকর্মসংস্থান ব্যাংক, তার তিনতলায় গিয়া হাজির হই।
দ্যাখি, আরও জনপাঁচেক আগে থেকেই হাজির। বারান্দায় সবাই ঘুরঘুরে ব্যস্ত। কেননা আফলাতুনভাই তখনো আসেননি। রুমের দরজা তাই খোলা হয়নি। কিন্তু ঘুরঘুরকারীদের পানে তাকায়ে দ্যাখি কেউ-ই আমার পরিচিত নয়। সব অপরিচিত মুখ। ফলে যেন অথৈ জলে পড়ে যাই। নিজেরে অসহয় মনে হয়। তাই একবার ভাবি ফিরে যাই, আরেকদিন আসা যাবে। কিন্তু ঠিক তখন আমার পরিচিত একজন এসে হাজির হয়। তার লেখা প্রায় নিয়মিতই ‘সাতভাই চম্পা’য় স্থান পায়। ব্যস, আমি যেন তৃণখণ্ড পেয়ে যাই। সাথে সাথে তাই তারে আঁকড়ে ধরি। তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াই। ফলে ভয়-ডরটা একটু দূরে হটে।
আধ ঘন্টাখানেক পর আকারে-প্রকারে উঁচা-লম্বা এবং পুরু ফ্রেমের চশমা ও এলোমেলো, আয়রণ-ইস্তিরিবিহিন প্যান্ট-শার্ট পরা একজন আসতেই সবাই টটস্থ হয়ে ওঠে। তাদের দেখাদেখি আমারও সতর্ক হতে হয়। পরিচিতজন তখন কানের কাছে ফিসফিসায়— ‘আফলাতুনভাই’।
আমরা সবাই তাতে স্থান নেই। আর আফলাতুলভাই টেবিলে বসতেই, বলা নাই কওয়া নাই, প্রথাবন্ধ নিয়মের মতোই যেনবা, সবাই তাদের লেখা তাঁর সামনে রাখে। আমিও তাদের অনুসরলে আমার লেখাটা পকেট থেকে বার করে টেবিলে সমর্পণ করি।
তিনি গম্ভীর মুখে রুমের তালা খুলে ভেতরে পা দেন। আমরাও তাঁর পিছু পিছু ঢুকি। দ্যাখি, ছোটো, অপরিসর রুম। ভেতরের দিকে মাঝারি সাইজের একটা টেবিল আর দুপাশের দেয়াল ঘেঁষে খানপাঁচেক চেয়ার। আমরা সবাই তাতে স্থান নেই। আর আফলাতুলভাই টেবিলে বসতেই, বলা নাই কওয়া নাই, প্রথাবন্ধ নিয়মের মতোই যেনবা, সবাই তাদের লেখা তাঁর সামনে রাখে। আমিও তাদের অনুসরলে আমার লেখাটা পকেট থেকে বার করে টেবিলে সমর্পণ করি।
তারপর রায়ের অপেক্ষায় থাকি। আর এখানকার প্রথা অনুযায়ী রায় তো মাত্র দুই প্রকার— হয় ফাঁসির আদেশ— লেখাটারে একেবারে খারিজ করে দিয়া ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেয়া, নয়তো খালাস— একেবারে পাকাপোক্ত মনোনয়ন, আগামী সংখ্যায় ছাপা। তার কোনটা যে জুটবে আমার লেখাটার ভাগ্যে সে ভাবনায় হার্টবিট বেড়ে যায়। হাজার মাইল বেগে সে ছুটতে শুরু করে।
কিন্তু আফলাতুনভাই তার কোনো পথেই না গিয়া একটার পর একটায় সবগুলো লেখার উপর একবার চোখ বুলায় নিয়া আবার সবার মধ্যে সেগুলো ভাগ করে দেন। একজনের লেখা আরেকজনরে দিয়া বলেন— ‘পড়ো, পড়ে বলো কেমন অইছে?’
দ্যাখি, সবাই আফলাতুনভাইয়ের পরিচিত। তিনি তাদের নাম ধরে ডাকেন। আমিই কেবল নতুন। তাই হয়তোবা আমারে কোনো লেখা দেন না। আমি তাই চুপচাপ বসে থাকি। তবে সৌভাগ্যবশতই হয়তোবা আমার লেখাটা পড়ে আমার পরিচিতজনের হাতে।
যেহেতু বেশিরভাগ লেখাই দু-চার লাইনের ছড়া-কবিতা বা লিমেরিক, তাই অল্প সময়েই তা সবার পড়া হয়ে যায়। কিন্তু আমার লেখাটা গদ্য, শিশুতোষ গল্প এবং বেশ বড়ো, তাই তার আগাগোড়া সায়ের করতে আমার পরিচিতজনের অনেক সময় লাগে। ততক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকে। পড়তে দেয়া লেখা সম্পর্কে কেউ কিছুই বলে না। আর আমি তখন যেন ফাঁসি অথবা মুক্তির রায়ের অপেক্ষায় কম্পমান আসামি হয়ে থাকি।
অবশেষে আমার পরিচিতজন পড়া শেষ করে মাথা তোলে— ‘লেখাটা ভালো ছাপা যায়।’ আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তখন বাকিরাও তাদের মন্তব্য হাজির করে। তাতে কোনো কোনোটা মনোনীত হয়। সেগুলো আফলাতুনভাই হাতে নিয়া নিজে একবার পড়ে ছাপতে দেবার প্রক্রিয়া শুরু করেন। আবার কোনো কোনোটা ফেরত দেন— ‘আগামী সপ্তাহে নতুন লেখা নিয়া এসো।’
পুরাটা না হলেও বেশ কিছু অংশ পড়েন হয়তোবা। তার মাথায় গিয়া আমার পানে ফেরেন— ‘লেখাটা ছাপা যাবে। কিন্তু তোমার এতো বড়ো নাম ছাপানোর জায়গা হবে না।’
একদম শেষে আমার লেখাটা হাতে নেন। পুরাটা না হলেও বেশ কিছু অংশ পড়েন হয়তোবা। তার মাথায় গিয়া আমার পানে ফেরেন— ‘লেখাটা ছাপা যাবে। কিন্তু তোমার এতো বড়ো নাম ছাপানোর জায়গা হবে না।’
আমার নামটা তখন চার অক্ষরের। আরব দেশের সর্বশেষ সেমেটিক ধর্মের অনুসারী হিসাবে তার পয়গম্বরের নাম দিয়া শুরু আর ডাকনাম দিয়া শেষ। কিন্তু এতো বড়ো লেখা, প্রায় পাঁচশ শব্দের গল্প ছাপা গেলে তার সাথে আমার বাপের দেয়া, সার্টিফিকেটে খোদাই করা চার শব্দের নামটা ছাপা যাবে না কেন? আমি বিস্ময়ে তাঁর পানে তাকাই।
— হ্যাঁ, এতো বড়ো নাম আমার পাতায় ছাপা হয় না। তবে তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে ছোটো করে দিতে পারি। কিন্তু এখন থেকে সেটাই ব্যবহার করতে হবে। বলো রাজি?
আমার পরিচিতজন ইশারায় আমারে রাজি হতে বলে। তাছাড়া আমার তখন লেখক হবার পথের সব বাধা দূর করার, মানে ‘সাতভাই চম্পা’য় লেখা ছাপানোর খায়েস আকাশ ছোঁয়া। তার জন্য জান কোবরান দিতেও প্রস্তুত। আর এতো সামান্য নাম। আমি তাই ঘাড় কাতাই, রাজি হয়ে যাই।
আফলাতুনভাই তখন প্রথমেই নামের শুরুতে ধর্মের নিশানবাহী ‘মুহম্মদ’-এর উপর কাঁচি চালান। তার গায়ে মোটা করে ক্রস চিহ্ন আঁকেন। তারপর মাঝ বরাবর ভুঁড়ির মতো ফুলে-ফেঁপে থাকা ‘উল’-এর উপর এবং সবশেষে ডাকনামটারে একেবারে ছেঁটে ফেলে দেন। মুণ্ড কাটা লেজ ছাঁটা ও ভুঁড়ি বাদ দেবার পর সে হয়ে দাঁড়ায় ‘জিয়া হাসান’।
— যাও, বুধবারে পাতা দেখো।
হ্যাঁ, ‘সাতভাই চম্পা’র পরের সংখ্যাতেই অর্ধেকেরও বেশি জায়গা নিয়া আমার লেখাটা ছাপা হয় এবং আমি ‘লেখক’ হয়ে উঠি। তবে ‘হাসান’ থেকে ‘হাশান’ হয়ে ওঠার গল্প যেমন আলাদা তেমনি তার গোত্রও ভিন্ন। তা না হয় আরেকদিন করা যাবে।

জন্ম ১৯৬৬ সালে পিরোজপুর শহরে। তিনি ঢাকা বিশ্বদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে মাস্টার্স পাস করে সাংবাদিকতায় পা দেন। দৈনিক খবর, ভোরের কাগজ ও প্রথম আলো পত্রিকায় বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিকতা শেষে তিনি দেশের অন্যতম বৃহৎ এনজিও ব্র্যাক-এ মিডিয়া ম্যানেজার হিসাবে জয়েন করেন। বর্তমানে তিনি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল স্কলাসটিকায় যোগাযোগ কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করছেন। তার লেখা বইগুলোর মধ্যে রয়েছে : ‘সোনায় সোহাগা কাহিনি’ (গল্পগ্রন্থ) ‘জোসনার সাথে মোলাকাত ও অন্যান্য’ (স্মৃতিগদ্য) ‘খেয়ালি ভুঁই ও তার ফসল বিন্যাস’ (গল্পগ্রন্থ), ‘সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়’ (গল্পগ্রন্থ), ‘শোনো বাতাসের সুর’ (হারুকি মুরাকামির উপন্যাসের অনুবাদ) ‘পাসপোর্ট’ (হার্তা মুলারের উপন্যাসের অনুবাদ) ‘বাঁক বদল’ (মো ইয়ানের উপন্যাসের অনুবাদ) ‘চোর দেখার ফাঁদ’ (কিশোর গল্পগ্রন্থ) ‘বুড়িগঙ্গায় কালো জাহাজ’ (কিশোর গল্পগ্রন্থ) এবং ‘নির্বাচিত ছোটগল্প’ (সম্পাদনা)।