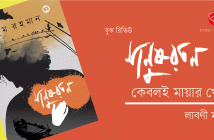আনিসুর রহমান (জ. ১৯৯৪) স্বল্পপ্রজ লেখক। কিন্তু এই ‘স্বল্পপ্রজ’ বিষয় থেকে যদি ভালো সৃষ্টি সম্ভব হয়, তো সেই স্বল্পপ্রজতাকে বোধহয় দোষ না দিয়ে প্রশংসাই করা যায়। এই প্রতিযোগিতার যুগে কম লিখে বেশি হওয়ার যে নিদর্শন তিনি রেখেছেন, তা তারিফ করার মতো। সাত বছর ধরে লিখেছেন একটি গল্পগ্রন্থ! প্রকাশ হলো এ বছর। তাঁর লেখার বিষয় আর ঢং প্রচলিত আর প্রথাগত পদ্ধতি অনসৃত হয়েই তৈরি হয়েছে; কিন্তু কৌশলের বেলায় তিনি স্বতন্ত্র। কারণ গল্পলেখার গৎবাঁধা ধারণা থেকে তিনি বের হননি। হলে গল্প হতো না; তিনি গল্পকারও হতেন না। কিন্তু বাংলা ছোটোগল্পের বিবেচনায় তাঁর গল্প এখন যে কারো কাছে একটু ভিন্ন আমেজ আর আবেগ নিয়ে হাজির হবে, হলফ করে তা বলা যায়। যে কেউ তাঁর গল্প পাঠের বেলায় এই সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আমি তাঁর গল্পের জগতকে তুলনা করব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র (১৯২২-১৯৭১) গল্পের জগতের পরবর্তী প্রয়াস হিসেবে। সেটাই আমার বিবেচনায় সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হবে বলে মনে করছি। আরও কেউ কেউ থাকবেন, আগেপিছে। সেটা জরুরিও বটে।

সিসিফাস শ্রম | আনিসুর রহমান | প্রকরণ: ছোটোগল্প | প্রচ্ছদ: মাসুক হেলাল | প্রকাশক: প্রথমা | মুদ্রিত মূল্য: ২৫০ টাকা | বইটি সংগ্রহ করতে এখানে ক্লিক করুন।
২.
সিসিফাস শ্রম (২০২৪) এই গল্পগ্রন্থের নাম। নয়টি গল্প নিয়ে এই গল্পগ্রন্থ। এই কয়টি গল্প দিয়েই তাঁর স্বতন্ত্র অবস্থান তিনি জানান দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি গল্পই ভিন্ন। ভিন্ন প্রতিটি গল্পের বিষয়, আর গল্প লেখার কৌশলও। এই গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প ‘এপিটাফ’। মৃতের কবরে প্রোথিত প্রস্তরফলক ও প্রস্তরফলকে যা লেখা থাকে তাই মিলে এপিটাফ। কিন্তু এই ‘এপিটাফ’ নামের গল্পটি আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা আর দুনিয়ার সঙ্গে না পেরে ওঠার এক মহৎ শিল্পরূপ। জীবনের নিয়তি আর নিরর্থকতার এক দারুণ সন্নিবেশ সম্পাদিত হয়েছে এই গল্পে। গল্পের কথক যে মানুষটি, সে বেঁচে আছে, আবার বেঁচে নেই। কিন্তু বেঁচে থেকেই সেই মানুষটি মৃত হিসেবে নিজেকে দাবি করছে। কেন এমন দাবি তাকে করতে হচ্ছে? জিনের কলাকৌশল যেন এই মানুষকে নিয়তই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মানুষটি তার জীবিত জীবনের পথটি হারিয়ে মৃতের রূপকল্পে আসীন হয়ে গেছে। সেখান থেকে সে যে ফিরে আসবে, সেই শক্তিটি আর নেই।
কিন্তু প্রশ্ন তো এখানেই, কেন মানুষটি আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারছে না। না পারার কারণই বা কী? এর বিশ্লেষণ বোধহয় এই গল্প পাঠের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। আনিসুরের গল্পের প্রকাশভঙ্গি যেহেতু এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কারবার করে না। জানায় না। পাঠককে তাই একটু চতুর হতেই হয়। পাঠক যদি মনোনিবেশের সমগ্র কলকব্জা স্থির না রাখতে পারে, তো পাঠকের জন্য এই গল্প একটি সামান্য রূপকথা হয়ে উঠবে কেবল। তখনই এই বিষয় নিয়ে গল্প হওয়া না-হওয়া; বোঝা না-বোঝার মতো বিষয় সৃষ্টি হবে। ফলে তৈরি হবে সংকটের; কিন্তু সমাধানকল্প কী হবে, তা তো আগেই বলেছি।
বংশপরম্পরায় অর্জিত নানা বিষয়-আশয় মানুষকে মৃত্যুর আগ অবধি বহন করতে হয়। মানুষ তা বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ভেতর দিয়ে অর্জন করে। আনিসুরের এই গল্পের কথক তেমনি কাজ-কারবার করে। তার পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া নানা রোগ-ব্যাধি আর নানা মানসিক সংকটের বিষয় এই কথককে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলতে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় এই গল্পে ক্রমাগত কথা বলে চলা কথক কি একাই এমন একটি অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে? ধরুন, এই যে বাস্তবতা আনিসুর তাঁর গল্পের কথকের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেন, তা কি একান্তই তাঁর নিজের আলাপ নয়? এই প্রশ্ন প্রশ্নই রয়ে যাবে, যদি না এর সদুত্তর গল্পকার আমাদের না দেন। কিন্তু এই বিষয় তো গল্পকারের কাছে প্রশ্ন করে করে পড়া ও করা সম্ভব নয়। পাঠককেই এই ভার নিতে হবে; মাঝে-মাঝে নিতে হয়। ধরা যাক, পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের কোনো গ্রাম-সমাজে যে মানুষটি বাস করছে, সেই মানুষটিকে এই গল্প পড়তে দিলে গল্পের ভেতরে প্রকাশিত কথকের বিপন্ন জীবন-বাস্তবতা সম্পর্কে একদমই ঠাহর করতে পারবে না। যদিও পঞ্চাশের দশকের আগেই কাম্যু-কাফকা-সার্ত্রের লেখায় এই জীবনের নিরর্থকতা, বিপন্নতার বিষয় ভুরি-ভুরি পাওয়া যায়। কিন্তু আমি যে কথকের জীবনের বিপন্নতা ২০২৪ সালে এসে বিচার করছি, তার পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। এই কথকের এপিটাফের চেয়ে কবর আর শ্মশান চেনাই বেশি যৌক্তিক ছিল। যেখানে কবর কিংবা শ্মশানে লেখা থাকে ‘স্বর্গীয়’ কিংবা ‘আখেরী সফর’। কিন্তু কোন পরিস্থিতির ভেতরে গল্পকার কথকের মুখ দিয়ে এমন ‘পশ্চিম-প্রভাবিত এপিটাফ’ নিয়ে হাজির হলেন? এই প্রশ্ন দেশ-কাল-সমাজের নিরিখে যে কাউকে ভাবাবে, যদি সে ভাবে।
মনে রাখা জরুরি যে, পশ্চিম আর পুবের ‘এপিটাফের’ মতো পর্যায়ে পৌঁছোতে বেশ সময় লাগার কথা। লেগেছেও তাই। পশ্চিম যখন যেখানে ছিল, পুব তো তা ছুঁতে পারে নাই। এই না পারার বিষয়ই গল্পের কথকের চিন্তার সত্যতায় স্পষ্ট হয়েছে।
মনে রাখা জরুরি যে, পশ্চিম আর পুবের ‘এপিটাফের’ মতো পর্যায়ে পৌঁছোতে বেশ সময় লাগার কথা। লেগেছেও তাই। পশ্চিম যখন যেখানে ছিল, পুব তো তা ছুঁতে পারে নাই। এই না পারার বিষয়ই গল্পের কথকের চিন্তার সত্যতায় স্পষ্ট হয়েছে। কথক যে বাস্তবতা ছুঁতে পেরেছে, সেই বাস্তবতায় এই সময়ের অধিকাংশ শ্রেণিবিন্যস্ত মানুষ বেশ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ত্রিশের আধুনিকতার বিচ্ছিন্নতার মনে হয় না ততোটা সত্যতা ছিল, যতোটা সত্য হয়ে উঠেছে এই সময়ে এসে। তাই গল্পকার এইরকম ব্যক্তিক বয়ান নির্মাণে সাহসী হয়েছেন। যা এই সময়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বেশ কার্যকরও বটে।
৩.
অ্যাবসার্ড জগতের যাত্রা ‘এপিটাফ’ গল্পে শুরু করলেন গল্পকার। সেই জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে প্রবেশ করলেন নতুন গল্প নিয়ে: ‘সেলেব্রেটিং সেঞ্চুরি উইথ আদুরী’। পূর্বে যে বিপন্নতা, তা ছিল একজন মানুষের বিবেচনায়, যার সঙ্গে পরিবার-সমাজ সর্বোপরি পরিপার্শ্ব থাকলেও ব্যক্তিই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিগত যাপিত জীবনের দুঃসহ আর দমবন্ধ পরিস্থিতিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই গল্পের বিষয় ভিন্ন: সামষ্টিক ক্রিয়ায় নির্মিত দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৩ সনের মহা দুর্ভিক্ষের বয়ানে পুরো দুনিয়ার ক্ষমতাকাঠামোর বিষয় এক নতুন ধারাপাতে বর্ণিত হয়েছে। সময় ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার বিন্যাস বদলে যায়। এই বিষয় মানুষের জীবনের বিন্যাসও বদলে দেয়। ধরুন, এই গল্পের আদুরী দুর্ভিক্ষের সময়ে যে পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল এবং তাতে তার শরীরের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল সেই পরিস্থিতি সে বহুদিন পরে পত্রিকায় দেখলো। কিন্তু ওই একই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে ভিন্ন প্রকল্পে।
অর্থাৎ, এর মাঝে সময় বদলেছে। শরীর-শুকনোকরণই হয়েছে বর্তমান সময়ের ফ্যাশনের মাপকাঠি। যে পরিস্থিতি আদুরীর কাছে না খেয়ে থাকার ফলাফল, আদুরী বহুবছর পরে দেখে সেই পরিস্থিতিই, মানে শরীরের পণ্যায়ণ, আর্থ-উত্পাদনের বিলবোর্ড হয়ে গেছে। প্রচারের যন্ত্র হয়ে গেছে। আদুরীর ওই সময়ে যা ঘটেছে তাও একরকম পণ্যায়ণ। সুজান সানটাগ তাঁর ‘অন ফটোগ্রাফি’তে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। ছবির গুরুত্ব আর রাজনীতি নিয়ে। এমনকি ছবির বাজারের সঙ্গেও আর্থ-আত্পাদনের সম্পর্ক আছে। আর খ্যাতি তো আছেই। জয়নুল আবেদিন এই দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেই বাজিমাত করেছিলেন। অর্থাৎ নারীর ‘স্লিম বডি’ দিয়ে যেমন বর্তমানে বাজারের অর্থের হিসেব-নিকেশ হতে পারে; তেমনি দুর্ভিক্ষের সময় অস্থিচর্মসার মানুষকে নিয়ে আর্থ-উত্পাদনের প্রচারের বিষয়ও সংঘটিত হতে পারে।
কিন্তু এই গল্পে এসবের চেয়েও বেশি কিছু আছে। যা প্রশ্ন আকারে এসেছে। প্রথমত দুর্ভিক্ষ কেন ঘটলো; কারা এর পেছনে কাজ করেছিল। ‘নয়নচারা’ বলে একটা গল্প ওয়ালীউল্লাহ্র আছে। সেই গল্পে ওয়ালীউল্লাহ্ যেভাবে প্রশ্ন করেছেন, আনিসুর তার চেয়ে বেশি প্রশ্ন করেছেন। বেশি তিনি বর্ণনায় স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। ক্রমশই ক্ষমতাকাঠামোকে প্রকাশ করেছেন মকারির ভেতর দিয়ে। ফলে বিষয়টি স্যাটায়ার নয়, উইট নয়; যেন তার চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠেছে।
মিথের একটি বৃহৎ ভূমিকা সাহিত্যে থাকে। সাহিত্যিক সাহিত্যে যে কথা সিধেভাবে বলতে পারেন না, সেই কথা যদি মিথের মধ্য দিয়ে বলা সম্ভব হয়, তো সেই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। আনিসুর এই গল্পে রাম-লক্ষণের প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু এই বিষয় কোনোভাবে বিশেষ হয়নি; এবং আহামরি গুরুত্বকে সম্ভ্রমশালী করেনি। গল্পকার একটি অনির্দেশ্য পথকেই চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন সর্বদা। যে পথ আসলে দুর্ভিক্ষের সমান্তরেলে প্রতিষ্ঠিত। গল্পে এই মিথ ব্যবহার মিথের রূপকল্পকে খারিজ করে দিয়েছে। একেবারে মিথের বান্তবতার বাইরে গিয়ে বর্তমান বাস্তবতাকে খারিজ করেছে। ব্যাপারটি এই গল্পের প্রকৃত অর্থে গল্প হতে সহায়তা করেছে।
তবে এই গল্পে মাঝে মাঝে গল্পের চেয়ে বেশি গল্প আছে। মানে বাস্তবতাকে খারিজ করে দেওয়ার পরও অনেক বাস্তবই যেন রয়ে গেছে। যেমন মানুষ চালের বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে; কিংবা বহুদিনের ব্যবহৃত ও সঞ্চিত যে সামান্য সম্পদ তাও চালের বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে। এই বাস্তবতার জন্য দায়ী কে? সেই দায়ের ভারও আনিসুর দারুণ চাবুক হাঁকিয়ে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শ, দৃষ্টি আর কর্মের ভারে যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো এবং এই পরিস্থিতি একরকম অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডেরই নামান্তর, তা এই গল্পের বর্ণনায় স্পষ্ট হয়। উইনস্টন চার্চিলকে নিয়ে যে মাহাত্ম্যপূর্ণ বয়ান পুরো পশ্চিম-জগতে চালু আছে, সেই বিষয় পুরোপুরি খারিজ করেছেন গল্পকার। এই সত্য ইতিহাসেরও সত্য। কিন্তু গল্পে এসে বিষয়টি ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। এই গল্পের সংকট হলো এখানে আরও কিছু বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গ জুড়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু গল্পকার এমনভাবে শুরু করেছেন যে, গল্পের বিষয় ছাড়িয়ে আদুরী আসলে এখন কোন সময়ে উপস্থিত হয়েছেন তা আমাদের অজানা। একটা গুইসাপের জলে ডুব দেওয়া আর জল থেকে মাছ মুখে নিয়ে উঠার যে সময়—সেই সময়ের মধ্যেই গল্পের পুরো বয়ান শেষ হয়েছে। বিষয়টি আবার ছোটোগল্পে অবধারিতভাবে থাকতে হবে এমন একটি বিষয়, আকাঙ্ক্ষা বিষয়টিকে স্পষ্ট করে। ফলে সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়াতে পাঠকের দুঃখের বিষয় চাপা দিতেই হয়।
৪.
‘অচেনা মানুষ’ গল্পে এসে গল্পকার আবার আধুনিক মানুষের বিপন্নতাকে পুঁজি করে গল্প লিখলেন। বিপন্নতাবোধ, এই বিষয়ই তাঁকে যেন নতুনভাবে ভাবিয়েছে। গল্পের সূচনা হয়েছে পৃথিবীতে বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামো আর খাদ্যশৃঙ্খলা নিয়ে। অভিযোজন, টিকে থাকা, বিবর্তন—এই সমস্ত শব্দ এই গল্পকে বিশেষ করেছে। খাদ্যচক্রে আধিপত্য আর সাম্রাজ্যবাদের বিষয় একটি একচেটিয়া ধারণা হিসেবে দেখিয়েছেন গল্পকার।
বিপন্নতাবোধ মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তোলে। একা হয় মানুষ। এর চেয়ে বড়ো ব্যাপার, এই গল্পে বহু প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন গল্পকার। যেমন একটি বিষয়: ঠোঁটের জ্বলন্ত সিগারেটকে রূপকে কারখানায় জ্বলন্ত চিমনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ পুঁজির ক্ষমতাবলয়ে মানুষের যে নিয়তি, তাই তিনি স্পষ্ট করেছেন একটি লাইনে। এমন প্রসঙ্গ অহরহ পাওয়া যাবে এই গল্পে।
বোদলেয়ারের কবিতার বই ‘প্যারিস স্পিলিন’-এ ‘আউটসাইডার’ বলে যে কবিতা আছে, সেই কবিতার কয়েক পঙ্ক্তি এই গল্পের সূচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। বোদলেয়ারের কবিতার মৌল প্রপঞ্চ আধুনিক মানুষ ও তার নিয়তি। মানুষ হিসেবে ব্যক্তি যে নানাভাবে অসহায় অবস্থায় থাকে, এই বিষয় এই কবিতা ও কাব্যেরও প্রধান সুর ও স্বর। আনিসুর এই বিষয়ই বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের নিরিখে এই গল্পে নিয়ে আসলেন। প্লানাটেরি মুভমেন্ট—একইসাথে চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের নিরিখে সবকিছু বদলাতে থাকে। এটি অ্যাস্ট্রোলজির একরূপ বয়ান। এটা বস্তুতন্ত্রের আর ভাবজগতের মাঝামাঝি বিদ্যমান। কিন্তু জগতের, একেবারেই বস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে, একটি দৃশ্যমান পরিবর্তনও রয়েছে। এই হিসেবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব বদলাতে বাধ্য। পুরোনো সময়ের বিপন্নতাবোধের বিষয় আর নতুন সময়ের বিপন্নতাবোধ, একাকীত্বের রূপ একই থাকে। কিন্তু দেশ-কাল-সময়ের বিবেচনায় এই বিষয় নতুন রূপে বদলাতে বাধ্য। যদিও রূপ একইরকম থাকে। কিন্তু বোদলেয়ারের জগতের সঙ্গে আনিসুরের গল্পের জগতের দেশ-কাল-সময়গত পার্থক্য আছে।
কিন্তু গল্পের প্রথমেই আমাদের একটু থমকে দাঁড়াতে হয়, গল্পকার সরাসরি বলছেন, ‘আমি সাম্যবাদে বিশ্বাসী।’ কিন্তু এরপরই তাঁকে বলতে শোনা যায় যে, তিনি জীবনানন্দের ভক্ত। একদিকে একটি নির্ধারিত রাজনৈতিক আদর্শ এবং এই আদর্শসঞ্জাত আকাঙ্ক্ষা ধারণ করার পরও এমন একজন কবিকে বেছে নেন, যে কবি কোনোভাবেই নির্ধারিত রাজনৈতিক আদর্শ-কাঠামো নিয়ন্ত্রিত নন; এবং এই কাঠামো দ্বারা সামান্য হলেও প্রভাবিত, কিন্তু পরিচালিত নন। তাহলে এই বাইনারি মেনে নেওয়ার কারণ কী? কেন গল্পকার এই যুগ্ম-বৈপরিত্য মেনে চলেন? এটি কেবল গল্পকারের মেনে চলা যুগ্ম-বৈপরিত্য নয়, একইসঙ্গে এই যুগ্ম-বৈপরিত্য এই সময়ে বসবাসরত দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যই প্রযোজ্য। অর্থাৎ একটি ভালো বিষয় নিয়ে কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু তার কার্যকারিতা নিয়ে আলাপ করা বেশ কঠিন। এবং এইরকম পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন অনেকটাই বিপন্নতায় পরিশ্রুত হয়। গল্পকার তাই বলতে বাধ্য হন, ‘যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা এই জেনে।’
এই গল্পে শিল্পায়নের ধারণাকে ব্যক্তির ক্ষুদ্র কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যক্তি ক্রমশই সামষ্টিক চিন্তা-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে একটি কাঠামো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গল্পকার সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম তাত্ত্বিক কার্ল মার্ক্সের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য। বলেন, ‘মার্ক্স তো চুরুট খেতেন, শুনেছি কাজও করেছিলেন তাঁর মতাদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক জায়গায়।’ এই উক্তিই আমাদের চোখ খুলে দেয়। দেখিয়ে দেয় চরমভাবে ক্ষমতাকাঠামো আর আর্থ-উত্পাদন-কাঠামোকে প্রশ্ন করা কার্ল মার্ক্সও তাঁর বিরুদ্ধের মতামতের ভেতরে বসেই বিরুদ্ধতার স্বর জারি রেখেছিলেন। এছাড়া মার্ক্সের আর বোধহয় কিছু করারও ছিল না। করতেও তিনি পারতেন না কিছু। মার্ক্সের নিজের আদর্শ যেমন তিনি ঠিকঠাক পালন করতে পারেননি, তেমনি এই গল্পে যে ব্যক্তি বয়ান তৈরি করে, সেও কিন্তু কর্পোরেট অফিসে কাজ করতে বাধ্য হয়। হতে হয়; মার্ক্সের মতো করে। কিন্তু গল্পের সূচনা তিনি করেন সাম্যবাদী ব্যবস্থায় আস্থা রাখার কথা বলে। এই যে অসহনীয় পরিস্থিতি, ব্যক্তির জন্য, এইটাও তিনি বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়ে আসেন এখানে।
এই গল্পে রাজনৈতিক আদর্শের বিষয় যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি করে নৃবৈজ্ঞানিক বিষয়ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন লেখক। মানুষের উদ্ভব এবং বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সভ্যতার বিকাশের বিষয়ও বিশেষ হয়েছে এই গল্পে। আর সমাজের ভেতরেই তো মানুষের অবস্থান। মানুষের কর্মকাণ্ডের ক্রমশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন আর উন্নয়নের ভেতর দিয়েই এই নৃবৈজ্ঞানিক বিষয়টি সামনে এগোয়।
যে কোনো সমাজে একটি পিরামিড সদৃশ কাঠামো গড়ে উঠতে বাধ্য। এর কারণ আইনসহ আরও নানা বিধিনির্ভর কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রেও একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকা দরকার। আর ‘রাষ্ট্রপ্রধান’ এই শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আসে এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও অনেক বিষয়। যা শ্রেণিনির্ভর হতে বাধ্য।
কিন্তু সমাজ তৈরি হলে সমাজে শ্রেণি ব্যাপারটি তৈরি হতে বাধ্য। শ্রেণি-সমতার বিষয় আদতে একটি হাস্যকর প্রপঞ্চ হিসেবে মনে করি আমি। এর মানে এই নয় যে, বঞ্চণা নিয়ে সমাজে মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে। না তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে কোনো সমাজে একটি পিরামিড সদৃশ কাঠামো গড়ে উঠতে বাধ্য। এর কারণ আইনসহ আরও নানা বিধিনির্ভর কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রেও একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকা দরকার। আর ‘রাষ্ট্রপ্রধান’ এই শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আসে এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও অনেক বিষয়। যা শ্রেণিনির্ভর হতে বাধ্য। ফলে শ্রেণিহীন সমাজ নেই। থাকতে পারে না। কোনোদিন ছিল না। এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। সম্ভব হবে না। যদি হতে হয় তাহলে তা হবে পরম নৈরাজ্যমূলক রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্র ভালো করলে যেমন তা জনগণের কল্যাণে কাজ করে। তেমনি এই রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে যদি তা জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় , তা হবে একটি সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড। এই পরিস্থিতিতে মানুষের হারানোর কিছু নাই ভেবে শূন্যবাদী হতেও যেন মানুষ বাধ্য হয়।
এই গল্পে আলাপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যক্তি-গর্ব ও বস্তু-গর্ব। এই গর্বের বিষয়টি সমাজ কিংবা রাষ্ট্র ব্যক্তির চেতনজগতে ঢুকিয়ে দেয়। ব্যক্তিমানুষ এই বিষয়টি নিয়ে গর্ববোধের জায়গায় পৌঁছায়। কিন্তু মনে রাখা জরুরি যে, এই ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যমে মানুষের গর্বের আড়ালে একটি রাষ্ট্রীয় ধান্দা লুকিয়ে থাকে। রাষ্ট্রে ধরা যাক, কাউকে ম্যাজিস্ট্রেট বানায়; কিংবা ধরুন কেউ কেউ ম্যাজিস্ট্রেট হয়, বিপুল ইচ্ছায়ই হয় এই ব্যাপারটা। কিন্তু রাষ্ট্রে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আপনি রিকশাচালক হতে বললেই ব্যাপারটা বেশ অপমানজনক হয়ে যাবে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষ কি রিকশা চালাতে পারবে না? পারলে সেটা দোষের কিছু হবে কেন? এইটার উত্তর রাষ্ট্র বেশি ভালো জানে। বোঝে। আসলে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া বেশি বড়ো কিছু নয়। বরঞ্চ ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া যে কোনো রাষ্ট্রের ক্ষমতাকাঠামোর উদ্দেশ্যই সম্পাদন করে। কেবল ম্যাজিস্ট্রেট নয়, সবাইই একই কাজ করে। কিন্তু এটা খারাপ কিছু নয়। রাষ্ট্রের জন্য কাজ তো করাই যায়। কিন্তু যা জনস্বার্থবিরোধী—এমন কাজকে দূরে রাখা জরুরি। কিন্তু ক্ষমতা তো সবকিছুই দূষিত করে। তবুও ওই যে সমাজের ভেতরে স্থিত ফাঁপা বেলুনের মতো ব্যক্তি-গর্ব আর বস্তু-গর্বের জন্যই এই কাজ করে লোকজন। ইচ্ছে করলেও লোকজন এই ধারণার বাইরে যেতে পারে না। এই আক্ষেপে আজীবন দুঃখ সয়ে গেছেন জীবনানন্দ, তাঁকে টেনে আনার কারণও বোধহয় এই।
কিন্তু যাওয়ার তো একটি আক্ষেপ থাকে। ইচ্ছে থাকে। মানুষ নীতিকথা বলে। কাল্পনিক মানদন্ড তৈরি করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কোনোটাই সে ঠিকঠাক করে উঠতে পারে না। সমাজে কেবল বাইনারি নয়, বহুস্বরও লুকিয়ে থাকে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র—আরও যে সমস্ত তন্ত্রই থাক না কেন, কোনো তন্ত্রেই সামগ্রিক মানুষের মুক্তি যেন মেলে না। তাই গল্পকার বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি এক একনিষ্ঠ অনুগত ক্রীতদাস। নিজের ক্রীতদাস আমি। এই দাসত্ব থেকে আমার মুক্তি নেই, মুক্তির পথ জানা নেই।’ হ্যাঁ—এই হলো এই মানুষের জীবনের বাস্তবতা। মাটিচাপা দিতে হয় চরম আদর্শের আকাঙ্ক্ষাও।
তা না হয় দেওয়া গেল। কিন্তু, এই মানুষটি কীভাবে বেঁচে থাকে শেষ পর্যন্ত। বেঁচে থাকতে হয় একটি দুর্বিষহ জীবন নিয়ে। একটি দাসবৃত্তির ভেতর দিয়ে জীবন পার করতে হয়। কেউ কেউ এটিকে ব্যক্তির সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে চায়। কেউ কেউ করে। কিন্তু এই যে রুগ্ন, কাফকেয়স্ক মানুষ, তাকে স্বীকার করতে হয় চরম হাহাকারের ভেতর দিয়ে। তাই গল্পের শেষের দিকে বলতে হয় গল্পকারকে, ‘আমি থরো নই, জীবনানন্দ দাশও নই। আমি সাম্যবাদী, শোষক ও ক্রীতদাস। আমার মুক্তি নেই।’ ‘আধুনিক’ মানুষের মুক্তি আদতেই নেই। এই গল্পগ্রন্থের সেরা গল্প হিসেবে আমি এটিকেই বিবেচনা করব।
৫.
‘অচেনা মানুষ’ গল্পে আনিসুর তাঁর কথিত ব্যক্তি ও ব্যক্তির যাপিত জীবনকে যে জগতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছেন সেই জগতের ভেতরে যে রুগ্ন মানুষের নির্মাণ, আমরা পূর্বেও দেখেছি সেই নির্মাণের পরিবর্ধিত রূপ ‘সিসিফাস শ্রম’ নামের গল্পে বিবৃত হয়েছে। গল্পটি ‘সিসিফাস শ্রম’ গল্পগ্রন্থের নামগল্প। কিন্তু এই গল্পগ্রন্থের সামগ্রিক বিষয় ধারিত হয়েছে ‘অচেনা মানুষ’ গল্পে। ‘সিসিফাস শ্রমে’ নয়। তবুও একটি প্রধান প্রবণতা, এই গল্পের, হলো কর্পোরেট যুগে মানুষের চরম নিয়তি। সিসিফাস তো পুরাণের চরিত্র। যাকে ক্রমশই পাথর ঠেলে যেতে হয়, কোনো বিশ্রাম দেবতা তার জন্য রাখেনি। তেমনি করে বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি মানুষই যেন এক-একজন মিথিক্যাল চরিত্র হিসেবে জীবন যাপন করছে। এর বাইরে তাদের বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।
এই গল্পের অন্দরে আলব্যের কাম্যু, ফ্রানৎস কাফ্কার অ্যাবসার্ড আর অসস্তত্ববাদী দর্শনের আনাগোনা চোখে পড়ে। আনিসুরের বিশ্বসাহিত্য-পাঠের একটি ভালো অভিজ্ঞতার নিদর্শনও বলা যেতে পারে এটিকে। কারণ লেখকমাত্রই প্রভাবিত। কেবল লেখক নন, আমি বলবো একেবারেই সাধারণ মানুষেরও দার্শনিক বিশ্বাস আছে। সেই দার্শনিক বিশ্বাস তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে তার জীবনের বাস্তবতা তার দর্শনের মতো হয়ে ওঠে। আনিসুরের এই দার্শনিক বিশ্বাসের ভিত তাঁর গল্পের জগতকেও বেশ দারুণভাবে শাসন করেছে।
গল্পকার এই যে তাঁর নিজের জনসমাজ থেকে আলাদা বৈদেশিক ও বিজাতীয় দর্শনের বিষয় নিজের গল্পের জগতের সঙ্গে একত্রিত করেছেন, সেই একত্রিতকরণের বেলায় তিনি তাঁর নিজের চারপাশের জনসমাজকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন।
কিন্তু গল্পকার এই যে তাঁর নিজের জনসমাজ থেকে আলাদা বৈদেশিক ও বিজাতীয় দর্শনের বিষয় নিজের গল্পের জগতের সঙ্গে একত্রিত করেছেন, সেই একত্রিতকরণের বেলায় তিনি তাঁর নিজের চারপাশের জনসমাজকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। এই গল্পের আফসার মিয়া এই ধারার ও ধারণার ভেতরে নির্মিত গল্প-চরিত্র। যে চরিত্র কোনো বিশ শতকীয় ইউরোপের কোনো এক মেট্রোপলিটনের দান নয়। সে নেহাতই এই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভেতরে একটি ঔপনিবেশিক পরিবর্তন-কাঠামোয় বেড়ে ওঠা মানুষ। এই পরিবর্তনের ধারায় তার মানসিক পরিবর্তনের বিষয়টি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এইজন্য ঢাকার বয়ানে আফসার মিয়ার জীবন যতোটা ঝকমারি, ততোটাই মানসিকভাবে তাকে বিপন্নতায়বিদ্ধ মনে হয়েছে। এই বিপন্নতাবোধ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কর্পোরেট শাসনের অনুগামী হয়ে। কিন্তু নস্টালজিয়া তাকে খুন করেছে বারংবার। মানুষ বারবার ফিরে যেতে চায় তার শৈশবে। কারণ ঝঞ্ঝাটমুক্ততা এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মানুষ আর ফিরে যেতে পারে না। তাই গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখতে ও গাইতে বাধ্য হন এই বলে, ‘ফিরব বললে ফেরা যায় নাকি/পেরিয়েছ দেশ-কাল জানো নাকি এসময়’।
৬.
‘মাস্টারপিস’ গল্পটি একটি রেটোরিকের ভেতর দিয়ে গল্প হয়ে উঠেছে। এই গল্পের ভেতরে আছে একটি বাস্তবতা, বাংলাদেশের বাস্তবতা। সেটি সড়ক দুর্ঘটনা। ২০২৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় সর্বমোট মৃতের সংখ্যা ৭ হাজারের উপরে। এই মৃত্যুর হিসেব যে কোনো সংক্রমক রোগের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনা এড়িয়ে মানুষের কি পথে নামা সম্ভব? উত্তর না। কিন্তু এর রোধের একটি ব্যাপার তো থাকে। সেই বিষয় কি বাংলাদেশে মেনে চলার বিষয় দেখা যায়। উত্তর হবে না। সড়কের নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে হরহামেশাই নিজেদের নিয়মে গাড়ি হাঁকানোর বিষয়ও এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফলে জনগণের সড়কে মৃত্যুর বিষয়টি হয়ে ওঠে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক বিষয়।
কারো কাছে এই গল্প প্রথম পাঠে নিয়তি নির্ভর মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি সিস্টেমের ভেতর দিয়েই ঘটেছে। আর এই সিস্টেম অবশ্যই নেতিবাচক। কারণ মানুষের মৃত্যু যে সিস্টেম ঘটায়, সেই সিস্টেম কখনই ইতিবাচক হিসেবে বিচারের সুযোগ নেই। গল্পকার এই বিষয়ে ফিরিস্তিও দিচ্ছেন, বলছেন, ‘ঘটনাটি এগিয়ে যাচ্ছিল নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়।’ কিন্তু গাড়ির ধাক্কায় মানুষের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রস্তাব গল্পকার এই গল্পের বয়ানে স্পষ্ট করেন, সেই বয়ান অনেকাংশেই শিল্পিত। কোনো পত্রিকাওয়ালার বর্ণনা এই বয়ানে নেই। কেউ কেউ শিল্পের উপযোগিতাবাদকে খারিজ করতে চান। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একটি আলাপ জারি রাখতে চাই যে, শিল্পের কোনো না কোনো উপযোগিতা থাকবেই। ধরুন, কেবল সৌন্দর্যবোধের বিষয়ও একটি উপযোগিতার ভেতর দিয়ে তৈরি হয়।
এই গল্পের এই সৌন্দর্যবোধের ধারণা অনেকাংশে ‘ভয়ঙ্কর সুন্দরের’ মতো। আর্টের ভেতর দিয়ে যে সামাজিক অসংগতির বিষয় উপস্থাপিত হতে পারে, এই বিষয় উপস্থাপনই প্রধান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে গল্পে। আর্টের ভেতর দিয়ে দর্শন আর রাজনৈতিক দর্শনের বিষয়ও উপস্থাপিত হয়েছে। যা দ্বৈতভাবে কাঠামোগুলোকে রাজনৈতিক অর্থনীতির হিসেবের মধ্যেও প্রবিষ্ট করাতে বাধ্য করে। ফলে সমাজের প্রচলিত নৃশংসতার বয়ান শিল্পের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়ে একটি সফল শিল্প হয়ে ওঠে। পাবলো পিকাসোর গোয়ের্নিকার বেলায়ও এই সত্যিটা আমাদের বলতে হয়।
৭.
সমাজ বদলায়। সভ্যতা বদলায়। এই বদলের ভেতর দিয়ে বদলায় জনসমাজ। জনসমাজ আবার কোনো একক প্রত্যয়ের আওতাধীন নয়। বহুবর্ণিল প্রত্যয়-প্রপঞ্চ একত্রিত হয়ে একটি জনসমাজের পূর্ণাঙ্গ পরিসর নির্মিত হয়। আনিসুরের মাথায় এই বিষয়টি বিশেষভাবে ঠেসে আছে বলেই বোধ হয়। ‘১৯৮০’ গল্পে সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় মানুষের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে; তেমনি একইসঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আর পরিবর্তনের রাজনীতিও বিশেষভাবে জারি রয়েছে। এই গল্পের ঘটনা-পরিসর জুইখালি বলে এক গ্রামের। যে গ্রাম প্রত্যন্তই বটে। গ্রামের বিবরণ প্রত্যন্ত হলেও টেকনোলজির বুমিং ব্যাপারটা আর ততোটা প্রত্যন্ত করে রাখেনি এই অঞ্চলের গ্রামকে।
পঞ্চাশের দশকের গ্রামের যে বিবরণ ও বর্ণনা আপনি পাবেন, সেটাই ৮০-৯০ এর দিকে একভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার এই সময়ে এসে গ্রাম-শহরের পার্থক্য প্রায় নাই হয়ে গেছে। যাই হোক, যে আলাপে ছিলাম, জুইখালি গ্রাম আর জয়নাল ব্যাপারীর বাইনারির বিষয়। জয়নাল ব্যাপারীর সাংস্কৃতিক পরিসর যাত্রাপালাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে। আর এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং পরিচয় রয়েছে এই গ্রামের অধিকাংশ লোকের। এরা সবাই মিলে এক বর্গ। বিপরীতে চেয়ারম্যানের ছোটো ছেলে আর তার আনা টেলিভিশন ও টেলিভিশন নির্ভর সংস্কৃতি-কাঠামো আরেক বর্গ। এই দুই বর্গের সংঘর্ষই এই গল্পের প্রধান বিষয়। কিন্তু সংঘর্ষ মানে খুনোখুনি নয়। সংঘর্ষ প্রধানত সংস্কৃতি নির্ভর। সংঘর্ষ সাংস্কৃতিক বিবর্তনে টিকে থাকার বিষয়। এবং একইসঙ্গে পুরোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নতুন সময়ে তৈরি হওয়া সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের।
কিন্তু সংকট তৈরি হয় জনসমাজেও। চেয়ারম্যানের ছোটো ছেলের সঙ্গে জয়নাল ব্যাপারীর সাংস্কৃতিক জগতের যে ফারাক ও মনোস্তাত্ত্বিক সংকট, সেই সংকট তাদের চারপাশের মানুষের ভেতরেও প্রবিষ্ট হয়। জয়নাল ব্যাপারী সাধারণ লোকজনকে বোঝাতে যাননি, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভেতরে একটি ভয় যেন ঢুকে গেছে। ডাকাতের ভয়। বলে রাখা ভালো যে, এই রূপান্তরের প্রতি পুরোনো সংস্কৃতির মানুষের একটি সন্দেহের বিষয় রয়েই গেছে। অর্থাৎ প্রচলিত ও প্রথাগত সাংস্কৃতিক জগতের ভেতরে নতুন করে আমদানি হওয়া প্রযুক্তিগত সাংস্কৃতিক জগৎ নানা কারণে সন্দেহজনক হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে এই গল্পে। কিন্তু যে প্রযুক্তিগত সাংস্কৃতিক জগতের বিষয় নিয়ে আলাপ করা হচ্ছে এই গল্পে, মানে চেয়ারম্যানের ছোটো ছেলের সাংস্কৃতিক জগতের বিষয়, তার একটি কর্তৃত্ববাদী চরিত্র অবশ্যই আছে। আর এই কর্তৃত্ববাদীতা বিষয়টি শেষমেশ জয়নাল ব্যাপারীর গলায় জুতোর মালা পরাতে সমর্থ হয়। সে তার পুরোনো সাংস্কৃতিক জগতের কর্তৃত্ব হারায় নতুন সাংস্কৃতিক জগতের কর্তৃত্বের কাছে। কিন্তু জনসমাজের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয় একটি জাদুবাস্তবতার বর্ণনা-পরিসরে। এই বিষয়ে আমার শহীদুল জহিরের গল্পের জগতের কথা সামনে চলে আছে। ‘আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস’ কিংবা ‘ডলু নদীর হাওয়া’ এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।
৮.
আনিসুরের গল্পে ব্যক্তি আছে। পূর্বে গল্পের আলোচনায় সেই ব্যক্তির বেড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। আনিসুরের গল্পের ব্যক্তি দারুণভাবে একা, নিঃসঙ্গ; হতাশায় নিম্মজিত, কূল-কিনারা খুঁজে না পাওয়া চরম বিষাদে ভোগা শূন্যবাদী ব্যক্তি। আগের কয়েকটি গল্পে এই প্রবণতা জওয়ানকালের বিবেচনায় বর্ণিত হয়েছে। চরমভাবে আত্মনিমজ্জনের বিপরীতেও কিছুটা যৌবনের হাল ওইসব মানুষের ভেতরে দেখা যায়। ‘ভ্রষ্ট গণক ও বিকলাঙ্গ তাস’, ‘অক্টোবরের শেষ বিকেল’ ও ‘আগর আলীর প্রাতভ্রমণ’—এই তিনটি গল্পই প্রায় একই ধারার। এই গল্পগুলোতে ব্যক্তিজীবনের মাঝ কিংবা শেষ পর্যায়ে অবস্থান করছে এবং জীবনে ঘটে যাওয়া বিচিত্র বিষয় টেনেহিঁচড়ে সামনে নিয়ে এসেছে চরিত্রগুলো। চরিত্রগুলো সক্রিয় থেকেছে সর্বদা বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়ার মাঝখানে একটি ধূসর রেখার ওপর। সেখান থেকেই বারবার জীবনকে দার্শনিক প্রত্যয়ে বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়েছে। এই তিনটি গল্পই প্রায় এক ধারার। কিন্তু কিছু বিষয় বিষয়ের ভেতরেও বিষয়ের পার্থক্য তৈরি করেছে। ফলে আমার মনে হয় এই তিনটি গল্পের বিষয় নিয়ে একটি গল্পও লেখা যেতো। আনিসুর অবশ্য তিনটি গল্প লেখার মাধ্যমে তাঁর গল্প-বিষয়ের পরিসর বাড়িয়েছেন।
মানুষ মূলত বেঁচে থাকে তার সময়ের সঙ্গে। এই সময় সবসময়ই বহুবর্ণিল। বহুবর্ণিল বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুক্রমে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা কিংবা সামষ্টিক মানুষকেন্দ্রিকতার বিষয়ও এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত। এর সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ভেতরে তৈরি হয় ব্যক্তির নস্টালজিয়া।
আমি এই তিনটি গল্পের ভেতর থেকে একটি গল্প নিয়ে আলাপ করব: ‘অক্টোবরের শেষ বিকেল’। মানুষ মূলত বেঁচে থাকে তার সময়ের সঙ্গে। এই সময় সবসময়ই বহুবর্ণিল। বহুবর্ণিল বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুক্রমে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা কিংবা সামষ্টিক মানুষকেন্দ্রিকতার বিষয়ও এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত। এর সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ভেতরে তৈরি হয় ব্যক্তির নস্টালজিয়া। যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে, সে ব্যক্তি আদতে ক্রমাগত মরণের দিকে এগোয়। ব্যক্তির জীবন তাই বলা চলে ক্রমশই মরণের দিকে যাত্রা। ‘অক্টোবরের শেষ বিকেল’ গল্পে এই দার্শনিক বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়। গল্পটি মোটাদাগে তিনটি বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করেছে: ১. সময়ের প্রথাগত ধারণা বাতিল করে ফেলার এক দারুণ চেষ্টা; ২. নস্টালজিয়ায় ফ্লাশব্যাক-ফ্ল্যাশফরোয়ার্ড পদ্ধতিতে জীবনের মানে খোঁজার প্রচেষ্টা; ৩. আর বার্ধক্য ও মৃত্যু সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার নব রূপায়ণ। তবে এই তিনটি বিষয় নিয়ে লেনদেনের সময় আনিসুর রহমান বয়ে চলা জীবনের নিরন্তর ঘন্টাধ্বনিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। এবং তিনি বারবার এই বিষয়কে শূন্যবাদী মর্মার্থে প্রকাশের একটি বৃহৎ আকাঙ্ক্ষার উত্সকে জারি রেখেছেন।
৯.
আনিসুরের গল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাষা ও প্রবাদ; আর এই দুটি বিষয়ের সমন্বিত ব্যবহারিক শক্তির তাত্পর্য। এই শক্তির বলে এই গল্পগ্রন্থ আরও এক ধাপ সামনে এগোবে। আনিসুর এই ক্ষেত্রে ওয়ালীউল্লাহ্র মতো। বিষয় দেশি, প্রকরণ বা কথা বলার স্টাইল বিদেশী। কিন্তু যদি বাবলা গাছ দিয়ে আমার চারপাশের কথা বলা সম্ভব হয়, তো কেন পাইন-ফার-এল্ম গাছের কথা বলতে হবে? দৃশ্যজগতের অদৃশ্যতায় কি ভালো উদাহরণ তৈরি হতে পারে? না, তা হতে পারে না। আনিসুর এই বিষয়টি মাথায় রেখে তাঁর গল্পের জগৎ-পরিসীমা নির্মাণ করেছেন। তিনি তাঁর গল্পে ব্যবহৃত নস্টালজিয়া আর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ যে জগতকে তিনি বারবার তাঁর গল্পে হাজির করেন, সেই হাজিরা হিসেবের বিষয়টি এই। তিনি তাঁর পেছনে ফেলে আসা স্মৃতির জগৎ ও পুরোনো ভাষার জগতকে একদম নতুনভাবে নতুন সমাজের সঙ্গে একত্রিত করে নতুন ভাষার জগতের সঙ্গে একীভূত করেন। ফলে আমাদের কারো কারো কাছে তা বেশ বৈসাদৃশ্য লাগে। কিন্তু বলে রাখা জরুরি যে, পুরোনো সময়-ভাষা নতুন সময়ে প্রকাশ করতে হলে নতুন সময়-ভাষায় এই কাজ করতেই হবে; না হলে তা গুরুত্ব হারাবে।
ভাষা প্রসঙ্গে কেউ কেউ গল্পগ্রন্থের ভাষায় ব্যবহৃত কাব্যিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কিন্তু কাব্যিক হলেই গদ্য কাব্য হয়ে যায় না। কাব্যিক গদ্যের কিছু উদ্দেশ্য থাকে। প্রকাশ করতে হবে এমন বিষয় নিয়ে যখন আলাপ হয়, তখন গদ্যকার বেছে নেন তিনি কোন তরিকায় তার গদ্য নির্মাণ করবেন। সিধে গদ্যের বিষয়, মানে খবরের কাগজের মতো সরল বর্ণনায় নির্মিত, কেউ কেউ গল্প-উপন্যাসের গদ্য হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু এই গদ্যের মাধ্যমে কথাসাহিত্যে প্রকাশিত ভাব-বিষয় সাহিত্যের রেটোরিকতার অনুষঙ্গে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে হুমায়ূনী গদ্যের মতো জনপ্রিয়তা বিষয়ক সমস্যা তৈরি হয়। অবশ্য সাহিত্য-সমাজে তারও একটা দাম আছে।
কিন্তু এর বিপরীতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র গদ্য এই কাব্যিকতার সমস্যাটাই তৈরি করে। এতো বেশি মনোলগের ভেতর দিয়ে তাঁর কথাসাহিত্যের গদ্য তৈরি হয় যে, সেই গদ্যের মাধ্যমে ‘অধিকারভুক্ত উদ্দেশ্য’ ব্যাপারটা চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই লেখকের তুঙ্গ আগ্রহের বিষয় বোধহয় গড় পাঠকের কাছে বিষের মতো তীব্র লাগে। দেখেন ওয়ালীউল্লাহ্র ‘লালসালু’ যেভাবে পঠিত হয়, আমার নিরিখ থেকে বলছি, ‘চাঁদের অমাবস্যা’ কিংবা ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ ততো নয়। কারণ এই গদ্য। গদ্যের কারণেই আজতক ওয়ালীউল্লাহ্ পঞ্চাশের দশকের লেখক হওয়া সত্ত্বেও যেন ‘দূরের কোনো দেশের রাজপুত্তুর’ হয়ে আছেন, যাঁকে ছুঁতে হলে লাগে আঠারো ঘা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তো আমাদেরই লোক। আমি আনিসুরের গদ্যকে ওতো তাত্পর্যের পর্দায় ঢাকনা দিতে চাই না। কিন্তু এমন একটি বিষয় সত্যি হয়েছে। এই বিষয় হওয়ার পেছনে তাঁর বিদেশি সাহিত্যপ্রীতির বিষয় বেশ সরব থেকেছে বলেই আমার মনে হয়। আর চিন্তার জগতের জটিলতার বিষয় তো আছেই, যা ভাষার প্রকাশ-জগতকে জটিল করে তোলে।
১০.
আরেকটি বিষয়, চেতনাপ্রবাহরীতি কিংবা ফ্ল্যাশ ব্যাক-ফ্ল্যাশ-ফরোয়ার্ড পদ্ধতি ব্যবহার করে গদ্য লেখার যে বিষয়, সেটির আমদানি এই দেশের কোনো কোনাকাঞ্চি থেকে নয়। তা পশ্চিমের জিনিস। কিন্তু এটি ব্যবহার করা কি পাপ? না। তা নয়। কিন্তু সমন্বয় আর আরোপণ—এই দুটি শব্দ এই বিষয় বোঝার জন্য বেশ তাগদই হবে নিশ্চয়। আমিও এই কথাটিই বলতে চাই। আনিসুর তাঁর গল্পের ভাষার ব্যাপারে এই কাজটি করেছেন। তিনি নস্টালজিয়ায় ভর করে তাঁর ফেলে আসা স্মৃতিভান্ডার থেকে ছেনেকুঁদে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। যা তাঁর গল্পকে আর গল্পের ভাষাকে করেছে অন্য রকম। দেখুন, এইক্ষেত্রে আনিসুরের গল্পের ভাষার দুর্বোধ্যতা নিয়ে কথা বলতে পারেন। মানে অনেকটা অলৌকিক বিষয়। কিন্তু গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ‘শতবর্ষের নির্জনতায়’ মার্কেজ যে জগতের বর্ণনা দেন, তা কোনো অলৌকিক জগৎ নয়। মার্কেজের অভিজ্ঞতায় এবং তাঁর পরিপার্শ্বের অভিজ্ঞতায় তাঁর জগৎ তৈরি হয়। কিন্তু আমাদের কাছে তা অবাস্তব মনে হয়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা যার আছে, সে কিন্তু কখনো বলবে না যে, মার্কেজের গল্পের জগৎ কোনো জাদুর জগৎ। তেমনি করে আনিসুরের গল্পের জগৎও তাঁর একান্তই নিজের জগৎ, যে জগৎ ও ব্যবহার করে চারপাশের পুরো দৃশ্য-কর্মজগতকে একত্রিত করতে চান। কিন্তু আনিসুর যেভাবে গল্প বর্ণনা করেন, তা ওই পুরোনো পদ্ধতিই বটে। ইন্টেরিয়র মনোলোগে ঠাসা। মাঝে মাঝে কিছু গল্পের ভাষা বিষয় মনে হয় ধাঁধা লাগানো। এই ধাঁধা লাগানো ব্যাপারটাই মাঝে মাঝে বড়ো লেখককে দূরবর্তী করে। এই ধাঁধা লাগানো ব্যাপারটাই ওয়ালীউল্লাহ্কে দূরে রেখেছে। মন্দির বানিয়েছে। একপাক্ষিক পূজার ফুল দিয়ে পূজা করেছে। এই গল্পকার এই ফাঁদে পড়বেন কি না, তাও বোধহয় সময় নির্ধারণ করবে। তবে একথা সত্য যে, এই ধারার অন্যান্য লেখকদের মতো একটা অবস্থান ভাষার বেলায় আনিসুরের হবে।
১১.
শেষ কথা। এই গল্পের আধুনিকতার বাস্তব এবং দরকারি ভূমি বিষয়ে। ‘ওয়ালীউল্লাহ্’ যে সময়ে আধুনিকতা নিয়ে সাহিত্য করেছিলেন, সেই সময়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা আধুনিক সাহিত্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশের যথাযথ সময় কিনা, এই বিষয়ে একরকম সন্দেহ রয়ে গেছে। কিন্তু আনিসুর যে সময়-বাস্তবতায় তাঁর গল্পে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করতে চেয়েছেন, তা যেন নানা কারণে তার ভিত্তি মোটামুটি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। এটি আধুনিকতার ভিত্তি প্রসঙ্গে বেশ জরুরি বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে। আনিসুরের গল্পের আধুনিকতার প্রকল্পের বেলায়ও। তাঁর গল্প সম্পর্কে ভালো-মন্দ মিলিয়ে যে সমস্ত কথা বললাম, তাও বোধহয় সময় মাপবে; যে এই সমস্ত কথা থাকবে কি থাকবে না।

প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক। জন্ম ১৮ মে ১৯৯৪ সালে, ঝিনাইদহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর। পেশা শিক্ষকতা। নিয়মিত লিখছেন ও অনুবাদ করছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৬০-এর অধিক।