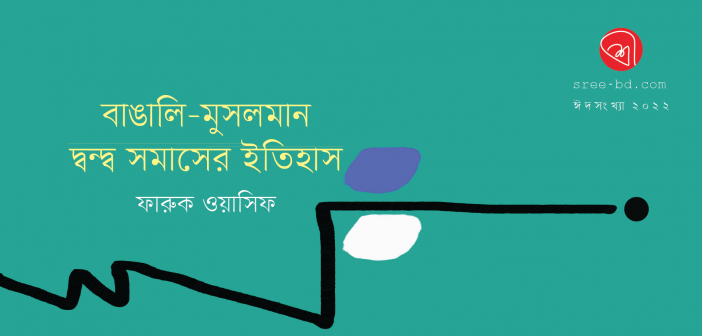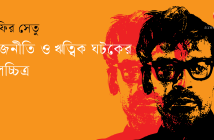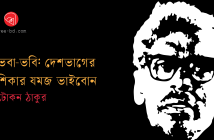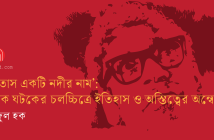১৮৭১ সালে ভারতবর্ষের এক ব্রিটিশ প্রশাসক উইলিয়ম হান্টার ‘দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস’ বইটা প্রকাশ করেন। প্রথম বাক্য ছিল, ‘আমাদের সীমান্তে বিদ্রোহীদের শিবির’। রিচার্ড ইটনের ফ্রন্টিয়ার (সীমান্ত) তত্ত্ব হয়তো এর কাছে খানিকটা ঋণী। হান্টার প্রশ্ন তোলেন: হু আর দি ইনডিয়ান মুসলমানস? প্রায় একইসময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ও জানতে চান, কে বাঙালি মুসলমান? কোথা থেকে এলো তারা? এসব স্ফিংসীয় প্রশ্নের সামনে আজও জড়োসড়ো (ভারতীয় বা বাঙালি) মুসলমান। এই প্রশ্নের কাঠগড়া থেকে বাঙালি মুসলমান যে আজও বের হতে পারে নাই তার নমুনা বহুত। পরিচয় রাজনীতির দ্বারবানদের সামনে মুসলমান যে থতমত, তার সাক্ষ্য দেবে বাঙালি মুসলমান নিয়ে ‘বাঙালি মুসলমানের মন’ (আহমদ ছফা, ১৯৭৬) থেকে সাম্প্রতিক ‘বাঙালি মুসলমান প্রশ্ন’ (মাহমুদ হাসান,২০২২)। প্রশ্ন যিনি করেন তিনি পরিচয় রাজনীতির দালানের দারোয়ান। প্রশ্ন করার ক্ষমতা আসলে রাজনৈতিক ক্ষমতা।
এই প্রশ্ন বাংলাদেশি ইসলামিস্টদেরও তাড়া করে। বারেবারে তাঁরা বাঙালিত্বের পরীক্ষা দিতে বসেন। এটা কেবল হাস্যকরও না এটা তো ফাঁদ। বাংলার সব মানুষ ইহুদী, খ্রিষ্টান বা তালেবান হয়ে গেলেও বাঙালিই থাকবে, যতদিন না তারা বাংলা ভাষা ছাড়ে।
আহমদ ছফাও কুণ্ঠিত হয়ে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্নের দাপটে। এই প্রশ্ন বাংলাদেশি ইসলামিস্টদেরও তাড়া করে। বারেবারে তাঁরা বাঙালিত্বের পরীক্ষা দিতে বসেন। এটা কেবল হাস্যকরও না এটা তো ফাঁদ। বাংলার সব মানুষ ইহুদী, খ্রিষ্টান বা তালেবান হয়ে গেলেও বাঙালিই থাকবে, যতদিন না তারা বাংলা ভাষা ছাড়ে। বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা, বাঙালিত্বকে অসাম্প্রদায়িক করা এবং তাকে টিকিয়ে রাখায় বাঙালি মুসলমানের অবদান তো কারো চাইত কম না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদদের তালিকাতেও সংখ্যায় তারাই বেশি। তারপরও তার হীনম্ম্যন্যতা কেন? কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের ওই প্রশ্নের জবাবের ভাষা আজও তার আয়ত্বে নাই। সে পরীক্ষায় জয়ী, কিন্তু মার্কশিট তার হাতে নাই।
বাঙালিত্ব কোনো রেইস নয়। বাঙালিত্ব মানে যদি হিন্দুত্বই তাহলে আলাদা করে বাঙালি নামের পরচিয় থাকার দরকার হতো না। বাঙালি যখন মুসলমান কিংবা মুসলমান যখন বাঙালি, তখন বাঙালি পরিচয় উভয় ধর্মোত্তীর্ণ হয়ে যায়। বাঙালিত্ব মানে কেবল হিন্দুকে বোঝাত যদি মুসলমান বাঙালিত্বের শরিকানা দাবি না করত।
বাঙালি-মুসলমান কি দ্বন্দ্ব সমাস? কার সঙ্গে কার দ্বন্দ্ব? বাঙালিত্বের সঙ্গে মুসলমানিত্বের? তাহলে প্রশ্ন, বাংলাভাষী মুসলমান কি বাঙালি নয়? মুসলমান হলে বাঙালি থাকা যায় না? বাঙালি আর হিন্দু কি তবে সমার্থক? যদি তা হয়, তাহলে বাঙালি হতে হলে বাংলাভাষী মুসলমানকে হিন্দু হতে হবে। বাঙালিত্ব কি তবে কোনো ধর্ম যে মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে সেটা পালন করা যায় না? বাঙালিত্ব কি কোনো রেইস বা জাত বা বর্ণ যে, জন্মসূত্রে ছাড়া কারো পক্ষে বাঙালিত্বে দাখিল হওয়া অসম্ভব? তবে কি হিন্দু বিনা কেহ বাংলাবর্ষে বাঙালি হতে পারে না? (‘বাঙালি মুসলমান কি দ্বন্দ্ব সমাস?/ফারুক ওয়াসিফ, বাসনার রাজনীতি কল্পনার সীমা, ২০১৫, আগামী প্রকাশন’)
কিন্তু কী যুক্তিতে বাঙালিদের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যারা বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের বড় অঙ্গ, তাদের বাঙালিত্বে সমান অধিকার থাকবে না? বাঙালি আর হিন্দু সমার্থক হলে যিনিই বাঙালি তিনিই হিন্দু। অর্থাৎ সব হিন্দুই বাঙালি, সব বাঙালিই হিন্দু। তাহলে ‘বাঙালি’ ও ’হিন্দু’ দুটি শব্দ কেন দরকার হবে যদি দুটি ‘পরিচয়’ একই হয়?
তাহলে হিন্দুদের বাঙালি হওয়ার আর দরকার নাই, যেহেতু তাঁরা তা হয়েই আছেন। শুধু মুসলমানদের ওপর বাঙালি হওয়ার একটা আলাদা দায় বর্তায়। এই যুক্তি মতে, বাঙালি মুসলমানের বাঙালিত্ব জন্মগত নয়, তা সাংস্কৃতিকভাবে অর্জন করতে হয়। সেই অর্জনের জরুরি শর্ত হলো তার মুসলমানিত্ব খারিজ করা। কিন্তু চর্যাপদে যে বাঙালি বৌদ্ধ গণহত্যার কথা আসে, তারাও তো বাঙালি। আবার একাত্তরে যে বাঙালি নামের লোকেরা যুদ্ধ করেছিল তারা মূলত বাঙালি মুসলমান। বাংলা ভাষার জন্য জীবনও দিয়েছে তারা। আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির দুটি সর্বজনীন উৎসব; একুশের প্রভাতফেরি আর বৈশাখী শোভাযাত্রার উদ্ভাবনও তাদের হাতে। সেন আমলে বাংলা রাজ দরবারে সমাদর পেত না। বাংলা রাজভাষা হয় মুসলমান সুলতানি আমলে। বাংলা ভাষার বিস্তার ও সাহিত্যের উদয়ও সেসময়ের ঘটনা। মহাভারত ও রামায়ণের বাংলায়ন সেন আমলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। সুলতানি আমলে তা পুরস্কৃত হলো।
বাঙালির গায়ে মুসলমানের যে অমোচনীয় দাগ লেগে গেছে, বাঙালিত্বের বিকাশে বাংলাভাষী মুসলমানের যে অবদান তা অস্বীকার করা আর মুসলমানকে কম বাঙালি বলা সমান কথা।
সাংস্কৃতিক বর্ণবাদ মুসলমানের বাঙালিত্বকে অস্বীকার করে সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদের বীজ বুকে বহন করে চলছে। আবার উল্টোদিকে বাঙালি বিরোধী মুসলিম রাজনীতি হয়ে উঠতে চাচ্ছে গরিষ্ঠতাবাদী; আসলে যা ফ্যাসিবাদের আরেক চেহারা। যেহেতু বাঙালিত্ব কোনো ধর্ম নয়, সেহেতু কোনো ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে তার বিরোধ কল্পনা করা সাম্প্রদায়িকতা।
সাংস্কৃতিক বর্ণবাদ মুসলমানের বাঙালিত্বকে অস্বীকার করে সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদের বীজ বুকে বহন করে চলছে। আবার উল্টোদিকে বাঙালি বিরোধী মুসলিম রাজনীতি হয়ে উঠতে চাচ্ছে গরিষ্ঠতাবাদী; আসলে যা ফ্যাসিবাদের আরেক চেহারা। যেহেতু বাঙালিত্ব কোনো ধর্ম নয়, সেহেতু কোনো ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে তার বিরোধ কল্পনা করা সাম্প্রদায়িকতা। কিছু ইসলামপন্থি ও কিছু হিন্দুত্ববাদী (এমনকি কিছু সেক্যুলারও) এভাবেই বাঙালি বিরোধিতায় একাকার হয়ে যান। এ থেকেই জন্মায় বাঙালি ও মুসলমানের ফুটবল খেলার দ্বন্দ্বতত্ত্ব।
বাঙালি পরিচয়টাকে যদি আমরা অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক করতে না পারি, তাহলে কখনো হিন্দু (পশ্চিম বাংলায়) এবং কখনো মুসলমান (বাংলাদেশে) পরিচয় নিয়ে হীনম্মন্যতা আসবে। বাঙালি ও মুসলমান দ্বন্দ্ব সমাস ভাবার ভুলটা ঊনিশ শতকে কলকাতায় তৈরি সাম্প্রদায়িক বাঙালিবাদের জের, এখনো অনেক সংস্কৃতিবাদী তাতে মজে আছেন। বাঙালি মানে যদি হিন্দুত্ব হয় তা হলে মুসলমান তা হতে চাইবে কেন? বাংলাদেশের বাংলাকে মুসলমানি বাংলা বলার জবাবে কি বলব ভারতীয় বাংলা হিন্দুয়ানি? ভাষার গায়ে সম্প্রদায় চিহ্ন থাকবেই। বাংলা ভাষার জন্ম সাঁওতালি-মুন্ডারি উৎস থেকে। একে সমৃদ্ধ করেছে সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি। ভাষাকে সেকুলার করা যায় না, ভাষা তার মানুষের মুখের পেঁয়াজ, সুক্তো, ঘরের ধূপ, আগর-আতর, সব কিছুর ঘ্রাণ বহন করতে চায়। ভাষা কখনো নাস্তিক হয় না। বাঙালি ও মুসলমান কোনো দ্বন্দ্ব সমাস নয়, এটা মিলনাত্মক ঐতিহাসিক সমাস হিসেবে নির্মাণ পেয়েছে। ভবিষ্যতে কী হবে জানি না, তবে যে হারে মুসলমানমনা একটি অংশ বাঙালিত্বকে বাদ দিয়ে ‘শুদ্ধ’ হতে চাইছে, তাতে মনে হচ্ছে বাঙালি হিসেবে তার যাবতীয় ঐতিহাসিক অর্জনকে বাদ দিয়ে দেউলিয়া হওয়াতেই তার সুখ। আত্মঘাতী বাঙালিরা দেশভাগ করেছিল, মুসলমানরা যদি বাঙালিত্বকে ভাগ করে; তবে সেটাও হবে মারাত্মক আত্মঘাত।

জন্ম বগুড়ায়। প্রথম পাঠ বগুড়া মিশন স্কুলে, স্নাতকোত্তর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা ও গল্প লেখা দিয়ে শুরু হলেও প্রতিরোধী রাজনীতিতে জড়িয়ে যান ছাত্রকালেই। পেশাগতভাবে সাংবাদিক। প্রথম আলোর নিয়মিত কলাম লেখক। কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক। আগ্রহের বিষয় জাতি ও জাতীয়তাবাদ, ইতিহাস, সাহিত্য ও রাজনীতি। কবিতার বই : ‘জল জবা জয়তুন’ (আগামী প্রকাশনী, ২০১৫), ‘বিস্মরণের চাবুক’ (আগামী প্রকাশনী, ২০১৭), প্রবন্ধের বই : ‘জীবনানন্দের মায়াবাস্তব’ (আগামী প্রকাশন, ২০১৭), ‘বাসনার রাজনীতি, কল্পনার সীমা’ (আগামী প্রকাশন, ২০১৬), ‘ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে’ (শুদ্ধস্বর, ২০১১), ‘জরুরি অবস্থার আমলনামা’ (শুদ্ধস্বর, ২০০৯)। অনুবাদের বই : ‘সাদ্দামের শেষ জবানবন্দি’ (প্রথমা, ২০১২)।