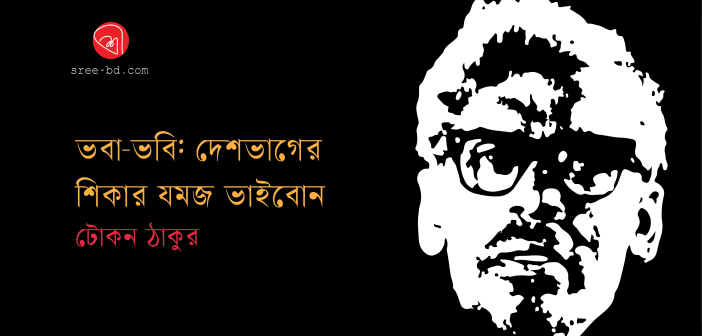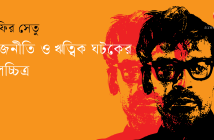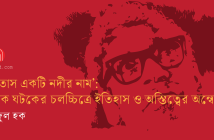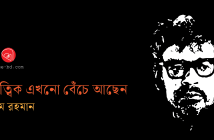দেশভাগের পর নদীই হয়তো সীমান্তরেখা হয়ে গেছে। নগর কোলকাতার কয়েকজন থিয়েটারকর্মী এসেছে নদীর পাড়ে, নদীর ওপারেই বাংলাদেশ বা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান। থিয়েটার দলের অস্থির ও বিষণ্ণ নির্দেশক, যুবক ভৃগু তাকিয়ে থাকে বাংলাদেশের গ্রামটির দিকে। দলের নতুন সদস্যা যুবতি অনুসূয়াকে ভৃগু বাংলাদেশের গ্রামটি দেখিয়ে বলে, ‘ওই যে আমাদের গ্রাম, ওখানেই আমাদের বাড়ি ছিল কিন্তু কোনো দিন আমি আর ওখানে যেতে পারব না।’ চরম এক হতাশার অতল থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা দেশভাগের যাতনার আখ্যান বলে দেয় কয়েকটি সংলাপে—আমরা ঋত্বিককুমার ঘটকের ‘কোমলগান্ধার’ ছবিতে এরকমই দেখতে পাই। পুরো ‘কোমলগান্ধার’ ছবিতেই দেখি দেশভাগ এপিক হয়ে ওঠে। দেশভাগ হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। ‘সুবর্ণরেখা’তেও দেখি বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ভাইবোনের গল্প, ছোট্ট বোন সীতা ও তার ভাই অভিরামের গল্প। ভাইবোন হাঁটছে নদীপাড়ের বালিয়াড়ি ধরে, বাড়িহীন ভাইবোন হাঁটছে পৃথিবীতে। সীতা হাঁটতে হাঁটতেই প্রশ্ন করে, ‘দাদা, আমাদের নতুন বাড়িটা কোথায়?’ ভাই অভিরাম উত্তর দেয়, ‘ওই তো, সামনেই।’ একটি নতুন বাড়ির সন্ধানে তারা নদীপাড়ের বালিয়াড়ি ধরে হাঁটতে থাকে। দেশভাগে তারা বাড়ি হারিয়েছে। নতুন দেশের সীমানার ভেতর শরণার্থীদের জন্যে গড়ে ওঠা যে নবরতন কলোনি, আপাতত কি সেখানে আশ্রয় মিলবে? এরকমটি দেখতে পাই ঘটকের ‘সুবরণরেখা’য়। আমরা জানি, সুবর্ণরেখা একটি নদীর নাম।
দেশভাগের পর নদীই হয়তো সীমান্তরেখা হয়ে গেছে। নগর কোলকাতার কয়েকজন থিয়েটারকর্মী এসেছে নদীর পাড়ে, নদীর ওপারেই বাংলাদেশ বা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান। থিয়েটার দলের অস্থির ও বিষণ্ণ নির্দেশক, যুবক ভৃগু তাকিয়ে থাকে বাংলাদেশের গ্রামটির দিকে। দলের নতুন সদস্যা যুবতি অনুসূয়াকে ভৃগু বাংলাদেশের গ্রামটি দেখিয়ে বলে, ‘ওই যে আমাদের গ্রাম, ওখানেই আমাদের বাড়ি ছিল কিন্তু কোনো দিন আমি আর ওখানে যেতে পারব না।’ চরম এক হতাশার অতল থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা দেশভাগের যাতনার আখ্যান বলে দেয় কয়েকটি সংলাপে—আমরা ঋত্বিককুমার ঘটকের ‘কোমলগান্ধার’ ছবিতে এরকমই দেখতে পাই। পুরো ‘কোমলগান্ধার’ ছবিতেই দেখি দেশভাগ এপিক হয়ে ওঠে। দেশভাগ হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। ‘সুবর্ণরেখা’তেও দেখি বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ভাইবোনের গল্প, ছোট্ট বোন সীতা ও তার ভাই অভিরামের গল্প। ভাইবোন হাঁটছে নদীপাড়ের বালিয়াড়ি ধরে, বাড়িহীন ভাইবোন হাঁটছে পৃথিবীতে। সীতা হাঁটতে হাঁটতেই প্রশ্ন করে, ‘দাদা, আমাদের নতুন বাড়িটা কোথায়?’ ভাই অভিরাম উত্তর দেয়, ‘ওই তো, সামনেই।’ একটি নতুন বাড়ির সন্ধানে তারা নদীপাড়ের বালিয়াড়ি ধরে হাঁটতে থাকে। দেশভাগে তারা বাড়ি হারিয়েছে। নতুন দেশের সীমানার ভেতর শরণার্থীদের জন্যে গড়ে ওঠা যে নবরতন কলোনি, আপাতত কি সেখানে আশ্রয় মিলবে? এরকমটি দেখতে পাই ঘটকের ‘সুবরণরেখা’য়। আমরা জানি, সুবর্ণরেখা একটি নদীর নাম।

টোকন ঠাকুর ও প্রতীতি দেবী
ঋত্বিকের শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’তে যেমন দেখা যায় পূর্ব বাংলা থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা এক উদ্বাস্তু তরুণী বঙ্গবালাকে, যাকে দেখে প্রোটাগনিস্ট নীলকণ্ঠ বাগচী, যে কিনা মাতাল, যে কিনা তার নিজের ভাষায় ‘আমি কোলকাতার ব্রোকেন ইন্টেলেকচুয়াল বা ভাঙা বুদ্ধিজীবী’, সেই নীলকণ্ঠ বাগচীর ঘরের দরজায় দিশেহারা তাড়া খাওয়া মেয়েটি নক করলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘কে, কে ওখানে?’ মেয়েটি ঘরে ঢুকে পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলে নীলকণ্ঠ বাগচী বলেন, ‘আশ্রয়? আশ্রয়ের সন্ধানে নীড়হারা আরেকটি পাখি, যে পাখির নাম, বাংলাদেশ।’ স্মর্তব্য, মাতাল লেখক নীলকণ্ঠ বাগচী বা ব্রোকেন ইন্টেলেকচুয়াল ক্যারেক্টারে পরিচালনার পাশাপাশি অভিনয় করেছেন স্বয়ং পরিচালক ঋত্বিককুমার ঘটক। ১৯৭৪-এ নির্মিত এটাই ঘটকের শেষ ছবি, এরপর ১৯৭৬-এ তিনি মাত্র ৫১ বছর বয়সে মারা গেলেন কোলকাতায়। আর দেশভাগের জ্বলন্ত দলিল তাঁর ‘মেঘে ঢাকা তারা’। ‘মেঘে ঢাকা তারা’তে ঋত্বিক ঘটক দেশভাগের যন্ত্রণাকে আরও বিস্তারিত এঁকেছেন আরও দহন-মহিমা মুড়িয়ে, যেখানে ক্ষতটা আরও বেশি দৃশ্যমান হতে দেখি আমরা। সম্পূর্ণ করা ঘটকের বাকি কাজ বলতে ‘নাগরিক’, যেটি তার প্রথম কাজ, ১৯৫২তে নির্মিত কিন্তু কী অপার দুর্ভাগ্য যে, ১৯৭৬ সালে পরিচালকের মৃত্যুর পরের বছর ১৯৭৭ সালে সে ছবি মুক্তিপ্রাপ্ত। এছাড়া ‘অযান্ত্রিক’, ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ও কোলকাতা থেকে বাংলাদেশে এসে নির্মিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মালোপাড়ার জলপুত্র অদ্বৈত মল্ল বর্মণের একমাত্র উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। আর বাকি কাজ কিছু তথ্যচিত্র বা অসমাপ্ত খণ্ড খণ্ড কিছু প্রয়াস—এই হচ্ছেন ঋত্বিক ঘটক। এককথায় দেশভাগের এপিক নির্মাণে ঋত্বিক ঘটকই এক জ্বলজ্যান্ত আর্কাইভ। দেশভাগ ট্রিলজি হয়ে উঠেছে তাঁর কাজে। হয়তো ট্রিলজি ছাড়িয়েও গেছে বলা যায়। এই ২০২৫-এ এসেও আমরা অনুভব করি, ঋত্বিককুমার ঘটক কতখানি আলোচ্য, ভাবোচ্য, যথেচ্ছ তর্ক-বিতর্কের অনুঘটক। এবং এটা এত দিনে প্রকাশ হয়ে গেছে যে, শিল্পকলার নানাবিধ মাধ্যমে দেশভাগ কমবেশি ফোকাস হয়ে থাকলেও, সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে ঋত্বিক ঘটকের চোখে, তাঁর ছবিগুলোর ভেতর দিয়ে। এতটা আর কেউই ধরে রাখতে পারেননি গান্ধি-জিন্নাহ-মাউন্ট ব্যাটেনের নেতৃত্বে ভাগ হয়ে যাওয়া, র্যাডক্লিফের মানচিত্র আঁকা দেশভাগকে। ঋত্বিক পেরেছেন বা একথাও বলা চলে, তিনি আত্মগত এক দায়বদ্ধতায় পারতে বাধ্য হয়েছেন নিজের জীবনব্যেপে, যে জীবন বড্ড স্বল্পায়ুর এবং ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। এবং যে জীবনে তিনি বাঙালিকে বলে গেলেন, ‘ভাবো, ভাবা প্রাকটিস করো।’
৪ নভেম্বর ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন। এবছর এই মহান নির্মাতার জন্মশতবার্ষিকী। তিনি ১৯২৫ সালে জন্মেছেন পুরোনো ঢাকার হৃষীকেশ দাস রোডের এক ঝুলন বাড়িতে এবং ঋত্বিকের যমজ প্রতীতি দেবী ঘটক জন্মেছেন পাঁচ মিনিটের অনুজ সহোদরা হিসেবে।
৪ নভেম্বর ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন। এবছর এই মহান নির্মাতার জন্মশতবার্ষিকী। তিনি ১৯২৫ সালে জন্মেছেন পুরোনো ঢাকার হৃষীকেশ দাস রোডের এক ঝুলন বাড়িতে এবং ঋত্বিকের যমজ প্রতীতি দেবী ঘটক জন্মেছেন পাঁচ মিনিটের অনুজ সহোদরা হিসেবে। তাঁদের বাবা সুরেশ ঘটক ছিলেন তৎকালীন ঢাকার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট। সুরেশ ঘটকের প্রথম সন্তান ছিলেন সাহিত্যিক মনীশ ঘটক। মনীশ ঘটকের জন্ম ১৯০০ সালে। মধ্যে আরও কয়েক সন্তানের পর বা ২৫ বছর পর এই যমজ সন্তানের জন্ম। যমজের ডাকনাম ভবা ও ভবি। ভবা হচ্ছেন ঋত্বিক, ভবি হচ্ছেন প্রতীতি দেবী। প্রতীতি দেবী অর্থাৎ ভবি আমাদের এই শহরেই বসবাস করতেন, সিদ্দেশ্বরীতে, রমনা সেঞ্চুরি টাওয়ারে, তাঁর মেয়ে প্রাক্তন সাংসদ আরমা দত্তের সঙ্গে। ভবা বা ঋত্বিক ঘটক মাত্র ৫১তে চলে না গেলে তিনিও থাকতেন কোলকাতায়। কী অদ্ভুত কথা, নাহ? যমজ তাঁরা, ঢাকায় জন্মেছেন। কিন্তু দেশভাগের ফলাফলে একজন কোলকাতার নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকলেন এবং একজন ঢাকার নাগরিক। প্রাচ্যের এদিকে এমনটি খুব সচরাচর নয়। তাই দেশভাগ মানে ঋত্বিককুমার ঘটকের কাছে যমজ ভাইবোনের ভাগ হয়ে যাওয়া। নাড়ির ফুল পোঁতা মাটি ভাগ হয়ে যাওয়া। উল্লেখ করি, ঋত্বিক ঘটকের কয়েক ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বড় ছিলেন, সেই মনীশ ঘটকের মেয়ে হচ্ছেন মহাশ্বেতা দেবী। মহাশ্বেতা দেবীর ডাকনাম খুকু। খুকু, ভবা ও ভবি বয়সের হিসেবে কাছাকছি সময়ে তাদের জন্ম। মহাশ্বেতা দেবীর স্বামী ছিলেন নাট্যকার ও অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য, সেই চল্লিশের দশকের গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা একজন। ঋত্বিকের ছবিতেও তাঁকে প্রায়শই দেখি আমরা। বিজন বাবু ছিলেন রাজবাড়ি-ফরিদপুরের লোক। বিজন ভট্টাচার্য ও মহাশ্বেতা দেবীর পুত্র কবি ও কথাসাহিত্যের এক নতুন গণমুখী উন্মাদনা নবারুণ ভট্টাচার্য, আমরা পড়েছি তাঁর কবিতা, ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না, এই জল্লাদের ভূমি আমার দেশ না।’ পড়েছি ও দেখেছি তাঁর ‘হারবার্ট’, ‘ফ্যাতাড়ু।’ পড়েছি ‘অ্যাকুরিয়াম’। ২০০২ সালে সার্ক রাইটার্স ফাউন্ডেশন কার্যক্রমের আওতায় সাহিত্য আকাদেমির আমন্ত্রণে ‘তরুণ কবি’ অভিধায় আমি প্রথমবারের মতো কোলকাতায় গিয়েছিলাম, সঙ্গী আমাদের কবি বন্ধুজন শাহনাজ মুন্নী। আকাদেমি থেকেই আমাদের একজন গাইডের সঙ্গে একদিন আমরা যাই দেবেশ রায়ের বাড়িতে, সম্ভবত কল্যাণীতে, যেমন ট্যাক্সিতে চড়ে আরেক দিন যাই মহাশ্বেতা দেবীর বাসায়, আড্ডার জন্য। তো গলফগ্রিনে যাওয়ার সময় কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফের গাইড লোকটি ট্যাক্সিতে বসে তো টেরই পেতে দেননি যে, তিনিই কবি নবারুণ ভট্টাচার্য। পরে, গলফ গ্রিনে মহাশ্বেতা দেবীর তৎকালীন বাসায় যাওয়ার পর সব পরিষ্কার হলো যে, তিনি বিজন ভট্টাচার্যের ছেলে বা ঋত্বিক ঘটকের ভাগ্নেও বটে। কয়েক বছর আগে, নবারুণদা আগে এবং মহাশ্বেতাদি পরে চলে গেছেন। তাঁদের প্রয়াণ নিয়ে ভবি বা ঋত্বিক ঘটকের যমজের সঙ্গে মানে প্রতীতি দি’র সঙ্গে সিদ্দেশ্বরীতে বসে আমার কথাও হয়েছে, সেই কথা বলার সময় প্রতীতিদি বলছিলেন, ‘শোনো, দীর্ঘ আয়ু অভিশাপের মতো একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।’
আমি বললাম, ‘রবীন্দ্রনাথ হয়তো ঠিক বলেননি।’
দিদি বললেন, ‘কেন?’
বলেছি, ‘তাহলে ভবার মতো তোমার সঙ্গেও আমাদের দেখা হতো না।’
প্রতীতি দেবী বললেন, ‘এই যে তোমরা আসো, আমার জন্যে আসো? আসো তো ভবার জন্যে, ঋত্বিকের জন্যে, ওর কাজ ওর ছবিগুলোর জন্যে আসো। নইলে আর আমি কে? বড়জোর ধীরেন দত্তের পুত্রবধূ, তাই না?’
১৯৫৪ সালে অবিভক্ত পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তার আগে ১৯৪৮-এ পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে বসে বাংলা ভাষার প্রশ্নে ধীরেন বাবু তাঁর অকপট সাহসী উচ্চারণ ব্যক্ত করেছিলেন। পরে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চ লাইটের পর ২৯ মার্চ কুমিল্লায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিজ বাড়িতে ভাষাসৈনিক ও ভারতবর্ষের সুবিদিত রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ওপরে অমানবিক নির্যাতন চালায় এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান। সন্দীপ দত্ত তার পুত্র, সন্দীপ দত্তের বধূই প্রতীতি দেবী ঘটক, আমাদের প্রতীতিদি বা ঋত্বিক ঘটকের যমজ।

টোকন ঠাকুর, আরমা দত্ত ও প্রতীতি দেবী
আমি নানা বিষয়েই দিদির সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতাম বটে, কারণ, অনেক কিছুই জানা হতো তাতে আমার। প্রতীতি দেবীর ঘরে নানান দেশ থেকে যমজ ভাইবোনের ছোটো ছোটো পুতুল পুতুল জোড়া ভাস্কর্য, যেগুলো তাঁর মেয়ে (১৯৭১-এ রোকেয়া হলের ছাত্রনেত্রী ও আওয়ামী লীগ সরকারের সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদ)—আরমা দত্ত এনে দিয়েছেন। আরমা দত্ত আর রাহুল দত্ত, ভাইবোন—প্রতীতি দেবীর সন্তান, ঋত্বিক ঘটকের ভাগ্নে-ভাগ্নি। রাহুলদা প্রায়ই আমাকে ফোন করেন, ‘টোকনদা, আজ ডেইলি স্টারে ছোটো মামার ওপরে একটা আর্টিকেল ছেপেছে, পড়েছ?’
ছোটো মামা বলতে ঋত্বিক ঘটক, রাহুলদা’র মায়ের যমজ ভাই। যাদের জন্ম হয়েছিল ঢাকায়, সেই ১৯২৫ সালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে এসে দুপুরবেলা আহ্নিক-আতিথ্য নিয়েছিলেন তদানীন্তন ঢাকার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট সুরেশ ঘটকের হৃষীকেশ দাস রোডের বাড়িতে। কথায় কথায় একদিন প্রতীতিদি-কে বললাম, ‘তোমার আর ঋত্বিকের বয়স তখন মাত্র ১ বছর, তাই না?’
প্রতীতিদি বললেন, ‘হ্যা।’
বললাম, ‘তাহলে তো রবীন্দ্রনাথ নিজে তোমাদের কোলে নিয়ে থাকতে পারেন।’
দিদি বললেন, ‘তা তো নিতেই পারেন, আমি আর ভবা তখন শিশু।’
বললাম, ‘সেকারণেই, ধরো কোলে নেওয়ার পর তোমরা রবীন্দ্রনাথের গায়ে হিসুও করে দিতে পারো, তাই না?’
এক পশলা হাসাহাসি হয় আমাদের। তবু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এমন ইয়ার্কি দিদি মানতে পারছিলেন না। আমরা সেকাল-একাল একাকার করে ফেলি এবং প্রতীতিদি’র সঙ্গে আড্ডায় সেটা অনায়াসেই সম্ভব। সাহিত্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত দিদির লেখা একটি ছোট্ট বই আছে, ‘ঋত্বিককে শেষ ভালবাসা’। বললাম, দিদি, ‘সুরমা ঘটকের বইও পড়েছি।’
দিদি বললেন, ‘শ্রীহট্টের মেয়েরা তো ভালো না। ভবাকে ঠিক মতো বুঝতেই পারেনি। ভবাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। তবে ওখানকার আলীদা আসতেন আমাদের বাসায়, আলীদা ভালো।’
বললাম, ‘আলীদা কে?’
দিদি বললেন, ‘সৈয়দ মুজতবা আলী, পড়োনি আলীদা’র লেখা?’
‘পড়েছি।’
দিদি একদিন বললেন, ‘আমার মৃত্যুর পর আর ডেডবডি দেখতে এসো না।’
বললাম, ‘কেন?’
প্রতীতিদি বললেন, ‘জীবদ্দশার চেহারাটাই মনে থাকবে তাহলে, আমি সেটাই চাই।’
কথায় কথায় কত কথা হয়। আমাদের নির্মাণাধীন ছবি ‘কাঁটা’র টিম নিয়ে কয়েকবার গেছি দিদির সঙ্গে আড্ডা দিতে। এলো এক ৪ নভেম্বর, যমজ ভাইবোনের জন্মদিন। আমরা কেক ও গোলাপ নিয়ে গেছি। কেকের ওপরে লেখা হয়েছে, ‘ভবা-ভবির জন্মদিন—কাঁটা’র পক্ষ থেকে।’ সেদিন দিদির মেয়ে আরমাদি’ও পুরো সন্ধে আমাদের সঙ্গে আড্ডায় যুক্ত থাকলেন। গান-কবিতা হলো। একসময় দিদি বললেন, ‘আচ্ছা, এখন ঢাকায় “বাংলা” কোথায় পাওয়া যায়, জানো? মরার আগে একদিন “বাংলা” খাব। “বাংলা” ভাবলেই ভবার কথা মনে পড়বে। একসঙ্গে মাত্র ৫ মিনিটের ব্যবধানে মায়ের পেট থেকে জন্মালাম, ও কত আগেই আমাকে একা রেখে চলে গেল।’
চুপ করে আছি, ঠিক কী বলব ভাবছিলাম, তখন দিদিই ফের বললেন, ‘সাঈদ জানে, বাংলা কোথায় পাওয়া যায়।’
বললাম, ‘কোন সাঈদ?’
‘ওই যে, হামিদুরের ভাই সাঈদ। হামিদুর তো আর্টিস্ট। আর সাঈদ নাটক লেখে।’
আমাদের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নকশাবিদ ভাস্কর নভেরা আহমেদের সঙ্গে সংযুক্ত আর্টিস্ট হামিদুর রাহমানের ভাই নাট্যকার সাঈদ আহমেদের কথা বলছেন দিদি। আমি তখন জানাইনি, সাঈদ আহমেদও মারা গেছেন।
‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি পড়তে পড়তে সে রাতে কাগজ ছিল না বলে ঋত্বিক যে তাঁর যমজের একটি সাদা শাড়ির ওপরেই কলম দিয়ে চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করেন, দিদি বলেন সে কথা।
‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি পড়তে পড়তে সে রাতে কাগজ ছিল না বলে ঋত্বিক যে তাঁর যমজের একটি সাদা শাড়ির ওপরেই কলম দিয়ে চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করেন, দিদি বলেন সে কথা। কথায় কথা বাড়ে, কথার শুরু আছে, শেষ নেই। নেই?

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ সিনেমার একটি দৃশ্যে অভিনেত্রী কবরী
আছে। কথারও নিশ্চয়ই কোনো স্টেশন আছে, যেখানে কথারা একটু দাঁড়ায়, কথা একটু এদিক-ওদিক চায়। হয়তো তখন আরও কিছু কথা এসে ফের যুক্ত হয় দাঁড়িয়ে পড়া কথার পাশে। ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে আমাদের কথা আর শেষ হতেই চায় না। কথা আবার নতুন শক্তিতে চলতে থাকে। কথা চলতে থাকে ‘কোমলগান্ধার’ ছুঁয়ে, কথা আমাদের ‘সুবর্ণরেখা’ নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে নিশ্চয়ই একটি নতুন বাড়ি পাওয়া যাবে। আমাদের কথারা সেই নতুন বাড়িতে উঠে পড়বে! আমাদের কথারা দেশভাগের এত বছর পরেও ঋত্বিককুমার ঘটকের ছবির ভেতর দিয়ে ধাবমান থেকে যাচ্ছে। কথার সঙ্গে যাচ্ছি আমরাও। আমরা কারা? আমরাও কি কিছু কথা হয়ে থেকে যাচ্ছি, নদীর মতো বেঁকে যাচ্ছি, স্বপ্ন-টপ্ন রেখে যাচ্ছি? কার জন্যে রেখে যাচ্ছি?
ঢাকায় জন্ম নিলেও ঋত্বিক ঘটকের বাড়ি ছিল রাজশাহী। পদ্মাপাড়ে। পদ্মার স্মৃতি আমৃত্যু তাড়িয়ে মেরেছে ঋত্বিককে। রাজশাহী হলেও আদিতে হয়তো তাঁরা পাবনার লোক। পাবনায় কি তাঁরা কোনোকালে বাগচী ছিলেন? এই তো আবার মনে পড়ল নীলকণ্ঠ বাগচীর কথা, যিনি ‘যুক্তি-তক্কো আর গপ্পো’তে বলছেন, ‘আমি কোলকাতার ব্রোকেন ইন্টেলেকচুয়াল।’ যিনি সারাক্ষণ মদিরার ঝুলন মায়ায় দুলছেন, যিনি খালি বোতলটা রাস্তায় ছুড়ে দিয়ে বলছেন, ‘ওহ! কী উন্মুক্ত এই হাওয়া, তরী অকূলে ভিড়ছে।’

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ চলচ্চিত্রের কিশোর মালো চরিত্রের অভিনেতা প্রবীর মিত্র ‘কাঁটা’ সিনেমার রিহার্সেল সেটে
আবার সেই কথা এসে গেল। আমার প্রথম ফুললেন্থ প্রজেক্ট ‘ব্ল্যাকআউট’ যা অধ্যাবধি আনরিলিজড এবং ‘ব্ল্যাকআউট’ টাইটেলে উৎসর্গ করা হয়েছে ঋত্বিককুমার ঘটক ও কুরোসাওয়াকে। ঘটকের একেকটি ছবি আমি কতবার দেখেছি ও দেখি, হিসেব নেই। সিনেমার আড্ডায় কতবার ঋত্বিক ঘটক প্রসঙ্গক্রমে আসেন, কতভাবে আসেন, কী ঢাকায় কী কোলকাতায়—হিসেব নেই। সত্যি, এত অনিবার্য তিনি! বিস্ময় ফুরোয় না। বিস্ময় এসে দাঁড়িয়ে থাকে দরজায়। বিস্ময় এসে চোখের মধ্যে বাসা বোনে। কেন? এত শক্তি বিস্ময়ের? একদিন প্রবীর মিত্রকে কাঁটা ক্যাম্পে এনেছি শুধু ঋত্বিককে আরেকটু বোঝার জন্যে, কেন না যৌবনে প্রবীর মিত্রই করেছেন কিশোর মালো ক্যারেকটার, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবিতে। তিতাসের প্রযোজক হাবিবুর রহমান খানকেও জিজ্ঞাসা করেছি কিছু কথা, যদি ‘লাইভ’-ঋত্বিক দেখা মানুষ থেকে এই ব্রোকেন ইনটেকচুয়ালকে আরেকটু পেতে পারি। সেই সক্ষমতা তো তিনি দেখিয়ে গেছেন। তাই না?
যন্ত্রণাই কি শক্তির উৎস হয়ে আছে? দেশভাগই কি নির্মাণ করেছে এই নির্মাতাকে? ভালোবাসাই কি প্রবল প্রেরণা হয়ে কাজ করেছে? আমাদের কথা চলতেই থাকে, আমরাও চলতে থাকি কথার সঙ্গে, যেন কথার সঙ্গে আমরা একটি নতুন বাড়িতে পৌঁছুব। হঠাৎ দেখি, এক বৃদ্ধ নদীপাড়ে বসে খোলা গলায় গান ধরেছেন—‘এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যে জাগনার চর, তারই মাঝে বইসা আছেন শিবু সওদাগর…’
আমাদের কথারা নদীর মতো, বহে বহে যায়। সেই নদী ভাগ হয়ে যায়। নদী কী করে ভাগ হয়? যমজের জন্যে মাতৃজঠর কী করে ভাগ হয়? মনে হয়, আবার কথার সঙ্গে আমাদের হণ্টন শুরু হলো। আমরা কথার সঙ্গে আবার হাঁটতে থাকি, আমাদের ধাবমান পা, ধাবমান মন, আমরা কোথায় যাচ্ছি? কথা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?
সংযুক্তি:
এই লেখাটা প্রথম লিখি যখন, কয়েক বছর আগে, প্রতীতিদি তখনও আছেন পৃথিবীতে। এরপর দিদি চলে গেছেন করোনাপীড়িত সময়ে। দিদির প্রয়াণের দিনে আবার যাই রমনা সেঞ্চুরি টাওয়ারে। অনেক লোক। দিদির ছেলে রাহুল দত্ত নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ালেন। কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। ঢাকার অভিজাত পল্লির বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ উপস্থিত। মনখারাপ করে দাঁড়িয়ে আছি আমরা কজন বন্ধু, যারা দল ধরে আগেও এসেছি দিদির সঙ্গে আড্ডা দিতে। সেই আড্ডা মূলত ঋত্বিক ঘটককে নিয়েই কথাবার্তা। হয়তো দিদি বললেন, ‘সিক্সটি ফোরের সময়টা, রায়ট বেঁধে গেল, আমি তখন কিছু বছর পরিবারের সঙ্গে কোলকাতায়ই ছিলাম। দাঙ্গায় ঘরবাড়ি সব শেষ, মাধবী এলো বরিশাল থেকে। কোলকাতায় তখন ওর জানাশোনা তেমন কেউ নেই, কাজ নেই। মাধবী তো দেখতে সুন্দর ছিল। ভবা ওকে কাজ দিল। মানিকদা’র কাছেও ওকে নিয়ে গেছি একদিন। মানিকদা কাজ দিলেন। ‘সুবর্ণরেখা’তে মাধবী কাজ করল, মানিকদা করালেন চারুলতা, সেই সেদিনের কথা সব…‘দিদি অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছিলেন। দিদি একদিন বলছিলেন কোলকাতায় যখন ভাড়াটিয়া ছিলেন, সেই বাড়ির কথা। বাড়িটির মালিক সেন পরিবার। একজন সেন সুচিত্রা সেন, পাবনার লোক এবং বাংলার মহানায়িকা তিনি তখন। তাঁর স্বামী দিবানাথ সেন। মাঝরাতে মদ্যপ স্বামী দিবানাথ স্ত্রী সুচিত্রা সেনের গায়ে হাত তুলতেন, নিচতলার ভাড়াটিয়া হিসেবে প্রতীতিদি’রা সেই ঝগড়াঝাটির অনিচ্ছুক সাক্ষী হতেন। দিদি বললেন একদিন, ‘খুকু অঙ্ক ভালো পারত না, আমার খাতা দেখে লিখত।’ খুকু হচ্ছেন মহাশ্বেতা দেবী, বড় ভাই মনীশ ঘটকের মেয়ে।’ কত কথা হতো দিদির সঙ্গে! মারা যাওয়ার পর আর যাওয়া হচ্ছে না সেঞ্চুরি টাওয়ারে। তো দিদির লাশ দিয়ে দেওয়া হবে পিজি হাসপাতালে, জানা ছিল আমাদের। দিদি বলেছিলেন, ‘আমার মরা মুখটা দেখবা না, আমি জীবিত থাকতে চাই তোমাদের কাছে।’ সেই কথা রাখা হয়নি আমার। সেঞ্চুরি টাওয়ার প্রাঙ্গণে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকের ভিড়ে, হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সের সামনে পড়ে গেলাম। তাকাতেই দেখি, অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে সাদা কাপড়ে মোড়ানো দিদির মরদেহ শুইয়ে রাখা হয়েছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে। কী করব, দেখা তো হয়েই গেল। দিদির ছেলে রাহুলদা অর্থাৎ শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতিছেলে নির্বিকারভাবে বললেন, ‘দ্যাখো ঘটক পরিবারের শেষ প্রতিনিধি আজ চলে গেলেন।’ এখনও মাঝেমধ্যেই রাহুলদা আমাকে ফোন করেন, কিন্তু দিদিই তো নেই আর! রাহুলদা মায়ের কথা বলেন, তাঁর মামা আমাদের অগ্রজ বন্ধু ঋত্বিককুমার ঘটকের কথা বলেন। অর্থাৎ কথা চলে আমাদের। কথা আমাদের ফুরোয় না। কথা আমাদের কোথাও নিয়ে যেতে চায়, কথা কোথায় নিয়ে যেতে চায়?
কথা শতবর্ষ অতিক্রম করতে চায়।
১৯২৫-২০২৫। ৪ নভেম্বর। জন্মশতবার্ষিকী ভবা-ভবির। শ্রদ্ধা আজীবন কীর্তিমানের জন্যে। আমার নির্মিত ‘কাঁটা’ এবছরেই মুক্তি দেবো। ‘কাঁটা’ ছবিতেও ঋত্বিকের প্রতি ঋণ আছে আমার। ‘কোমলগান্ধার’-এ ব্যবহার করা দুইটা ধামাইল গীত ‘কাঁটা’তেও ব্যবহার করলাম নতুন করে গাইয়ে নিয়ে। ধামাইল যদিও বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের গান। একেকটি গানের গায়কীও একটু আধটু হেরফের করেও গাওয়াগাওয়ি হয়তো হয়। ‘কাঁটা’র জন্যে আমরা সুর নিয়েছি ‘কোমলগান্ধার’-এ ব্যবহারের অনুরূপেই। একটি, ‘মিস্ত্রি বানাইছে পিঁড়ি’ ও অন্যটি ‘আমের তলায় ঝাম্মুর ঝুমুর…’ । ‘কোমলগান্ধার’ ১৯৫৮ সালের ছবি। তখনকার শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ানো হয়েছিল গীত দুইটা। আমাদের ছবি কাঁটা-কুটির গান-এর জন্যে এই গীত গেয়েছে এখনকার একদল শিল্পী, ক্লাস সেভেব থেকে ইলেভেনের ছাত্রী। আরও দারুণ কিছু গান আছে ‘কোমলগান্ধার’-এ। কী সুন্দর। ‘কাঁটা’র শরীরে গান ঢুকে গেল ‘কোমলগান্ধার’ থেকেও। কারণ? ভালোবাসা।
ঋত্বিক ঘটককে মর্ম দিয়ে অনুভব করা যেকোনো মানুষ, সে পশ্চিমবাংলারই হোক বা হোক আমাদের বাংলাদেশের, তাঁর জন্যেও আমার অনুরূপ ভালোবাসা ব্যক্ত করি আমি।
ভালোবাসার কথা আর শেষ হতে চায় না। ভালোবাসার কথা ঘুরতে ঘুরতে একদিন তোমার কাছেও পৌঁছে যাবে, এরকমই বলে যায় হাওয়া। হাওয়াকে তো কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। নদীর এপারের হাওয়া ওপারে বহে যায়, আর নদীর ঠিক মাঝ বরাবর দেশভাগের সীমান্তরেখা জলে প্রবহমান। মানুষের রাজনীতি কীভাবে প্রাকৃতিক নদীজল ভাগ করে গেল! থাক সে-সব অসঙ্গতির কথা আজ। কথা আজ শুধু শতবর্ষের ঋত্বিক ঘটকের জন্যে, তাঁর যমজ বোন বিদুষী প্রতীতি দেবী ঘটকের জন্যে…
কথা, এবার একটু থামো। চুপচাপ বসে থাকো…

জন্ম ১ ডিসেম্বর, ১৯৭২, ঝিনাইদহ। বেড়ে ওঠা, বসবাস: ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, খুলনা ও ঢাকা। একাডেমিক (সর্বশেষ) পড়ালেখা: চারুকলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ প্রকাশনা: কবিতার বই কয়েকটি, গদ্যের বই কয়েকটি। সম্পাদিত গ্রন্থ: ২টি। ছবি নির্মাণ: ‘ব্ল্যাকআউট’ (২০০৬) আনরিলিজড। ‘রাজপুত্তুর’ (২০১৪), ‘কাঁটা’ (২০২৫) । পেশা: আর্ট-কালচার চষে বেড়ানো।