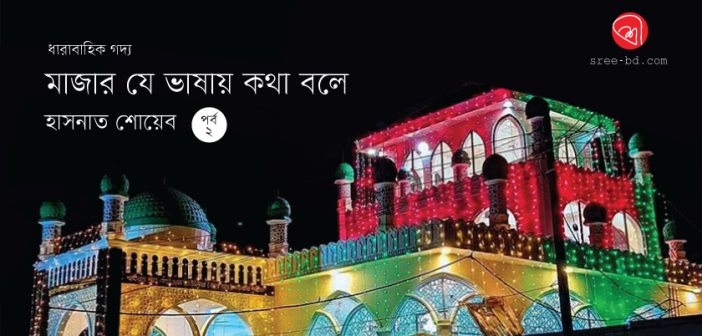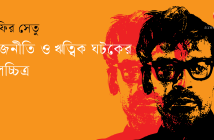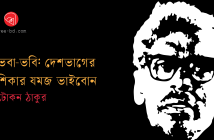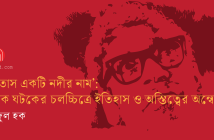শৈশব-কৈশোরের নির্জন বিকেল, উৎসবমুখর রাত কিংবা গ্রামীণ জীবনের নীরব বিস্ময়ে মাজার এক অদ্ভুত টান রেখে যায় মানুষের মনে। লেখক হাসনাত শোয়েব তাঁর নতুন ধারাবাহিকে ফিরে গেছেন সেই টানে—ব্যক্তিগত স্মৃতির অলিগলি পেরিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে মাজার কেবল আধ্যাত্মিক আশ্রয় নয়, বরং হয়ে উঠেছে লোকজ সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতীক। গণমানুষের ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে সেখানে মিলন, সমবেদনা ও একাত্মতার অনুভব। কিন্তু এই আশ্রয়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে সাম্প্রতিক এক অন্ধ প্রবণতা—মবের হামলায় মাজার ভাঙার অপসংস্কৃতি। শোয়েব তাঁর লেখায় এর অন্তর্লীন কারণ ও সামাজিক অভিঘাত অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিন পর্বের এই ধারাবাহিকের আজ প্রকাশিত হলো এর দ্বিতীয় পর্ব।
শাব্দিকভাবে মাজার একটি আরবি শব্দ যার অর্থ জিয়ারতের স্থান। তবে আমরা সাধারণত পীর-বুজুর্গদের কবরকেই মাজার বলে থাকি। মানে যার কবরকে আমরা মাজার বলছি তিনি সাধারণ কেউ নন, বিশেষ গুণাবলি সম্পন্ন একজন বুজুর্গ। তবে মাজার বলতে আমি বুঝি এক ধরনের আশ্রয়। এবার ‘আশ্রয়’ শব্দটিকে আপনি যত দূর সম্ভব বিস্তৃত করে নিতে পারেন। ক্যানভাসটাকে বাড়িয়ে নিতে পারেন অনেক দূর পর্যন্ত। এখন আশ্রয়টা আসলে কেমন? ইট-কাঠের একটা দালান কীভাবে মানুষের আত্মা ও শিকড়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে? তা ছাড়া একেকটা মাজারের কয়েক শ বছর পরও অস্তিত্বশীল হয়ে সটান দাঁড়িয়ে থাকা খুব সাধারণ কোনো ঘটনা নয়।
সেই কবে কোনো পীর-দরবেশ-বুজুর্গ ব্যক্তি ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য এক স্থানে ভ্রমণ করেন। অতঃপর তাঁকে দেখে, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে লাখ লাখ মানুষ ধর্মান্তরিত হচ্ছেন। এটা মোটেই সাদামাটা কোনো ঘটনা নয়। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টা গভীর চিন্তার খোরাকও দেয়। বিশেষ করে উগ্রপন্থা ও মারমুখী শরীরী ভাষা ধর্মকে ‘গণ’ থেকে আলাদা করে ফেলছে, সেই বাস্তবতায় বহু কাল একজন ব্যক্তির ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষ পিতৃধর্ম বদলে ফেলছে, এটা খুব সাধারণ কোনো বিষয় নয়।
কীভাবে চেতনা ও ভাবগত বিপ্লব সাধন করেছে তা ড. এনামুল হকের লেখা ‘বঙ্গে স্বূফী প্রভাব’ বইয়ে উঠে এসেছে এভাবে, ‘মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে, যতগুলো নবভাবের আগমনে, এ দেশের চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে স্বূফী ভাবধারাই প্রধান৷ ভাব-প্রবণ-বঙ্গ এ নব নব ভাবধারার সংস্পর্শে চমকিত ও পূর্ণরূপে বিপ্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ বিপ্লাবনের ফলে এদেশে কত নব নব ভাব ও চিন্তার বিকাশ ঘটিয়াছিল; আজ তাহার ইতিহাস আমাদের নিকট কে উন্মুক্ত করিবে!’
মাজারের অস্তিত্ব শুধু এই ভূমিতেই আছে তাও নয়। ইসলামের শুরু থেকেই মাজারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও ভাঙাভাঙির পরও ইসলামের শুরু থেকেই মাজার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তবে এখানে আমার আলাপের প্রেক্ষিত এই অঞ্চলের মাজার ও মাজারকেন্দ্রিক সংস্কৃতির। আরও নির্দিষ্ট করে বললে চট্টগ্রামের মাজার।
সুফি ভাবধারা হাওয়ার ওপর এসে এখানে জুড়ে বসেনি। এই অঞ্চলের যে চিরকালীন ভাববাদী চেতনা তা সুফিবাদী ভাবনাকে রাস্তা করে দিয়েছে। সেই রাস্তাতে হেঁটেই তাসাউফের বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন অলি-আউলিয়ারা। কীভাবে চেতনা ও ভাবগত বিপ্লব সাধন করেছে তা ড. এনামুল হকের লেখা ‘বঙ্গে স্বূফী প্রভাব’ বইয়ে উঠে এসেছে এভাবে, ‘মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে, যতগুলো নবভাবের আগমনে, এ দেশের চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে স্বূফী ভাবধারাই প্রধান৷ ভাব-প্রবণ-বঙ্গ এ নব নব ভাবধারার সংস্পর্শে চমকিত ও পূর্ণরূপে বিপ্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ বিপ্লাবনের ফলে এদেশে কত নব নব ভাব ও চিন্তার বিকাশ ঘটিয়াছিল; আজ তাহার ইতিহাস আমাদের নিকট কে উন্মুক্ত করিবে!’
এটাও সত্য যে, ইসলামের ডাকে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে শুধু পীর-দরবেশের একক ভূমিকা ছিল এমনও নয়। তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নানা হিসাব-নিকাশও এখানে ব্যাপকভাবে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে।
এই বিষয়টি নিয়ে আকবর আলী খান তাঁর ‘বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ’ বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেখানে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা, ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়ন, হিন্দুদের নিপীড়ন, অনুকূল গ্রামীণ পরিবেশে এবং পীরদের ভূমিকার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মোটাদাগে সম্ভাব্য সবগুলো কারণ একত্রিত হওয়ার পরই এই চেতনাগত বিপ্লবটা সম্পন্ন হয়েছে এবং এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের গণবিস্ফোরণ ঘটেছে। তবে আমরা যেহেতু পীর-দরবেশ এবং মাজার নিয়ে আলাপ করছি তাই আপাতত সেখানেই প্রাসঙ্গিক থাকার চেষ্টা করছি।

মৌলানা শাহ সুফি সৈয়দ খাজা ইউসুফ আহমেদ মাজার শরীফ
মধ্যাহ্ন
এই অঞ্চলে সুফিবাদী ও তাসাউফপন্থী ইসলামের বিকাশে অলি-আউলিয়াদের ক্রিয়াশীল কন্ডাক্টর হিসেবে দেখা যায়। অর্থাৎ সব যৌক্তিক কারণ উপস্থিত থাকার পর ওনারা এসে সেটাকে সঠিক পথে চালিত করেছেন। তাদের ব্যক্তিত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, নির্লোভ, প্রতিবাদী এবং লড়াকু মানসিকতা মুহূর্তের মধ্যে এই অঞ্চলের মানুষদের আকৃষ্ট করে। এমনকি যারা পিতৃধর্ম ত্যাগ করার সাহস দেখাতে পারেননি, তারাও এই পীরদের প্রভাব বলয়ের বাইরে যেতে পারেনি। যে কারণে ধর্ম পালন এবং পীরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ধারাকে আলাদা রাখতে পেরেছিলেন। তবে এর ফলে যে আন্তধর্মীয় সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে তাও স্বীকার করে নিতে হবে।
দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রচার মূলত পীরদের দ্বারা সম্পন্ন হলেও, বাংলা অঞ্চলেই সাফল্যের হার বেশি ছিল। সেটার পেছনে নানা কারণের কথা ওপরেই বলা হয়েছে। তবে এখানে প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের আধিক্য এবং ধর্মীয় নমনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। নানাভাবে নিষ্পেষিত মানুষ ইসলামের ভেতর দিয়ে নিজেদের মুক্তির একটা সম্ভাব্য রূপরেখাও তারা তখন এঁকে ফেলতে পেরেছিল। বলা বাহুল্য, সেই ইসলাম মোটেই এখনকার একাংশের উগ্র ও অনমনীয় ইসলাম ছিল না। ইসলামের যে উদারতা, সাম্য এবং ন্যায়ের বাণী সেটা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেই মানুষেরা। যারা নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাসহই এই ইসলামি ধারায় নিজেদের শামিল করেছিলেন।
আর আল্লাহর যে আউলিয়াকে ঘিরে এত বড়ো একটা বিপ্লব, তাকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখার বাসনা থেকেই মূলত মৃত্যুর পর পীরদের সমাধিকে পবিত্র তীর্থস্থানে রূপান্তর করা হয়। যে মাজারকে ঘিরে ধীরে ধীরে তৈরি হয় সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি ধর্মীয় প্রাণ প্রবাহের। এটি শুধু ভাবগত বা অধিবিদ্যক কোনো সত্তা নয়। এটি একেবারে দৃশ্যমান একটি সত্তা। যার মধ্য দিয়ে ভক্ত-মুরিদগণ নিজেদেরও অস্তিত্বশীল রাখে।
আমাদের এই অঞ্চলে প্রতিটি মাজার প্রথমত এক-একটি সাংস্কৃতিক হাব হিসেবে বিকশিত হয়েছে। সেখানে মানুষ শুধু যে নিজের ধর্মীয় তাগিদে যান তা নয়, একপর্যায়ে এই মাজারগুলোকে তারা নিজেদের যাপনের অংশও মনে করেন। এই মাজারগুলো তাদের ক্ষমতায়নের প্রতীকও। তারা মনে করে তাদের সঙ্গে কেউ একজন আছেন, যিনি শক্তিশালী এবং তাদের পক্ষের। মাজারে শায়িত আউলিয়াকে তারা নিজেদের প্রতিনিধি এবং স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির উসিলাও মনে করে। এর ভেতর দিয়ে তারা শুধু পারলৌকিক মুক্তিই খুঁজছে তা নয় বরং ইহলৌকিকভাবেও নিজেদের যে বিচ্ছিন্নতা—সেটাকে পেছনে ফেলে একটি আধ্যাত্মিক সংঘের অংশ হয়ে ওঠে।
মাজারে সবকিছুই ঘটে মূলত সেই পীরকে ঘিরে, যিনি শায়িত আছেন সেই মাজারেরই ছোটো কামরায়। কিন্তু নিজে না থেকেও, আধ্যাত্মিক শক্তিবলে অসংখ্য মানুষকে শত বছর ধরে এক করে রাখছেন তিনি। এই একতা একসময় সমাজ কাঠামোয় প্রভাবও বিস্তার করে। আর প্রভাবকে খর্ব করার জন্য এবং আধিপত্য নষ্ট করার জন্য বছরের পর বছর ধরে মাজার-দরগাকে ঘিরে নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। কিন্তু এরপরও সেগুলোর অস্তিত্বকে মুছে দেওয়া যায়নি। বরং যতবারই মাজারের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, ততবারই এটি আরও পরাক্রমশালী শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। এখন কেউ চাইলে একে মাজারে শায়িত ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির নিদর্শন হিসেবেও দেখতে পারে, আবার কেউ চাইলে একে মাজারপন্থী মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবেও দেখতে পারে। তবে এর বড়ো কারণ সম্ভবত শিকড়ের সঙ্গে যোগ। ভূমির সঙ্গে এবং ভূমির মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত থাকার কারণেই বছরের পর বছর ধরে টিকে আছে মাজার।
‘ব্যক্তি’র হৃদ মাজার
মাজার একদিকে যেমন সামাজিক কাঠামোর ভেতর বিকশিত হয়েছে, একইভাবে ব্যক্তির নিজস্ব যে সংকট সেটাও মাজারকে প্রাসঙ্গিক রেখেছে। সব বাদ দিয়ে আধুনিক মানুষের সংকটের কথাও যদি আমরা ভাবি, সেখানেও মাজারকে আমরা প্রাসঙ্গিক দেখতে পাব। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে মাজার-দরগা-পীর-ফকিরি তার পুরোনো প্রভাব হারিয়েছে। এর পেছনে মাজারবিরোধী ধর্মীয় গোষ্ঠীর যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি মাজারকে কুসংস্কার ভাবা প্রগতিশীল শিক্ষিত মানুষেরাও রয়েছেন। দুই পক্ষ ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচারণা চালিয়েছে বছরের পর, তাতে বিভিন্ন সময় মাজার এবং মাজারে যেসব খাদেম-ফকির-পাগল থাকে তারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুই মাজারকে বিলীন করতে পারেনি বা অস্তিত্ব মুছে দিতে পারেনি। মাজার বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং দাবি করেছে সমাজে নিজের ন্যায্য হিস্যা। মূলত ব্যক্তির অসহায়ত্ব এবং আশ্রয়-আকাঙ্ক্ষাও মাজারকে এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে এবং প্রাসঙ্গিক রেখেছে।
১৮ শত শতক থেকে বৈশ্বিক নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে ‘সেলফ’ বা ‘ব্যক্তি’র ধারণার বিবর্তন ঘটেছে। আমরা যদি সে সময়কার সাহিত্যিক ঘটনাগুলোর দিকে তাকাই, সেখানেও দেখব একই অবস্থা। ফিওদর দস্তয়েভস্কির লেখা ‘নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড’ বা ‘তল কুঠুরির কড়চা’কেই উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক। যার মধ্য দিয়ে আধুনিক সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী ধারণা তার নিজের অবস্থানকে তুলে ধরেছে।
১৮ শত শতক থেকে বৈশ্বিক নানা ঘটনার ভেতর দিয়ে ‘সেলফ’ বা ‘ব্যক্তি’র ধারণার বিবর্তন ঘটেছে। আমরা যদি সে সময়কার সাহিত্যিক ঘটনাগুলোর দিকে তাকাই, সেখানেও দেখব একই অবস্থা। ফিওদর দস্তয়েভস্কির লেখা ‘নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড’ বা ‘তল কুঠুরির কড়চা’কেই উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক। যার মধ্য দিয়ে আধুনিক সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী ধারণা তার নিজের অবস্থানকে তুলে ধরেছে। উনিশ শতকীয় মানুষ কেমন হতে যাচ্ছে, তার একটা ধারণাও এতে পাওয়া যায়। ব্যক্তির এই যে একা হয়ে পড়া, শূন্য অনুভব করা সেটা পাশ্চাত্যের পাশাপাশি প্রাচ্যকেও সমানভাবে আক্রান্ত করে। এ সময় মানুষ প্রচণ্ডভাবে আশ্রয়কামী হয়ে উঠতে থাকে। মানুষের সেই আশ্রয়কামীতার ভেতর দিয়েও মাজারগুলো জিন্দা থাকে। নয়তো আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা, কুসংস্কারবিরোধী ও যুক্তিবাদী ধারণাগুলোর ভেতরই মাজারগুলো হারিয়ে যেতে পারত।
যেমন আমরা দেখব সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর ‘লালসালু’ এবং ইবনে তাইমিয়া ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর মাজার বিরোধী জনপ্রিয় অবস্থান উদ্দেশ্যগতভাবে ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী হলেও শেষ পর্যন্ত একই বিন্দুতে এসে মিলে যাচ্ছে। ‘লালসালু’ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মাজারকে ব্যবসা ও লোক ঠকানোর কেন্দ্র হিসেবে আকার দেওয়ার চেষ্টা করে। ইবনে তাইমিয়া একই কাজ করছে শরিয়া ও ধর্মের দোহাই দিয়ে। আর আবদুল ওহাব তো তাইমিয়ার দর্শন বাস্তবায়নে রীতিমতো সংহারকের ভূমিকায় নেমেছিল। ফলে এসব মতবাদ দুই গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়ও হয়েছে বেশ। আবার এটাও ঠিক যে, এ সকল মাজারবিরোধী প্রকল্পকে আপনি হয়তো যুক্তি দিয়ে পুরোপুরি মোকাবিলাও করতে পারবেন না। যদিও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর একটা বড়ো অংশ পীর এবং মাজারের প্রাসঙ্গিকতার কথা সব সময় বলে গেছে। কোরআন-সুন্নাহর আলোকেই এসব আক্রমণের জবাব দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে ব্যক্তির মধ্যে এসব আলোকায়ন কিংবা পক্ষে-বিপক্ষের নানা যৌক্তিক আলাপ গিয়ে পৌঁছায়নি, সে কেন এত কিছু না জেনে বা না বুঝে মাজার ধারণায় আস্থা রাখছে বা কেন সে মাজারে যাচ্ছে?
মূলত ব্যক্তির আত্মার যে ক্ষুধা এবং নিজেকে খোঁজার যে প্রয়াস তা কোনো না কোনোভাবে মাজারগুলোর যে রুহ, তার ভেতর দিয়েও প্রবাহিত হয়েছে। এই সত্য মাজারকে প্রতিনিয়ত প্রাণবন্ত রেখেছে। ফলে মানুষের কাছে অনেক সময় মাজারে কেউ আদৌ আছেন কি না, তার চেয়েও বড়ো হয়েছে মাজারের স্রেফ থেকে যাওয়া। কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বললে মাজারের ধারণাটুকু। সেই আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে গিয়ে নিজেকে সঁপে দিতে পারাই একজন অস্থির এবং আত্মিকভাবে সব হারানো মানুষের আরাধ্য হয়েছে। পাশাপাশি এর মধ্য দিয়ে নিরাকার আল্লাহ এবং তার রাসুলের নৈকট্য পাওয়ার বাসনাও যুক্ত রয়েছে। আর এ কারণে অনেক নকল মাজারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে কিছু মাজার হয়তো নকল হতে পারে। কিন্তু যে মানুষটি সেখানে যাচ্ছে তার আবেগ মিথ্যা নয়। মিথ্যা নয় মাজারের সর্বজনীন স্পিরিটও।
মাজার যখন আশ্রয়
শুরুতে বলেছিলাম মাজার এক ধরনের আশ্রয়। বলেছিলাম, সেই আশ্রয়ের ধারণাকে বিস্তৃত করার কথাও। সেই বিস্তৃত ধারণাকে কেউ চাইলে আক্ষরিকভাবেও নিতে পারে। অর্থাৎ মাজারকে আক্ষরিক অর্থেই আমরা মানুষের আশ্রয় হয়ে উঠতে দেখি। এক সময় মসজিদগুলো মানুষকে আশ্রয় দিত। দূরের পথে যাত্রা করা কোনো অচেনা পথিককে বা কোনো ভবঘুরে ফকিরকে রাতে থাকতে দিত। কিন্তু ক্রমশ মসজিদগুলোকে কেবলই ইবাদতখানায় পরিণত করা হয়েছে। ফলে আশ্রয়কামী মানুষগুলোর জন্য থেকে গেছে কেবল মাজার-দরগা-খানকাগুলো। মাজারে কোনো ভেদাভেদ নেই। একজন পাগল, ফকির এবং একজন সুস্থ মানুষ এখানে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, পাগলকে সাধারণত মানুষ ভয় পেলেও মাজারে যেসব পাগল থাকে তাদের মানুষ ভয় পায় না। নিজের মাজার এলাকায় বড়ো হওয়ার কারণে এক সময় খুব ভাবতাম যে, মাজারে পাগলগুলো কেন আসে? কেন তারা থাকার জন্য মাজার এলাকাকেই বেছে নেয়। পরে উত্তরটা সহজেই মিলেছে। পাগলরা সব সময় নিজের জন্য একটা নিরাপদস্থলের সন্ধানে থাকে। সে এমন একটা জায়গা খোঁজে যেখানে তার অস্তিত্বকে কেউ হুমকিতে ফেলবে না, তার থাকাকে কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করবে না। যেখানে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না। মাজারে দুইবেলা খাবারের ব্যবস্থাও কেউ না কেউ তাকে করে দেবে। সে জন্যই কালে কালে পাগলদের আশ্রয় হয়ে উঠেছে এই মাজারগুলো। একই কথা ফকির বা ভবঘুরেদের জন্যও প্রযোজ্য। মাজার কর্তৃপক্ষ তো আছেনই, জেয়ারত করতে আসা মানুষেরাও সেই সব ছিন্নমূল মানুষের খাবারের বন্দোবস্ত করেন।
মাজারের অর্থ প্রবাহের ধারা
ধনীর অর্থে গরিবের ভাগ বসানো এটা কিন্তু মাজারের সচল অর্থনৈতিক প্রবাহকে চিহ্নিত করে। যদিও এর বাইরে মাজার সামগ্রিকভাবে বিশাল এক অর্থনৈতিক বন্দোবস্তও বটে। কোনো কোনো মাজার পরিচালিত হয় কমিউনিটি বা সামাজিক গোষ্ঠী দ্বারা। যেমন আনোয়ারার বটতলীর হজরত মোহছেন আউলিয়া (রঃ) মাজারের কথা আমি বলতে পারি। দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রাণ এই মাজার এবং চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড়ো মাজারগুলোর একটিও এটি। ১৯৬১ সালের ৯ মার্চ ২২ পরিবারের মাঝে ৩ জন মতোয়াল্লি ও ৬৪ খাদেম নিযুক্ত করা হয়। এখন এসে খাদেম সংখ্যা প্রায় ২০০ ছাড়িয়ে গেছে।
এই মাজার ঘিরে অসংখ্য দোকান, বাজার। আর রুস্তম হাটও মূলত এই মাজারের কারণে বিখ্যাত ছিল। মাজার দর্শনার্থীদের মানতের টাকাসহ নানা দান-খয়রাতের ওপর নির্ভর করে পরিচালিত হয় এই মাজারের যাবতীয় কার্যক্রম। মাজারের রক্ষণাবেক্ষণসহ নানা কিছুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এর মধ্য দিয়েই চালিত হয়। আগেই বলেছি মাজার ঘিরে যে বিশাল ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর বাস তাদের টিকে থাকার ব্যবস্থাও মাজারই করে থাকে। খাদেম গোষ্ঠীর বাইরে প্রায় পুরো অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোও কোনো না কোনোভাবে এই মাজারের ওপর নির্ভরশীল। ছোটো-বড়ো সব মাজারই কম বেশি এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা চালিত।
মাজারে মানত করাসহ নানা কিছুর কারণে ‘মাজার-ব্যবসা’ বলে একটা টার্ম বেশ প্রচলিত। অথচ কাউকে মাজারে আসতে বাধ্য করা হয় না। কেউ জোর করে কাউকে মাজারে আনে না। যে কেউ মাজারে স্বেচ্ছায় আসেন। যিনি মাজারে দান করছেন, তিনিও নিজের ইচ্ছায় করছেন। ফলে ‘মাজার ব্যবসা’ এটা মূলত এক ধরনের ফ্রেমিং। এগুলো মাজার বিষয়ক নেতিবাচক ধারণাকে শক্ত করতেই বলা হয়ে থাকে। এই অর্থনীতি যারা মাজার পরিচালনা করেন, তাদের যেমন অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা করছে, তেমনি পুরো অঞ্চলে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটা প্রাণচাঞ্চল্যও নিয়ে আসে।
বলে রাখা ভালো, সব মাজারের অর্থনৈতিক শক্তি একই রকম হয় না। এই ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চট্টগ্রামের লালদীঘি পাড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা পীর বদর শাহ ও হজরত আমানত শাহর কথা। ৫ মিনিটের দূরত্বে থাকা এই দুটি মাজারে জৌলুশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। পীর বদরের মাজারও আড়ম্বরহীন-সাদামাটা। অন্য দিকে আমানত শাহর মাজার তুলনামূলকভাবে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ।
বলে রাখা ভালো, সব মাজারের অর্থনৈতিক শক্তি একই রকম হয় না। এই ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চট্টগ্রামের লালদীঘি পাড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা পীর বদর শাহ ও হজরত আমানত শাহর কথা। ৫ মিনিটের দূরত্বে থাকা এই দুটি মাজারে জৌলুশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। পীর বদরের মাজারও আড়ম্বরহীন-সাদামাটা। অন্য দিকে আমানত শাহর মাজার তুলনামূলকভাবে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। আমানত শাহর মাজারে সারাক্ষণ লোকে লোকারণ্য থাকলেও পীর বদরের মাজার তা নয়। এর কারণ এই দুই মাজারের অনুসারীদের অর্থনৈতিক অবস্থান। পীর বদরের অনুসারী মূলত মাঝি-মাল্লা ও সমুদ্রগামী যাত্রীরা। অন্য দিকে আমানত শাহর মাজারে আসেন আদালতগামী মানুষেরা। যাদের সমস্যা অনেক বেশি বাস্তবমুখী। তাদের সমাধানও প্রয়োজন চটজলদি। ফলে আদালতে যারা নানা ঝুটঝামেলায় পড়ে আসেন, তাদের মানতের টাকা পয়সায় হৃষ্ট-পুষ্ট হয় এই মাজারটির অর্থনীতি। তবে সব মাজারেরই কম বেশি অনুসারী আছেন। তারাই মূলত বছরের পর বছর ধরে এই মাজারগুলোর অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।
অসহায়ের আর্তি
প্রশ্ন হচ্ছে কারা আসেন এই সব মাজারে? চট্টগ্রামে পীর বদর-গরম বিবিসহ অনেক মাজারের দেয়ালে নানা ধরনের আরজি লেখা আছে। কেউ পরীক্ষা পাসের জন্য, কেউ বিয়ের জন্য, কেউ ঘরের শান্তির জন্য, কেউ স্বামীর মন পাওয়ার জন্য পীরের মারফতে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন। এক কথায় বছরের পর বছর ধরে নানা শ্রেণি-পেশার দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলোই মাজারে আসেন। উচ্চবিত্ত শ্রেণির অনেক প্রতিবন্ধী সন্তানের বাবা-মারা প্রিয় ছেলে বা মেয়ের আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে মাজারে আসেন। এমন না যে তারা নিজেরা প্রার্থনা করেন না। কিন্তু আল্লাহর অলি-আউলিয়াদের মাধ্যমে নিজেদের বিশেষ দাবিগুলো আল্লাহর দরবারে তারা পেশ করেন। তাদের ধারণা, হয়তো প্রিয় বান্দাদের অছিলায় চাইলে আল্লাহ একটু তাড়াতাড়িই তাদের দাবিগুলো পূরণ করবেন কিংবা ঘটে যেতে পারে অলৌকিক কিছুও। এটাও শুরুতে যে আশ্রয়ের কথা বলছিলাম, সেই আশ্রয়েরই অংশ।
এটাকে আবার মানুষের আত্মিক মুক্তির পাশাপাশি বৈষয়িক চাহিদা পূরণের বাসনা আকারেও পাঠ করা যায়। মানুষের এই যে মাজারগুলোর ওপর বিশ্বাস, মাজারে শুয়ে থাকা পীর বা সুফি মানুষটির ওপর বিশ্বাস, এটাই মূলত মানুষের ফিতরত বা বৈশিষ্ট্য। মানুষ মূলত কিছু না কিছুর ওপর বিশ্বাস করে, কিছু না কিছুর ওপর বিশ্বাস করে তাকে টিকে থাকতে হয়। বিশেষ করে যখন সে কোণঠাসা অবস্থায় থাকে তখন তাকে কারও না কারও আশ্রয় চাইতে হয়। কিন্তু অনেক সময় চাওয়ার জন্য নিজেকে তার ক্ষুদ্র মনে হয়। তখন নিজের চেয়ে বড়ো সত্তার দ্বারস্থ হতে হয় তাকে।
ওরস মানেই উৎসব
মাজার যে আবার সব সময় আশ্রয়প্রার্থী মানুষের পদভারে নুয়ে পড়ে তাও নয়। মানুষ মাজারে নানা সমস্যা ও দেন-দরবার নিয়ে আসে তা ঠিক, কিন্তু কেবল মানসিক ও আত্মিক শান্তির জন্যও অনেকে মাজারে এসে থাকেন। আর এই মানুষগুলোই এক সময় এসে এই মাজারেরই একজন হয়ে ওঠেন। অংশ হয়ে ওঠেন মাজারের যাবতীয় কার্যক্রম, অনুষ্ঠান ও উৎসবের। আর মাজারের সবচেয়ে বড়ো উৎসব হচ্ছে ওরস। যে পীর বা সুফির কবরকে ঘিরে মাজার গড়ে ওঠে সেই মাজার প্রাঙ্গণে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করাই মূলত ওরস। এই ওরস প্রায় সব মাজারেই বেশ জাঁকঝমকভাবে পালন করা হয়। সেদিন হাজার হাজার মানুষ ওরসে অংশ নিতে মাজার এলাকায় আসেন। যারা দূরের তারা আগেই চলে আসেন। কিন্তু ওরসের দিন সকাল থেকে মাজারে মানুষের ঢল নামে। এলাকাভিত্তিকভাবে গাড়ি নিয়ে আসেন অনেকে। তবে মাজার প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বেশির ভাগ সময় গাড়ি আনার সুযোগ থাকে না। ফলে পায়ে হেঁটেই আসতে হয় সবাইকে। মোহছেন আউলিয়ার ওরসের সময় দেখেছি, অনেকে মাজার পর্যন্ত আসতেই পারেন না। রাস্তাতেই ওরস পালন করেন। ওরস পালন বলতে নিজেরা চাঁদা তুলে গরু, মহিষ, ছাগল কেনেন। ফাতেহার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে সেগুলো কোরবানি দিয়ে নিজেরা রান্না করে খাওয়া দাওয়া করেন, ফকির-মিসকিন-গরিব মানুষদের খাওয়ান। দলে দলে ভাগ হয়ে এসব আয়োজন চলতে থাকে। আবার অনেকে মানত করা জিনিসপত্র খাদেমের হাতে দেন। খাদেমরাই এসব রান্না করে তবারক হিসেবে খাওয়ান, প্যাকেটে করে দিয়ে দেন। ওরস উপলক্ষ্যে মাজারকে নতুন করে সাজানো হয়। মাজার ঘিরে প্রার্থনার নানা আয়োজন থাকে। হাজার হাজার ভক্ত সেসবে অংশ নেন। অনেক মাজারে সুফিবাদী ও ভক্তিমূলক গানবাজনার আয়োজনও থাকে।
ব্যক্তিগতভাবে এবং গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এসব অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওরসকে ঘিরে গড়ে উঠে ভ্রাম্যমাণ মেলা। মাজার এলাকায় বসে অস্থায়ী দোকানপাট। দূর-দূরান্ত থেকে শুধু ওরস উপলক্ষ্যে ব্যবসা করতে আসেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। অনেকে আছেন যারা শুধু ওরস কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। অল্প সময়ের এই ব্যবসা বেশ লাভজনকও। ওরস কেন্দ্রিক মেলায় নানা অঞ্চলের ঐতিহ্য বহন করা লোকজ পণ্যের সমাগম ঘটে। ফলে ওরস শুধু ধর্মীয় সম্মেলনে আটকে থাকে না। এটি গ্রামীণ বা প্রান্তিক ব্যবসায়িক সম্মেলন আকারেও সামনে আসে। তবে সবকিছুর কৃতিত্ব শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয় সেই মাজারে শায়িত আল্লাহ অলিকে। তার অছিলাতেই যে মাজারকে ঘিরে, ওরসকে ঘিরে এত রহমত আর বরকত! অনেক ওরসে গানবাজনার আসর বসে। ভক্তি আর প্রেমের গানের ভেতর ভক্তরা নিজেদের উজাড় করে দেন। এটা এক ধরনের তূরীয় অনুভূতি। খুব কম কিছুর সঙ্গেই এর তুলনা চলে। শৈশবে যখন ওরসে যেতাম, তখন মোটাদাগে বিষয়গুলো এমনই ছিল।
মাজারের গান
মাজারের গান অনেক বছর ধরে আলাদা একটা ধারাই তৈরি করে ফেলেছে। মাজারে শায়িত পীর-আউলিয়ার গুণ ও নানা কারামতকে প্রাধান্য দিয়ে তৈরি করা হয় এসব গান। পাশাপাশি নিজেদের ভালোবাসা ও ভক্তির কথাও এ গানগুলোর কথায় উল্লেখ থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সুফিবাদের বিকাশের সঙ্গে গানের জড়িয়ে থাকার ইতিহাসটা আরও পুরোনো। বিশেষত উপমহাদেশে গজল ও কাওয়ালির বিকাশই ঘটেছে মাজারকে ঘিরে। আমির খসরুর হাত ধরেই মূলত গজল চূড়া স্পর্শ করে। খসরু ছিলেন চিশতী পীর নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার ভক্ত। নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে নিয়ে অনেক গজল তিনি রচনা করেছেন।

কবিয়াল রমেশ শীল সমাধি সৌধ
পাশাপাশি এখানে সামার কথাও আলাদাভাবে বলতে হয়। যেখানে একান্তে ভক্তরা সুফি গান গেয়ে থাকেন। এই গানের সঙ্গে অনেকে বাদ্য বাজনা ব্যবহার করেন, অনেকে আবার করেন না। এর সঙ্গে থাকে সুফি কবিতা পাঠের আয়োজনও। সুফি নৃত্য রাকসের কথাও এখানে বলতে হয়। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়।
মাজার কেন্দ্রিক সামা, গজল ও কাওয়ালির চর্চা আমাদের এখানেও আছে। তবে এর বাইরেও আমাদের এখানে এসে মাজারের গানের আলাদা একটা স্কুল গড়ে উঠেছে। যা একান্তই আমাদের। মাজার নিয়ে গানগুলো অন্য লোকগান ও বাউল গানের চেয়ে খানিকটা আলাদা। গানের কথা ও সুরেই এটা ধরা যায়।
সব মিলিয়েই মাজারের গান এখন লোকজ সংস্কৃতির গৌরবময় অংশ। মাজারকে ঘিরে অসংখ্য লোক-গায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। কবিয়াল রমেশ শীল তো মাইজভাণ্ডারকে উদ্দেশ্য করে গান রচনা করে (যা ভাণ্ডারি গান নামে পরিচিত) রীতিমতো কিংবদন্তি হয়ে গেছেন। তাঁর একটি গানের কিছু কথা এমন—
“আমার গাউসুল আজম কেবলা বাবা কোথায় লুকালে,
তোমার আদরের সব ছেলে মেয়ে এতিম বানালে।।
করতে কত মেহেরবানি দিতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অন্ন-পানি ।
কে আর করিবে দয়া এ ভূমণ্ডলে।।”
তবে রমেশ শীলের লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত গানগুলোর অন্যতম নিচের গানটি।
গাউসুল আজম বাবা নুরে আলম,
তুমি ইছমে আজম জগতে তরানেওয়ালা।
নাম ধরেছ ভবে হক ভাণ্ডারী
বাবা তৌহিদের কাণ্ডারী নূরী মাওলা,
তোমার নূরে তজাল্লিতে পাহাড় জ্বলে
মুছা মচ্ছাগত দেথে নূর উজালা।
হুর ফেরেশতা পড়ি রবি শশী
দিবানিশি রহম মাগে হয়ে উথলা।
তব পদ সরোজ মকরন্দ আসে,
রমেশ ভৃঙ্গ বেশে কাটাই সারা বেলা।
এই গানের কথা যে সব বুঝতাম তা না, কিন্তু এসব গান প্রচুর গাওয়া হতো। বিশেষ করে ছুটিতে গ্রামে গেলে এসব গান অনেক বেশি শোনা হতো। মাইজভাণ্ডারী দরবারের উদ্দেশ্যে এমন অসংখ্য গান লেখা হয়েছে। রমেশ শীল ছাড়াও অনেকেই এসব গান লিখেছেন। মাইজভাণ্ডার নিয়ে যারা গান লিখেছেন তাদের মধ্যে সৈয়দ আব্দুল হাদি কাঞ্চনপুরি, সৈয়দ আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরি, মাওলানা আব্দুল্লাহ বাঞ্চারামপুরিসহ কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোহছেন আউলিয়ার ক্ষেত্রে আমরা শৈশবে শিমুল শীলের লেখা অনেক ভক্তি গান শুনেছি। মোহছেন আউলিয়া নিয়ে লিখেছেন চট্টগ্রামের লোকগানের কিংবদন্তি গফুর হালীও।
তার লেখার অসাধারণ কটি চরণ এমন—
‘চলরে জিয়ারতে আউলিয়ার দরবার/
মোহছেন আউলিয়া বাবার বটতলী মাজার’
এসব গানের বোল ভক্তদের মুখে মুখে থাকে। বিশেষ দিনে এই গানের আসর বসে। মানুষ পীরকে স্মরণ করে নিজেদের বিলীন করে দেন। মাজারের গানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে রূপক এবং উপমার ব্যবহার। এসব গানে প্রচুর রূপকের ব্যবহার করা হয়। যদিও গানের সুর বিন্যাস ও আয়োজনের কারণে ভক্তদের সেসবের গূঢ় অর্থ না জানলেও তাতে মজে যেতে খুব একটা সমস্যা হয় না।
আর মাজারের এই গানগুলো যে শুধু মাজারে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। মাজারের বাইরেও গ্রাম অঞ্চলের চায়ের দোকান, মফস্বলের বাসাবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এসব গান। মাজার ভক্তদের অনেককে দেখতাম সারা দিন রাত শুধু এসব ভক্তি গান শুনছেন। এসব গান শোনা যায় যানবাহনেও। বিশেষ করে দূরপাল্লার বাসে এক সময় প্রায় শোনা যেত এই গানগুলো।
আর মাজারের এই গানগুলো যে শুধু মাজারে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। মাজারের বাইরেও গ্রাম অঞ্চলের চায়ের দোকান, মফস্বলের বাসাবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এসব গান। মাজার ভক্তদের অনেককে দেখতাম সারা দিন রাত শুধু এসব ভক্তি গান শুনছেন। এসব গান শোনা যায় যানবাহনেও। বিশেষ করে দূরপাল্লার বাসে এক সময় প্রায় শোনা যেত এই গানগুলো। একটানা এই গান শুনতে শুনতে মন নরম হয়ে আসে। কোথাও একটা জায়গা যেন শূন্য হয়ে পড়ে। মনে হয় কেউ একজন ডাকছে। সে ডাকে সাড়া দিতে হবে আমাকেও।
সম্প্রীতির মাজার
মাজার আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির সবচেয়ে বড়ো চিহ্ন। এখানে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মগুলোর বোঝা পড়া তৈরি হয়েছে মাজারকে ঘিরে। বর্তমানে সালাফি ও খারেজিবাদের যে উত্থান তা দিয়ে কখনো মাজারকে বোঝা যাবে না। মাজারকে মাজারের ভেতর প্রবেশ করেই বুঝতে হবে। মাজারকে বুঝতে হবে তার বিশাল হৃদয় দিয়ে। কথিত আছে শুধু মাত্র গরীবে নেওয়াজ হজরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (র.) এর হাত ধরেই শুধু ৯০ লাখ মানুষ মুসলমান হয়েছে। এমন না যে, অনেক অর্থকড়ি বা সম্পদের লোভে মানুষগুলো ধর্মান্তরিত হয়েছে। আবার এমনও না যে, সবাইকে জোর করে ধরে মুসলমান বানানো হয়েছে। মাজারের উদার আহ্বানেই মূলত এই কাজটা হয়েছিল।
মাজারে শুধু মুসলমানরা যেতে পারে এমন নয়। সকল ধর্মের মানুষের মাজারে সমান প্রবেশাধিকার আছে। যে কেউ চাইলে বিনা বাধায় অলির রওজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, একজন হিন্দু বা বৌদ্ধ যে কিনা ইসলামে বিশ্বাস করে না, সে নিজের ধর্ম না বদলিয়েই কীভাবে মাজারে আসতে পারছে? কীভাবে ধর্মীয় ভেদের ঊর্ধ্বে উঠে পীরের দরগায় হাজিরা দিতে পারছে? এই বিষয়টি সত্যিই ব্যাপকভাবে আগ্রহ জাগানোর মতো। আজ একুটুই। বাকিটুকু পরের পর্বে।
পাঠ করুন: মাজার যে ভাষায় কথা বলে : পর্ব ১

কবি ও কথাসাহিত্যিক
জন্ম ১৯৮৮, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর। প্রকাশিত বই : সূর্যাস্তগামী মাছ (কবিতা) ব্রায়ান অ্যাডামস ও মারমেইড বিষ্যুদবার (কবিতা) শেফালি কি জানে (না কবিতা, না গল্প, না উপন্যাস) ক্ল্যাপস ক্ল্যাপস (কবিতা) দ্য রেইনি সিজন (কবিতা) প্রিয় দাঁত ব্যথা (কবিতা) বিষাদের মা কান্তারা (উপন্যাস) সন্তান প্রসবকালীন গান (কবিতা)