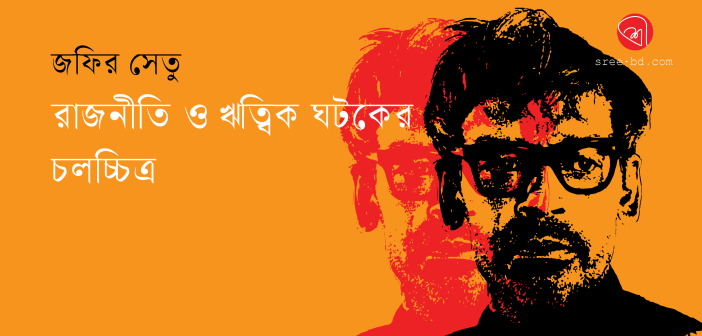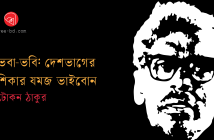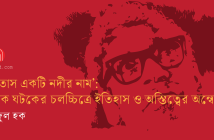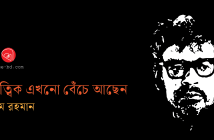ব্যক্তিজীবনে দেশভাগের মতো প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার এবং শিল্পের ব্যাপারে বের্টোল্ড ব্রেশ্টের পিপলস্ আর্টের চিন্তাধারা ও সের্গেই আইজেনস্টাইনের ভাষাবোধ যাঁর মনন পুষ্ট করেছিল তাঁর পক্ষে জীবনকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা আদৌ কি সম্ভব? কথাটা হচ্ছে ঋত্বিককুমার ঘটককে নিয়ে। একে তো তিনি ছিলেন মার্কসবাদী, তার ওপর আবার গণনাট্য সংঘ ও প্রগতি লেখক সংঘের সক্রিয় কর্মী; তাই সময় ও জীবনকে তিনি দেখেছিলেন স্বদেশ-বিদেশের বাস্তবতার কষ্টিপাথরে। ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র, বেড়ে উঠেছেন সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার পারিবারিক আবহে। পড়েছেন দেশবিদেশের ক্লাসিক সব সাহিত্য, যুবক বয়সেই হয়ে ওঠেন রাজনীতি-দর্শন-ধর্মতত্ত্ব-সংগীত-মিথপুরাণে ব্যুৎপন্ন; আর শিল্প ও সিনেমার নানা তত্ত্বে নিজেকে মাতিয়েই রাখতেন না নিজেকে, উজ্জীবিত হতেন প্রতিনিয়ত। সেই ঋত্বিক কবিতা-গল্প-নাটক লেখা এবং নাটক নির্মাণের পর এলেন ফিল্মের জগতে। এই শিল্পচর্চার জগতে আসা নিছক খেয়ালের বশে নয়, একটা অভিপ্রায় নিয়ে। বলা ভালো ঋত্বিক ঘটকের শিল্পের জগতে আসাটা একটা কমিটমেন্ট নিয়ে, আর সেইটে খুব গুরুত্বপূর্ণ।
ব্যক্তিজীবনে দেশভাগের মতো প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার এবং শিল্পের ব্যাপারে বের্টোল্ড ব্রেশ্টের পিপলস্ আর্টের চিন্তাধারা ও সের্গেই আইজেনস্টাইনের ভাষাবোধ যাঁর মনন পুষ্ট করেছিল তাঁর পক্ষে জীবনকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা আদৌ কি সম্ভব? কথাটা হচ্ছে ঋত্বিককুমার ঘটককে নিয়ে। একে তো তিনি ছিলেন মার্কসবাদী, তার ওপর আবার গণনাট্য সংঘ ও প্রগতি লেখক সংঘের সক্রিয় কর্মী; তাই সময় ও জীবনকে তিনি দেখেছিলেন স্বদেশ-বিদেশের বাস্তবতার কষ্টিপাথরে। ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র, বেড়ে উঠেছেন সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার পারিবারিক আবহে। পড়েছেন দেশবিদেশের ক্লাসিক সব সাহিত্য, যুবক বয়সেই হয়ে ওঠেন রাজনীতি-দর্শন-ধর্মতত্ত্ব-সংগীত-মিথপুরাণে ব্যুৎপন্ন; আর শিল্প ও সিনেমার নানা তত্ত্বে নিজেকে মাতিয়েই রাখতেন না নিজেকে, উজ্জীবিত হতেন প্রতিনিয়ত। সেই ঋত্বিক কবিতা-গল্প-নাটক লেখা এবং নাটক নির্মাণের পর এলেন ফিল্মের জগতে। এই শিল্পচর্চার জগতে আসা নিছক খেয়ালের বশে নয়, একটা অভিপ্রায় নিয়ে। বলা ভালো ঋত্বিক ঘটকের শিল্পের জগতে আসাটা একটা কমিটমেন্ট নিয়ে, আর সেইটে খুব গুরুত্বপূর্ণ।
ঋত্বিক ঘটকের শিল্পসৃষ্টির কমিটমেন্টটা তাহলে কী? ‘শিল্প, ছবি ও ভবিষ্যৎ’ প্রবন্ধে তিনি নিজেই এই কমিটমেন্টের কথা লিখেছেন এভাবে, ‘লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যোদ্ধা কাউকে ক্ষমা করে না। এখানেই তবে প্রশ্ন তুলছি: শিল্পী কমিটেড কি না, শিল্পী কোথাও বাঁধা আছেন কি না? কমিডেট কথাটার মানে কী? নিজেকে কোথাও সংলগ্ন করে রাখা। শিল্পীর জীবনেও তাই। তাকে কোথাও না কোথাও লাগতে হবে।… যদি না পারেন, তবে বাইরের একটা বস্তু খুঁজতে হবে, সেটা কী? মানুষ। শিশু। জীবন মৃত্যুকে অস্বীকার করে। সকল শিল্পকে তাই হতে হবে জীবন অনুগামী। জন্মই জীবন। শিল্পজীবন। এই কথাটা আমরা কখনো ভুলে না যাই। যত ক্লেদাক্ত, বিষাক্ত অভিশাপের ভেতর দিয়ে আমাদের বেরুতে হবে, হবে। শিল্প আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে।’ শুধু তাই নয় শিল্পসৃষ্টির বিষয়ে ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথের একটি কথাকে বেদবাক্যের মতো মানতেন। কথাটি এই, ‘প্রত্যেক শিল্প একমাত্র সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। শুধুমাত্র সত্য দ্বারা শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয় একথা সত্যি, কিন্তু সত্য ব্যতীত শিল্প সম্পূর্ণ হয় না।’ এই কথাটির প্রতিধ্বনি তাঁর ‘চলচ্চিত্রের স্বরূপ কী’ প্রবন্ধেও দেখতে পাই, ‘নিরালম্ব বায়ুভূত শিল্প কখনো শিল্পের পর্যায়ে ওঠে না। মানুষটিকে কোথাও না কোথাও আত্মীকরণ করতে হয়। ভালো না বাসলে শিল্প জন্মায় না। এর প্রকাশভঙ্গি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, শিল্পীর মেজাজের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু মূলসূত্র সেই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম।… সত্যসিদ্ধ না হলে কোনো শিল্পই শিল্পের পর্যায়ে ওঠে না।’ শিবম্কে তিনি সেই শাশ্বত বলে চিহ্নিত করেন যা মানুষ দুঃখ দিয়ে অর্জন করে; সেই জিনিসগুলো যা মানুষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে খুঁজে পায়। আর সুন্দরকে ঋত্বিক চিহ্নিত করেন সেই সত্তা হিসেবে যা সত্য ও শিবকে স্বীকার করে গড়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় ঋত্বিকের কাছে সত্য কী? ঋত্বিক স্পষ্ট করে বলেন না কিছু, কিন্তু তাঁর কর্ম ও চিন্তা থেকে এটুকু আমরা বুঝতে পারি যা কিছু নিয়ে মানুষ ও মানুষের জীবন তাই ঋত্বিকের সত্য। সুতরাং তাঁর শিল্পের সত্যও তাই। মানুষকে ছাড়া যেমন সত্য হয় না, শিল্পও মানুষ ছাড়া হয় না।
এই মানুষের জীবনটা কী? জীবন হচ্ছে টিকে থাকার লড়াই-সংকট, দ্বন্দ্ব আর সংগ্রামে ভরপুর। আর আধুনিক মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র, আবার রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতি। সুতরাং রাজনীতি ছাড়া জীবন নেই।
এই মানুষের জীবনটা কী? জীবন হচ্ছে টিকে থাকার লড়াই-সংকট, দ্বন্দ্ব আর সংগ্রামে ভরপুর। আর আধুনিক মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র, আবার রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতি। সুতরাং রাজনীতি ছাড়া জীবন নেই। আপাত যেখানে রাজনীতি নেই বলে মনে হয় সেখানেও রাজনীতির বড়ো খেলা নিহিত থাকে। ঋত্বিক তরুণ বয়স থেকে এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর পেরেছিলেন বলে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যে-সময়টাকে ঋত্বিক রাজনীতিতে সক্রিয় হন ১৯৪৪-৪৫ সালে তাঁর বয়স মোটে উনিশ-কুড়ি, সময়টাও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পটপরিবর্তনের কাল। জাতীয় ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন, জাপানের আক্রমণ, ব্রিটিশদের পলায়ন, দুর্ভিক্ষ, হিন্দু-মুসলমান সংকট, পাকিস্তান আন্দোলনসহ পরপর নানা ধরনের পটপরিবর্তনের ঘটনা ঋত্বিককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে তিনি বেছে নেন মার্কসবাদকে, যদিও ঋত্বিকের রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল মার্কসবাদ ও আদর্শবাদের একটা বিশেষ মিশ্রণ। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য তিনি মার্কসবাদকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন কিন্তু মানুষের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিশ্বাস করতেন। এও মনে করতেন যে মানুষের সব নিজস্বতাকে মার্কসবাদ দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়।
ঋত্বিকের বয়স যখন আঠারো সেই ১৯৪৩ সালে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ গঠিত হয়; যদিও লক্ষ ছিল দেশের সাংস্কৃতিক মুক্তিচেতনা আদপে এর কাজ ছিল রাজনৈতিক। এই সংঘ গণমানুষের ব্যথা-বেদনা-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করে। জনগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনই এর উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে সংঘ তার সকল শিল্পকর্মকে নিয়োজিত করে। জনগণই ছিল গণনাট্য সংঘের নায়ক। এর মূলনীতিতে বলা হয়েছিল ‘গণনাট্য সংঘ আশা করে দেশের সাংস্কৃতিক রূপকে বদলাইয়া সে এমন এক ভারতবর্ষের জন্ম দিবে যেখানে মানুষ হইবে স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধ; সংস্কৃতি ভারতের সর্বমানবের সম্পত্তি হইবে। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছোটো ব্যাবসাদার প্রভৃতিদের দ্বারাই আজ দেশের অগণন জনতা সংগঠিত। ইহারাই দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক অংশ। ইহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেসব অতীতমুখী ও বিজাতীয় ভাবধারা কাজ করিতেছে এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইহাদের পরিপন্থি হইতেছে—গণনাট্য সংঘের শত্রু তাহারাই। সে জানে দেশের বেশিরভাগ মানুষ তাহার কাজের সহায়।’ গণনাট্য সংঘের কর্মকাণ্ড তরুণ ঋত্বিককে খুব প্রভাবিত করল, আর গঠনের পরের বছরই তিনি তাতে যোগ দেন, আর ১৯৪৮ সালে সংগঠনের সেক্রেটারিও মনোনীত হোন। সুতরাং সূচনা থেকেই ঋত্বিক ছিলেন গণমুখী ও মুক্তিকামী সুতরাং সাহিত্যেও আসলেন ওই মন নিয়ে।
এরই মধ্যে ভারত-রাজনীতিতে বড়ো ঘটনা ঘটে। একদিকে উপনিবেশকে সর্বস্বান্ত করে শাসকগোষ্ঠীর পলায়ন, অন্যদিকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক যে-ঘটনা ঘটল তা দেশভাগ ও দাঙ্গা। বাংলাও ভাগ হলো, লক্ষ লক্ষ বাঙালি স্বদেশভূমি থেকে হলো উৎখাত; হাজার হাজার মানুষকে ভিন রাষ্ট্রে হতে হলো শরণার্থী। ১৯৪৮ সালে ঋত্বিকরাও বাংলাদেশ পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় ঠাঁইনাড়া হলেন। এই ক্ষত ঋত্বিকের মৃত্যুঅবধি যায়নি, বরং দেশভাগের দুঃসহতা তাঁকে সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। শারণার্থী, বাস্তুহারা এসব শব্দ তিনি নিতেও পারতেন না। অপরদিকে স্বাধীনতার পর দেখলেন ঋত্বিক অপর এক বাস্তব; শাসকশ্রেণির লুটতরাজ, দায়-দায়িত্বহীনতা, প্রতারণা ও ফাঁকাবুলি। চোখের সামনে দেখতে পেলেন উদ্বাস্তুজীবনের ট্র্যাজেডি, আর মধ্যবিত্তশ্রেণির অবক্ষয় ও পতন। এসব ঋত্বিককে সংক্ষুব্ধ করে তুলেছিল তাই কবিতা দিয়ে শুরু হলেও পরে গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। নিজের কথায়, ‘গল্প লেখার আর্জটা কিন্তু সেই কবিতা লেখার মতো ভুয়ো, ধোঁয়াটে ব্যাপার ছিল না। চারপাশে যে-সমস্ত খারাপ বদমায়েশি, অত্যাচার ইত্যাদি দেখছি, তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জীব হিসেবে সোচ্চার প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থেকেই গল্প লেখার আর্জ এসেছিল।’ কেননা শিল্পী হিসেবে ঋত্বিকের ইনভলভমেন্ট-এ বিশ্বাস ছিল যে চারপাশের মানুষের জীবনের সঙ্গে নাড়ির যোগ রেখে শিল্প করতে হয়। তাঁর মতে এমনকি প্রত্যেক সৎ শিল্পীকে সমাজের অংশীদার হতে হবে, লক্ষ মানুষের জীবনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সংগ্রামের অংশীদার হতে হবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে, দিকে দিকে প্রসারিত আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে কোনো শিল্পীর দ্বারা ভালো শিল্প বা ছবি করা সম্ভব হবে না। সেই প্রয়োজনে যদি রাজনীতি সম্পর্কিত হয়ে যায় তাতেও অসুবিধা নেই। কারণ শুধু শিল্পী নয়, সমাজে প্রত্যেক মানুষকে রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। বরং রাজনীতির ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে দুটো দল আছে একদল কমিটেড আর অপরদল নন-কমিটেড। ঋত্বিকের ভাষায়, ‘কেউই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন না।… এরা রাজনীতিতে একটা পক্ষ নিয়ে বসে আছেন, সেটার পোজ হচ্ছে…I am not commited. One cannot be non-commited. You are either for this or for that. কাজেই এরা কেউ বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন না, এরা মানুষের সর্বনাশ করার চেষ্টা করছেন।’ আর শিল্পীদের যেহেতু অতিরিক্ত সামাজিক দায় আছে, তারা যদি সেটা অবহেলা করেন ঋত্বিকের সে-ব্যাপারেও কঠিন মত হচ্ছে, ‘সামাজিক দায়িত্ব যারা অ্যাভোয়েড করে তারাও সামাজিক দায়িত্বই পালন করছে। অর্থাৎ তারা ওপরতলার শুয়োরের বাচ্চাদের সাহায্য করছে। সামাজিক দায়িত্ব প্রত্যেকেই পালন করছে।’ সুতরাং তাঁর সাফ কথা শিল্পীদের প্রথম ও শেষ দায়িত্ব মানুষের সেবা করা, মানুষের জন্য কথা বলা; তবে সেটা শিল্পসম্মতভাবে হতে হবে। কারণ রাজনীতিকের কাজ ও শিল্পীর কাজ একরকম নয়: ‘তবে তাই বলে স্লোগান মঙ্গারিং শিল্পীর কাজ না। এই “ক্লিপ স্লোগান” দিয়ে শিল্পী হয় না, শিল্পীকে কাজ করতে হয় মানুষের গভীরে। রাজনীতিকরা কাজ করে ওপরতলায়, মানে চেঁচামেচি, হট্টগোল, ক্লিপ স্লোগান একটা শর্ট স্লোগান, এইসব। শিল্পী এইগুলো করলে, আমি মনে করি, সেটা আর শিল্প থাকে না।’
দেশ স্বাধীন ও ভাগের পর দেশের সার্বিক অবস্থাকে ঋত্বিক ঘটক ‘গ্রেট বিট্রেয়াল’ বলে অভিহিত করেছেন বারবার। স্বাধীনতাকে তিনি ‘তথাকথিত স্বাধীনতা’ বলেই আখ্যায়িত করেছেন, আর সময়টাকে নির্ধারণ করেছেন নিও-কলোনিয়ালিজম নামে। কারণ উপনিবেশকদের ফেলে যাওয়া আমলাতন্ত্র ও ভণ্ড রাজনীতিবিদদের আখের গোছানো কর্মকাণ্ডে দেশটার প্রাণ মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল। আত্মজবানিতে সময়টা এভাবে ধরা পড়ে যে, ‘সমস্যাটা কোথায়, এভরিবডি নোওজ। সমাজে সেই উচ্চস্তর থেকে নিম্নতম পর্যন্ত আমি মিশি, আমি মিশছি—প্রত্যেকে জানে। একদল আছে এই অবস্থা থেকে ক্ষীর লুটছে, ননী লুটছে, সব লুটছে—কাজেই এই অবস্থাটা তারা perpetuate করতে চায়। আর একদল ঘুরছে কতকগুলো নেতার পেছনে—যেগুলো প্রত্যেকটা চোর, প্রত্যেকে তাদের নাম বজায় রাখা, পয়সা করা ইত্যাদিতে ব্যস্ত। এরা এইসব লোকের দ্বারা বিভ্রান্ত। এই হলো অবস্থা, কিন্তু কারও কাছে কোনো কিছু লুকানো নেই। জিনিসটা অত্যন্ত প্রকট, সূর্যের আলোর মতো প্রকট। এই যে ছেলেপুলেগুলো বখে যাচ্ছে, রাস্তায় বেরুলে দেখি আজকালকার ছেলেপুলেরা যে-ধরনের বিহেভিয়ার করে তা বলা যায় না, এ-সমস্তই হচ্ছে ফ্রাস্টেশন-এর ফলে।’ ঋত্বিক দেখেছেন ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের জার্মানিতে যেসব কাণ্ড ঘটেছিল তখনকার ভারত-পরিস্থিতি সেদিকেই যাচ্ছিল; জার্মানির ‘গেস্টাপো’ আর এখানকার ‘এসএস’ একই চরিত্রের দুই রূপ। গোটা সমাজব্যবস্থাটাকেই ভেঙে পড়তে দেখেছেন তিনি। একটা ফ্যাসিস্ট চেহারা নিচ্ছিল ভারত। এই অবস্থায় উপায়ও খুঁজছিলেন ঋত্বিক, ‘এখন আমার নিজের ধারণা দুটো রাস্তা পরিষ্কার—দুটো পথ খোলা—হয় লিনিনিস্ট-পদ্ধতিতে নিয়ে যাবার একটা ব্যাপার আছে, নইলে ফ্যাসিজম হবে।’
এই অবস্থায় ঋত্বিক ঘটকের নিজের কাজ কী? নিজেকে শানিয়ে নিচ্ছিলেন আর উপায় খুঁজছিলেন একজন শিল্পী হিসেবে নিজের দায়িত্বটা পালন করার। কবিতার পর এলেন গল্পে, দেখলেন এধরনের শিল্পাঙ্গিক মানুষকে সোজাসুজি প্রভাবিত করে না। এ-সময় স্টেজে এলো বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’, নতুন ধারার নাটক। ‘নবান্ন’ই বলতে গেলে ঋত্বিকের জীবনধারা পালটে দিল। ‘চারপাশের বদমাইশির বিরুদ্ধে অনেক চিৎকার আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। তখন ভাবলাম নাটকের মাধ্যমে মানুষের সামনে ঘটনাগুলি সোজাসুজি পৌঁছে দেওয়া যাবে। …আমার তখন টগবগে রক্ত, ইমিডিয়েট রিয়্যাকশন চাই।… সেই জন্য গেলাম নাটক করতে—স্টেজে। সামনে এক হাজার, দুহাজার লোক পাব, তাদের খেপিয়ে তুলতে পারব। ইমিডিয়েট রিয়্যাকশন হবে।… তারপর আমি পুরোপুরি গণনাট্যে ছিলাম। সেন্ট্রাল স্কোয়াড-এ লিডার-ও ছিলাম, নাট্যকার হিসেবে তখন নাটকও লিখেছি। নাটক ইমিডিয়েট রিয়্যাকশন তৈরি করে বলে দারুণ লাগছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে সেটাও মনে হলো ইনঅ্যাডিকেট, মনে হলো এটাও সীমিত। ব্যাপারটা হচ্ছে চার-পাঁচ হাজার লোক, আমরা যখন মাঠে-ময়দানে কাজ করতাম চার-পাঁচ হাজার লোক জমা হতো, নাটক করে তাদের সঙ্গে করা rouse করা যেত। তখন মনে হলো সিনেমার কথা, সিনেমা লাখ লাখ লোককে একসঙ্গে একেবারে কমপ্লিট মোচড় দিতে পারে। এইভাবে আমি সিনেমাতে আসি, সিনেমা করব বলে আসিনি। কাল যদি সিনেমার চেয়ে বেটার মিডিয়াম বেরোয়, তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব।’
এখন তাহলে ঋত্বিকের মোটিভ ও কমিটমেন্ট বোঝা গেল। অন্যদিকে মাধ্যমটা তাঁর কাছে বিষয় ছিল না, বিষয় ছিল বক্তব্য। দেশ ও দেশের মানুষকে জাগাতে যে-মাধ্যমটা কার্যকরী তা-ই আসল, যে-মাধ্যমে যত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় তাতেই তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কিন্তু মাধ্যম দিয়ে কী পৌঁছাবেন শিল্পী? সে তো বক্তব্যই, ‘আমার কাছে বক্তব্যের মূল্য আছে। আমি কেন এ-সমস্ত মাধ্যম চেঞ্জ করেছি, বদলেছি? কারণ বক্তব্যটা মানবদরদি। বক্তব্য বলার চেষ্টা বা পৃথিবী সম্বন্ধে জানা বা মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি মমত্ববোধের প্রশ্নটাই প্রথম কথা, সিনেমার প্রতি মমত্ববোধটা কোনো কাজের কথাই না, ও-সমস্ত যারা aesthete, তারা করুন গিয়ে। Arts for art’s sake যারা, তারা করুন গিয়ে।’ তাঁর মোদ্দা কথা হচ্ছে All art expression should be geared towards the betterment of man-for man.
আর ঋত্বিক এ-মন নিয়ে হাঁটলেন ফিল্মের দিকে। তাও আসলেন ফিল্মের নতুন ঘরানা ধরে। হলিউডের রৈখিক কাহিনি-বিন্যাস, ঘটনার ঘনঘটা আর দৃশ্যাড়ম্বর রীতি তাঁকে টানল না, রাশিয়ার বাস্তবনিষ্ঠতা তাঁকে পথ দেখাল। সের্গেই আইজেনস্টাইন প্রথমে ‘স্ট্রাইক’, পরে ‘ব্যাটলশিপ পোটেমকিন’ ফিল্ম দিয়ে সোভিয়েট বাস্ততার সূত্রপাত করেন। জার্মানিতেও নতুন বাস্তবতার ফিল্ম তৈরি হয় বিশের দশকে। যুদ্ধোত্তর কালের কথকথার পরিধি ছাড়িয়ে স্বয়ম্বর ভাষানিষ্ঠ নিও-রিয়েলিস্টিক ধারার ফিল্ম তাও তাঁকে টানল না। সোভিয়েটের চরিত্র ছিল বিপ্লবী; মানুষের অন্তরকে জাগাও। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়ো। তাই আইজেনস্টাইন হলেন তাঁর ভাবগুরু, তাঁর কাছেই শেখা ঋত্বিকের সিনেমার ভাষা। আর ভাবগত দিক থেকে বিপ্লব-উত্তর লেনিনীয় সাংস্কৃতিক রণকৌশলের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিজের অন্তর্গত চৈতন্যের প্রকাশ। ঋত্বিকের ফিল্মের কৌশল প্রসঙ্গে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছিলেন, ‘কাইয়ে দু সিনেমা’র নবীন সদস্য জঁ-লুক গোদার যখন পঞ্চাশ দশকের শেষ ও ষাটের দশকের শুরুতে সিনেমার পর্দায় পরিসংখ্যান, রাজনীতি, দর্শন ও ব্যক্তিগত সংস্কার অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট শিল্পরূপকে বহু নিন্দিত বর্ণনাধর্মের অভিশাপমুক্ত প্রায় তখনই, কথঞ্চিৎ আগে পরে, আমরা বলার চেষ্টা করব প্রাচ্য ভূখণ্ডে ঋত্বিককুমার ঘটকের পৌরহিত্যে চলচ্চিত্র সুচারু প্লটের মায়াজাল ছিন্ন করে বক্তব্যধর্মী হয়ে উঠল।’ কাব্য, নাট্য ও কথাসাহিত্যের তথাকথিত প্লটবিন্যাস পালটে গিয়েছিল অন্তত টি এস এলিয়ট, বের্টোল্ড ব্রেশ্ট ও জেমস জয়েসের রচনায়। ঋত্বিক এ-ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। চলচ্চিত্রও যে নতুন বার্তা নিয়ে হাজির তা ধরতে পেরেছিলেন শুরুতেই, ‘ছবিতে গল্পের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন এসেছে বক্তব্যের যুগ। শুধু ছবির কথা কেন বলব, সব শিল্পেই এই বিবর্তন ঘটেছে। বহু আগে জেমস জয়েস কর্তৃক তাঁর ‘ইউলিসিস’ উপন্যাসে এই ধারা এনেছিলেন, বের্টোল্ড ব্রেশ্ট তাঁর ‘ড্রামস ইন দ্য নাইট’ নাটকে এই ধারার প্রবর্তন করেন।’ শুরু থেকে ঋত্বিক এই ধারা অনুসরণ করেন এবং তার সঙ্গে সিনেমার ভাষায় আইজেনস্টাইনের দেখানোর পথের সঙ্গে যুক্ত করেন মার্কসীয় দ্বন্দ্বচিন্তার সংশ্লেষ। এটাই হয়ে উঠল ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের বিশিষ্টতা।
২.
ঋত্বিক ঘটকের প্রথম সম্পূর্ণ ছবি ‘নাগরিক’ ১৯৫৩ সালে নির্মিত হলেও ১৯৫৮ সালে নির্মিত দ্বিতীয় ছবি ‘অযান্ত্রিক’ই জনসমক্ষে প্রদর্শনের প্রথম সুযোগ পায়। সত্যজিৎ রায় ‘নাগরিক’ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘“নাগরিক” যদি ‘পথের পাঁচালি’র আগে মুক্তি পেত তবে বাংলা ছবির ক্ষেত্রে ‘নাগরিক’ই দিশারি হয়ে থাকত।’ কারণ ‘নাগরিকে’র নির্মাণ ‘পথের পাঁচালি’রও আগে। এমনটা কেন বলেছিলেন সত্যজিৎ? ‘নাগরিক’ ঋত্বিকের নিজের লেখা চিত্রনাট্যের ওপর নির্মিত বাস্তববাদী ছবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণার প্রথম বস্তুনিষ্ঠ শিল্পরূপ। এটাই শেষ কথা নয়, একটি অতি সাধারণ কাহিনি কীভাবে রাজনৈতিক হয়ে উঠতে পারে ছবিটিতে তাই দেখানো হয়েছে। ছবির বিষয়বস্তু নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন। যুবক রামু চাকরির জন্য প্রতিদিন রাস্তায় ঘুরে, চাকরি পায় না। তাকে কেন্দ্র করে আছে আরও ক’টি অবসাদগ্রস্ত, উদাসী জীবন। যে-করে হোক বেঁচে থাকার লড়াই সবার। কিন্তু টিকে থাকার লড়াইয়ে ওরা দেখে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নীতিহীনতা ইত্যাদি জীবনের ভগ্ন রূপ। রামুর চাকরি হয় না, বাবার অকালে মৃত্যু হয়। প্রেমিকা উমার সঙ্গেও সংকট। ভীরুতা, হীনন্মন্যতা, কাপুরুষতা তাকে ক্রমাগত গ্রাস করে। কিন্তু প্রতিদিন আশায় বুক বাঁধে। একসময় রামুর মনে হয় সমাজ-রাষ্ট্রের চলমান কাঠামোতে তার কোনো পরিবর্তন আসবে না, সে নীচেই পড়ে থাকবে আজীবন। এই উপলব্ধির সঙ্গে সিদ্ধান্তও নেয়, আর স্বপ্ন নয় লড়াইয়ে নামতে হবে। রামুর লড়াইয়ের যোগ্য সঙ্গী উমাই হোক। হাতের সংখ্যা তো বাড়ল। গল্প এটুকুই, কিন্তু গল্পের ভেতর যে বক্তব্য তা সচেতন দর্শককে ভাবিত করে।
স্বাধীনতার পর মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তজীবনে যে-সংকট ঘনীভূত হয় তা থেকে মুক্তির কোনো পথ দেখা যাচ্ছিল না। যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতার মোহমুক্তি ঘটেছিল, দেখতে পেয়েছিল সমাজজুড়ে উপনিবেশকদের সমান অত্যাচারের খড়্গ, চারদিকে বিফলতার গহ্বর। মধ্যবিত্তের জীবনের সংকট ও বেঁচে থাকার লড়াইকে উপজীব্য করে ঋত্বিক একটা বয়ানও তৈরি করেন। নিজেও বলছেন, ‘আমি বিশ্বাস করি না যে আমার কোনো শিল্পকর্ম করার অধিকার আছে যদি না দেশের সংকটকে কোনো না কোনো দিক থেকে উদ্ঘাটিত করে তুলতে পারি। আমার বেশিরভাগ ছবিই সেই সংকটকে ধরবার চেষ্টা মাত্র।’ কারণ সংকটটা তো তিনি জানেন ‘যেখানে দারিদ্র্য আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, সেখানে কালোবাজারি আর অসৎ রাজনীতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি।’ ঋত্বিক সংকটের মূলে প্রবেশ করতে চান, আর একই সঙ্গে চান সংকট থেকে মুক্তিও। কিন্তু তিনি তো তরুণ, একজন শিল্পী তার ক্ষমতা আর কতটুকু। একটা গল্প লিখেন; চিত্রনাট্য তৈরি করে সমমনা ভূপতি নন্দীর কাছে আরজি জানান, ছবিটি করতে চান, করা প্রয়োজন। ভূপতি নন্দী থিমটা ধরতে পারেন; ঋত্বিকের রাজনৈতিক স্ট্যান্ড, হয়তো তাঁরও। তিরিশ বছর পরে লিখেও ছিলেন ভূপতি নন্দী, ‘ওই সময়টাতে আমরা প্রায় সকলেই তখন একটা কিছু করতে চাইছিলাম, কিন্তু কোন পথে যে সেই কিছুটা করা যাবে তার একটা পরিষ্কার ধারণা আমরা তখনও পড়ে তুলতে পারিনি। ‘নাগরিকে’র কাহিনির মধ্যে পেলাম মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতার সেই নিখুঁত ছবি যা উপলব্ধির আলোকে সব পরিষ্কার করে দেয়। এই প্রথম শুনলাম যে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ করা যায়, যা শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতিরই পরিপূরক।’ ছবিতে আরেকটা জিনিস দেখা যায় যে এত সংকটের মধ্যেও জীবনকে অস্বীকার করার প্রয়াস কোথাও নেই। আছে ভবিষ্যতের আশাবাদ, আর মৃত্যুকে পেছনে ফেলে জীবনের পথে সংগ্রামের প্রত্যয়। সম্মিলন ও সংগ্রাম এটাই ঋত্বিকের দেখানো রাজনৈতিক পথ। ‘নাগরিক’ ছবিতে সরাসরি রাজনীতির বয়ান কোথাও ছিল না, কিন্তু ঋত্বিকের বন্ধুদের কেউ কেউ মন্তব্যও করেছেন ভয়ংকর ‘রাজনীতি-ঘেঁষা’ বলে। ঋত্বিক নিজেও অস্বীকার করেননি, একটা সাক্ষাৎকারে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, ‘ছবিতে আমাদের একটা প্রাণপণ চেষ্টা ছিল রাজনৈতিকভাবে কিছু করার, কিছু বলার।… তখন বিটিআর-এর যুগ, বিটি রনদিভে, অর্থাৎ লেফটিজম-এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ঢুকে গিয়েছিল, অনেকটা এখনকার নকশালবাড়ি রাজনীতির মতো।…ও ছবি দেখলে লোকে ভাবত ঋত্বিক ঘটক রাজনীতির জন্য ছবি করে। ও-ছবিতে রাজনীতি ছিল সোচ্চারভাবে, বেশির কমভাবে।’ অর্থাৎ ঋত্বিক ঘটক প্রথম ছবি প্রবল রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েই শুরু করেন।
ঋত্বিকের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘অযান্ত্রিক’ ছিল ভিন্ন স্বাদের, বাংলা সিনেমার ইতিহাসে। তখনকার সময়ের চালে নিও-রিয়েলিস্টিকের পরিবর্তে ফ্যান্টাসটিক রিয়েলিজম ধারার। ‘নাগরিকে’র রেশমাত্র কোথাও নেই না বিষয়ে, না নির্মাণে।
ঋত্বিকের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘অযান্ত্রিক’ ছিল ভিন্ন স্বাদের, বাংলা সিনেমার ইতিহাসে। তখনকার সময়ের চালে নিও-রিয়েলিস্টিকের পরিবর্তে ফ্যান্টাসটিক রিয়েলিজম ধারার। ‘নাগরিকে’র রেশমাত্র কোথাও নেই না বিষয়ে, না নির্মাণে। এর পরের ছবি ‘মেঘে ঢাকা তারা’তে খুঁজে পাওয়া গেল মধ্যবিত্তের সেই নিষ্পেষিত সংগ্রামশীল অদম্য জীবন ও রাজনীতির ভেতরগত দিক। ঋত্বিক নিজে বলেছেন এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি। ছবিটি নির্মিত হয় ১৯৬০ সালে শক্তিপদ রাজগুরুর ‘চেনামুখ’ গল্প অবলম্বনে। তবে মূল লেখকের গল্পটাকে ভেঙেচুরে পরিবর্তন করে চিত্রনাট্যটা তিনি রচনা করেন। গল্পের বিষয় সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবন হলেও চলচ্চিত্রকার হিসেবে ঋত্বিক ব্যবহার করেছেন ঐতিহ্যমিশ্রিত দেশজ পটভূমিকা। এ ব্যাপারে বলেছেনও যে, ‘এইখানে আমি ভারতীয় মাইথোলজিকে ব্যবহার করা শুরু করি। যেটা আমার জীবনের অংশ।’ কিন্তু ‘মেঘে ঢাকা তারা’র বিশেষ দিক রাজনৈতিক অনুষঙ্গ। ভারতীয় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মর্মন্তুদ ইতিহাস চিত্রায়ণের এটি ছিল সূচনামুখ। বঙ্গবিভাজনের ফলে বাঙালিজীবনে যে-উদ্বাস্তু-সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করে তার ইতিবৃত্ত দেখা যাবে তাঁর পরবর্তী আরও দুই ছবি ‘কোমলগান্ধার’ ও ‘সুবর্ণরেখা’তে। যাদের ঋত্বিক ঘটকের ট্রিলজি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।
‘মেঘে ঢাকা তারা’ দেশভাগ-পরবর্তী বাংলার গল্প। এক নিম্নমধ্যবিত্ত শরণার্থী পরিবারের স্বপ্ন-আশা মিশ্রিত টিকে থাকার লড়াই। কাহিনিতে পরিবারটি যে উদ্ধাস্তু কোথাও বলা নেই। স্কুলশিক্ষক বাবা আর গৃহিণী মাকে নিয়ে দুই ছেলে দুই মেয়ের পরিবার। নীতা উপার্জনক্ষম, তার রোজগারে সংসার চলছে, বড়ো ভাই শংকর বড়ো শিল্পী হওয়ার সাধনায় মশগুল। নীতার আছে প্রেমিক, সনৎ। ভালোই চলছিল, হঠাৎ বাবা দুর্ঘটনা-কবলিত হলে পুরো পরিবারের দায়িত্ব পড়ে নীতার ঘাড়ে। সনৎ বিয়ে করতে চায় নীতাকে, নীতা সময় চায় পরিবারের জন্য। এরই মধ্যে পরিবারের ছোটো ছেলে মন্টু চাকরিতে যোগ দেওয়ার কদিন বাদে কারখানায় দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শয্যাশায়ী হয়। দুর্যোগ ঘনীভূত হয়, নীতা আর সনতের দূরত্ব বাড়ে, এই ফাঁকে সনৎ নীতার চঞ্চলমতি ছোটোবোন গীতার হাতছানিতে সাড়া দিয়ে আকস্মিক বিয়ে করে বসে। শংকর দেশান্তরী হয়। এদিকে কঠিন জীবনযুদ্ধে নীতার শরীর ভেঙে পড়ে, আক্রান্ত হয় যক্ষ্মায়। রোগের কথা কাউকে সে বলে না, আর বাড়ির কোথাও এক কোণে নির্বাসিত হয়ে জীবন কাটাতে থাকে। এরই মধ্যে শংকর বড়ো গায়ক হয়ে অর্থবিত্ত নিয়ে বাড়ি ফেরে দেখে নীতার মরণাপন্ন অবস্থা। সে নীতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে শিলং পাহাড়ের হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, নীতা মারা যায়। কিন্তু মৃত্যুর আগে ভাইকে জড়িয়ে পাহাড় কাঁপিয়ে ঘোষণা করে বেঁচে থাকার আকুতি: ‘দাদা, আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমি যে বাঁচতে বড়ো ভালোবাসি।’ ছবিতে এ-টুকুই গল্প। কিন্তু এরই মধ্যে ঋত্বিক দেখিয়েছেন দেশভাগের বঞ্চনা ও যন্ত্রণা, স্বার্থপরতা ও দায়িত্বশীলতা, অবক্ষয় ও আবেগ, উচ্চবিত্ত ও বিত্তহীনদের মধ্যকার তফাত। সর্বোপরি নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই কত কঠিন ও পীড়াদায়ক। গল্পে দেখা যায় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সংসার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবে তাই নীতাকে বিয়ে দিতে অনিচ্ছুক তার মা। আবার মাথার ওপর যে মেয়ের বোঝা সেটাও অনুভব করেন তিনি সর্বদা। তাই গীতার সঙ্গে সনতের মিশতে দেওয়া কিংবা বিয়ে দেওয়াতে আপত্তি করেননি। এই যে স্বভাব তা মাতৃবিরুদ্ধ, কিন্তু মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ নয়। ঋত্বিক দেখিয়েছেন অস্তিত্বরক্ষার জন্য মাও সন্তানের সর্বতো কল্যাণ নাও চাইতে পারেন। কিন্তু শয্যাশায়ী বাবা এটা মেনে নিতে পারেননি কোনোভাবে, কিন্তু তিনি অসহায়। গীতার বিয়ের ঘটনায় তিনি দাঁত চেপে সহ্য করছেন সত্যকে। আর সত্য যে বড়ো নির্মম। একপর্যায়ে নিজের যন্ত্রণা আর চেপে রাখতে পারেন না, উচ্চারণ করেন ‘সেকালে মাইনষে গঙ্গাযাত্রীর গলায় ঝুলাইয়া দিত মাইয়্যা, তারা ছিল বর্বর। আর একালে আমরা শিক্ষিত, সিভিলাইজড। তাই লিখাপড়া শিখাইয়া মাইয়ারে নিংড়াইয়া, ডইল্যা, পিষ্যা, মুইছা ফেলি ভবিষ্যৎ। ডিফারেন্সটা এই।’ নিজে খুব শ্রেণিসচেতন ছিলেন নীতার বাবা। একপর্যায়ে বলেন মধ্যবিত্ত শেষপর্যন্ত এই পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। এই যে শ্রেণিচেতনা এটাও গল্পের বিশেষ দিক। পুঁজিবাদী সমাজে যে-শ্রেণিব্যবধান ও শ্রেণিশোষণ, মালিক আর শ্রমিকপক্ষের মধ্যকার দূরত্ব ও ভেদ তার প্রকাশও বিভিন্ন দৃশ্য ও সংলাপে দেখা যায়। সবেচেয়ে বড়ো কথা জীবনের প্রতি দরদ এবং বেঁচে থাকার লড়াই ও আকাঙ্ক্ষা; মৃত্যুর চেয়ে জীবন বড়ো কিংবা মৃত্যু জীবনকে পরাভব করতে পারে না নীতার জীবন দিয়ে দেখালেন যা ঋত্বিকের ছবির প্রধান দিক তাও এতে দেখা যায়।
সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি আপনাকে এলিয়েনেট করব প্রতি মুহূর্তে। যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন, ছবি দেখে বাইরের সেই সামাজিক বাধা বা দুর্নীতি বদলের কাজে লিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার প্রটেস্টকে যদি আপনার মাঝে চারিয়ে দিয়ে পারি তবেই শিল্পী হিসেবে আমার সার্থকতা।’
ঋত্বিক দেশভাগকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে, দেশভাগের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। এমনকি বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর যে-ভেঙে-পড়া দশা তিনি মনে করতেন দেশভাগ-এর ‘বেসিক ফেক্টর’। জীবনের যে-ক্রান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানি তা ওই একই কারণে। তিনি বলেন তাই, ‘এই দেশভাগকে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারিনি। আজও পারি না।’ এর বিপরীতে তাই একজন শিল্পী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব মনে করেন একটা ডিসকোর্স বা থিসিস হাজির করা। সেটা কী? তার কথায়, ‘আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাব যে, It is not an imaginary story, বা আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসিনি।…যা দেখেছেন একটা কল্পিত ঘটনা, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যেটা বোঝাতে চাইছি আমার সেই থিসিসটা বুঝুন, সেটা সম্পূর্ণ সত্যি। সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি আপনাকে এলিয়েনেট করব প্রতি মুহূর্তে। যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন, ছবি দেখে বাইরের সেই সামাজিক বাধা বা দুর্নীতি বদলের কাজে লিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার প্রটেস্টকে যদি আপনার মাঝে চারিয়ে দিয়ে পারি তবেই শিল্পী হিসেবে আমার সার্থকতা।’
ঋত্বিকের মূল অভিপ্রায় ছিল দেশের সংকটকে শিল্পকর্ম দিয়ে উদ্ঘাটিত করা এবং বাংলার জরাজীর্ণ চেহারাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা, বাঙালিকে নিজের অস্তিত্ব, নিজের ইতিহাস-ঐতিহ্য-অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করা। তিনি জানতেন স্লোগান মঙ্গারিং করে, বড়ো বড়ো থিওরি কপচিয়ে সমাধান দেখানো তাঁর কাজ নয়। যেহেতু চলচ্চিত্র শিল্পে তখনও দেশের সংকট ও সমস্যাকে কেউ তুলে ধরেননি তাই তাঁর একটা কর্তব্য রয়েছে। ‘আমি যদি সেটা করতে পারি, লোকের সামনে ছুড়ে ফেলতে পারি যে এই হলো তোমাদের সমস্যা, এখন ভাবো—What to be done—তাহলেই যথেষ্ট। আমার মনে হয় এটাই আমার কাজ।’ তাই দেখা যাবে ‘মেঘে ঢাকা তারা’তে তিনি কোনো প্রেসক্রিপশন দেননি। বিভক্ত হওয়া দুই দেশের মিলনের প্রসঙ্গও তুলেননি, ভাবেনওনি। আর এ ব্যাপারে তিনি সচেতনও ছিলেন যে, পরে বলেছেনও ‘মেঘে ঢাকা তারা’ দিয়ে যখন আরম্ভ করলাম তখনও আমি রাজনৈতিক মিলনের কথা বলিনি, এখনও ভাবি না। কারণ ইতিহাসে যা হয়ে গেছে তা পালটানো ভীষণ মুশকিল। সেটা আমার কাজও নয়।’ তার বদলে তাঁর ছবিতে বারবার এসেছে পুরাণ ও ঐতিহ্য, সমন্বয়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আর আবহমান বাংলা। একই সঙ্গে বর্তমানের দারিদ্র্য, নীতিহীনতা, কালোবাজারি, অসৎ রাজনৈতিক রাজত্ব, নিম্নবিত্ত মানুষের বিভীষিকাপূর্ণ জীবন ও দুঃখেভরা নিয়তি।
রাজনৈতিক মিলনে তো অনেক বাধা, সম্ভাবনা বলতে শূন্যও—তাঁর মনে হয়েছিল; কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় যে-সূত্রে—সংস্কৃতি—তার মধ্য দিয়ে মিলন তো সম্ভব। কারণ সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালিদের বদল করা সম্ভব নয়—উভয় বাংলার মানুষের সংস্কৃতি এক। ঋত্বিকের কথা হচ্ছে, ‘রাজনৈতিক মিলনের কথাবার্তা… ও-সমস্তের মধ্যে আমি নেই। আমি ওগুলি বুঝিও না, আর আমার দরকারও নেই। কিন্তু সাংস্কৃতিক মিলন—আমি দুই বাংলাতেই কাজ করেছি, এবং করছি। এবং আমার থেকে বেশি কেউ করেনি।’ তাই দেখা যায় পরবর্তী ছবি ‘কোমলগান্ধারে’ সাংস্কৃতিক মিলনের কথা দেখিয়েছেন, যা ‘মেঘে ঢাকা তারা’তে ছিল এবং ‘সুবর্ণরেখা’তেও আছে। ঋত্বিক সাক্ষাৎকারে স্বীকারও করেছেন যে ‘মেঘে ঢাকা তারা’ তাঁর ‘subconscious affair’, ‘কোমলগান্ধার’ ‘conscious affair’ এবং ‘সুবর্ণরেখা’ ‘serioue work’. আর ছবি তিনটির যোগসূত্রতা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই একটা অন্তর্নিহিত সূত্র আছে।… যোগসূত্র এই তিনটার মধ্যে একই মাত্র। সেটা হচ্ছে দুই বাংলার মিলন। দুইডা বাংলারে আমি মিলাইতে চাইছি। দুইডারে আমি ভালোবাসি হেইডা কমু গিয়া মিঞা, এবং আমি আজীবন কইয়া যামু, যখন মৃত্যুপর্যন্ত আমি কইয়া যামু।’ যদি বলতে হয়, এটাই ঋত্বিক ঘটকের রাজনীতি।
‘কোমলগান্ধার’ নির্মিত হয় ১৯৬১ সালে, ঋত্বিকের নিজের কাহিনি ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে। গণনাট্য আন্দোলনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নাট্য-আন্দোলনের দলাদলি, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নিয়ে নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে। দেশভাগের রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে যুবক ভৃগু যে-নাট্যদল গড়ে তোলে সেই দলের নাটক হয় দেশভাগ নিয়ে; তারপর নাটক শকুন্তলা অভিনীত হবে। অনসূয়া নামের তরুণী যে অন্য আরেকটি দলের, সেই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েই শকুন্তলা রিহার্সেল হয়। কিন্তু মঞ্চে এসে তা ভেস্তে যায়। তারপর নতুন আরেকটি নাটক লেখা হয় যাতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ক্ষুদিরাম থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সব আছে। এদিকে ভৃগুর সঙ্গে অনসূয়ার প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়, যদিও অনসূয়া সমর নামের আরেক প্রবাসী তরুণের কাছে দায়বদ্ধ। শেষপর্যন্ত নাট্যসূত্রে ভৃগু ও অনসূয়ার প্রেমের পরিণতি হয় জীবন ও সংগ্রামের প্রতিজ্ঞায়। নাটকের অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক আন্দোলন, দাবি আদায়ের লড়াই, নাট্যাভিনয় প্রভৃতিকে ছাপিয়ে দেশভাগের ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে ‘কোমলগান্ধারে’র মূল বিষয়। ঋত্বিক পূর্ববঙ্গ থেকে তাড়া খেয়ে আসা লোক, তাই সিনেমায় পূর্ববঙ্গের নস্টালজিয়া—মায়ের স্মৃতি, প্রকৃতি, জীবন, সংস্কৃতি ও সুর প্রভৃতি দৃশ্যের পর দৃশ্যে অনুরণিত হতে দেখা যায়। ঋত্বিক নানা মাত্রিকতা দিয়ে সিনেমাটি তৈরি করেছিলেন, সেখানে দেশভাগোত্তর মর্মন্তুদ জীবন, তৎকালীন যুবচিত্ত, শিল্পবোধ, সামাজিক দায়, নারীশক্তি, ঐতিহ্য ও মিথের পুনর্গঠন, কালিদাস ও শেকসপিয়রের চরিত্রের নবায়ন, দ্বিধাগ্রস্ত মন, আবহমান বাংলার গীত ও সুর, সমন্বয়পন্থি সংস্কৃতি, লোকায়ত বাংলা সর্বোপরি মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যায়। ছবির প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যেও একটি অখণ্ড বাংলাকে দেখতে পাই। শুরু থেকে শেষপর্যন্ত দেশপ্রেমের সুর ধ্বনিত হয়; নাট্যদলের সকলের মুখে গণনাট্য সংঘের নবজীবনের গান, গণসংগীত শোনা যায়। পদ্মাপারের লোকসংগীত, বিয়েরগান, মুকুন্দদাশের গান, মুসলমান লোককবির গান প্রভৃতিতে এক অসাম্প্রদায়িক বাংলার রূপ ফুটে উঠতে দেখা যায়। অনসূয়ার মায়ের স্মৃতিতে, ডায়েরিতে রয়েছে নৃশংস দাঙ্গার কথা, গান্ধীর নোয়াখালি অবস্থানের কথা।
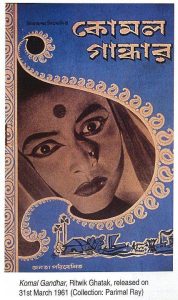
কোমলগান্ধার সিনেমার পোস্টার
ঋত্বিক ‘কোমলগান্ধার’-এ বাংলাকে করুণভাবেই অঙ্কিত করেছেন। অনসূয়াকে বাংলাদেশের শকুন্তলা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যে একদিন তপোবন ছেড়ে দেশান্তরী হয়েছিল। শকুন্তলাকে যেমন পরিচিত জগৎ, আজন্ম বাসভূমি আশ্রম ছেড়ে নিজেকে ছিন্ন করেছিল অনসূয়াও তাই। শুধু অনসূয়া নয়, পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুচ্যুত অন্যান্য লোকের চরিত্রেও ওই একটি দিক; শেকড়চ্যুতির মর্মবেদনা দেখিয়েছেন ঋত্বিক। সিনেমার শুরুতে নাট্যদলের যে নাটক মঞ্চস্থ হয় তাতে পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত বুড়োটি চিৎকার করে প্রতিবেশীকে বলে, কেন যামু? বুঝা আমারে! এমন কোমল দ্যাশটা ছাইড়া, আমার নদী পদ্মারে ছাইড়া আমি যামু ক্যান?
—যাইবা খাইবার লাইগ্যা! এই শেষ সুযোগ, এখনো শরণার্থী হও!
—কী? শারণার্থী?
—বাস্তুহারা শারণার্থী! নাম দিছে কাগজের বাবুরা।
—ছি! ছি! ছি।
বুড়োর মেয়ে যখন কলকাতার কল্পনায় বাপকে কলকাতার জৌলুস নিয়ে প্রশ্ন করে তখনও বুড়ো চিৎকার করে বলে, আমি একটা কপাল পোড়া। আমার চৌদ্দ পুরুষ কপালপুইড়া। যে-কয়টা জন্ম দিছি সব কয়টা কপালপোড়া। নইলে আমি এ-পদ্মার পারে জন্মাইলাম ক্যান!
আবার পদ্মার এপারে দাঁড়িয়ে পারে ভৃগু ও অনসূয়া যখন দেশের স্মৃতিচারণ করছিল তখন সংলাপগুলো ছিল এমন—
অনসূয়া: সেই নিশ্চিন্তি বোধ হয় আমরা আর ফিরে পাব না। মনে হয় আমরা যেন কেমন বাইরের লোক হয়ে গেছি। আপনার মনে হয় না? …
ভৃগু: ওই পারেই আমার দেশের বাড়ি। ওই যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। এত কাছে, অথচ কোনো দিন আমি ওখানে পৌঁছাতে পারব না। ওটা বিদেশ। যখন তুমি বলছিলে ওপারে তোমার দেশের বাড়ি তখন আমি কী খুঁজছিলাম জানো? নিজের বাড়িটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিলাম। কারণ, কোথাও নয়, ঠিক ওপারেই আমার দেশের বাড়ি… যে রেললাইনটার ওপরে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কলকাতা থেকে ফেরার সময়, ঠিক ওইখানে আমি ট্রেন থেকে নামতাম। স্টিমার থাকত দাঁড়িয়ে, ওপারে নিয়ে যেত। মা! অপেক্ষা করে থাকতেন। ওখানে দাঁড়িয়ে একটা মজার কথা মনে এলো, মনে হলো, ওই রেললাইনটা তখন ছিল একটা যোগচিহ্ন, আর এখন, কেমন যেন বিয়োগ চিহ্ন হয়ে গেছে। ওখানে দেশটা কেটে দু-টুকরো হয়ে গেছে।’ এই বেদনাপীড়িত গাঁথাই ‘কোমলগান্ধার’ যার আবহজুড়ে নস্টালজিক সুর, এই সুরকথায়ই আবহমানের ভাঙা-বিধ্বস্ত বাংলাকে বাঁধতে চেয়েছেন ঋত্বিক। লিখেছেনও এ ব্যাপারে যে, ‘শকুন্তলা বাংলাদেশে পরিণত হয় আমার কাছে। রবিঠাকুরের সেই অত্যাশ্চর্য প্রবন্ধটি শকুন্তলা এবং মিরান্দার অপূর্ব তুলনা যেখানে রয়েছে, সেটি আমাকে প্রভাবিত করে। চারপাশে যে, যে-ভাঙন আমি জানি তার মূল হচ্ছে ভাঙা বাংলা। পূর্ববাংলার লোক বলে একথা মনে করি না। গোটা বাংলার ঐতিহ্যটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করি বলেই একথা জানি যে, দুই বাংলার মিলন অবশ্যম্ভাবী। তাই রাজনৈতিক তাৎপর্য আমার হিসাব করার কথা নয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক মূল্য আমার কাছে অবধারিত। তাই “কোমলগান্ধারে”র মূল সুর হচ্ছে মিলনের। স্বরের ওপর স্তর দিয়ে, রূপকের ওপর রূপক দিয়ে, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো যদি কোথাও সেই জীবনসত্যটিকে ছুঁতে পারি সেই চেষ্টাই করেছিলাম।’ অন্যত্রও বলেছেন, ‘আমি অনসূয়ার দ্বিধাবিভক্ত মন, বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্ব এবং দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশের মর্মবেদনা—তিনটিকেই একত্রে টানতে চেয়েছিলাম। শব্দের দিক থেকে বহুশত শতাব্দীর সুরকথাকে মিলিয়ে ছবির ওপরে নতুন দ্যোতনা অভিনিবিষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলাম। আর্কিটাইপালি এদের বিরোধী হচ্ছে বিবাহ মিলন।—‘আমের তলার ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া/আইলেনগো সুন্দরীর জামাই মটুকমাথায় দিয়া।/মিস্ত্রি বানাইছে পিড়ি মধ্যে চাইরকোনা তুলিয়া/ব্রাহ্মণে চিত্রাইছে পিড়ি মধ্যে সোনা দিয়া/আইজ হইব সীতার বিয়া।’ এই গানগুলি ব্যবহারের পিছনে একটি চিন্তার্থ ছিল তা হচ্ছে মিলনের ভাবখানি, যা অবশ্যাম্ভাবী। অন্যদিকে পূর্ববাংলার মুসলমান লোককবির গান, হজরত আলির নামের দোহাই আর রবীন্দ্রনাথের গানের সুর সর্বত্র দ্বিধাবিভক্ত দেশ ও সমাজের মিলনের বার্তা দিয়ে হাজির হয়েছে। আর এই মিলন কার মাধ্যমে আসতে পারে? ঋত্বিক সব সময় যে-নারীশক্তির উদ্বোধনের কথা বলেন এই সিনেমায়ও অনসূয়ার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, ‘মা বলতেন, পিশাচের বর্বরতা বারবার হানা দিচ্ছে এদেশে। তাই বীর তৈরি করতে হবে, আর সেই ক্ষমতা একমাত্র মেয়েদেরই আছে।’ ভৃগুকে অনসূয়া তার মায়ের ছেলে বলেই অভিহিত করে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ মিলনের পতাকাবাহী ভৃগু যেমন, সেও। ‘কোমলগান্ধার’ দর্শকের আনুকূল্য পায়নি। এমনকি মার্কসবাদী দর্শকও ছবিটি গ্রহণ করেননি। এতে ঋত্বিক বেদনাহত হয়েছিলেন।
এই গল্পের মূল কাহিনি দেশভাগের শিকার উদ্বাস্তু মানুষের কাহিনি। হরপ্রসাদ আর ঈশ্বর দুই নিপীড়িত ও জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত মানুষ। উদ্বাস্তু কলোনির কঠিন দায়িত্ব ফেলে বোন সীতা আর বাগদি বউ কৌশল্যার ছেলে অভিরামকে নিয়ে নতুন যুদ্ধ শুরু করে ঈশ্বর, বন্ধুর কারখানায় চাকরি নিয়ে।
‘সুবর্ণরেখা’ নির্মিত হয় ১৯৬২ সালে এবং প্রদর্শিত হয় তার চার বছর পরে। দেশভাগ নিয়ে ঋত্বিক-নির্মিত ট্রিলজির শেষ ছবি। ঋত্বিকের মতে তিনি কোনো ট্রিলজি করতে চাননি, কিন্তু হয়ে গেছে। এই গল্পের মূল কাহিনি দেশভাগের শিকার উদ্বাস্তু মানুষের কাহিনি। হরপ্রসাদ আর ঈশ্বর দুই নিপীড়িত ও জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত মানুষ। উদ্বাস্তু কলোনির কঠিন দায়িত্ব ফেলে বোন সীতা আর বাগদি বউ কৌশল্যার ছেলে অভিরামকে নিয়ে নতুন যুদ্ধ শুরু করে ঈশ্বর, বন্ধুর কারখানায় চাকরি নিয়ে। বসত গড়ে সুবর্ণরেখার তীরে। যে-নদীর ওপারে সীতা ও সীতা-পুত্র বিনুর স্বপ্নের বাড়ি। কয়েক বছর পরে ভাইয়ের অমতে একসঙ্গে বড়ো হওয়া অভিরাম ও সীতা বিয়ে করে কলকাতায় আসে। বাস দুর্ঘটনায় অভিরামের মৃত্যু হলে পতিব্রতী সীতার ঠাঁই হয় বেশ্যালয়ে। আত্মহত্যা করতে গিয়ে ফিরে আসা ভাই ঈশ্বর বেশ্যাগৃহে গমন করে মুখোমুখি হয় বোনের। সীতা আত্মহত্যা করে; ঈশ্বর জেল থেকে মুক্ত হয় সীতাপুত্র বিনুকে নিয়ে সুবর্ণরেখার ওপারের স্বপ্নের বাড়ির দিকে যাত্রা করে, যেখানে সত্যি কোনো ঠাঁই নেই। এই কাহিনির সঙ্গে যুক্ত আছে নানা শাখাকাহিনি, নানা চরিত্র ও ঘটনা এবং আধুনিক মনস্তত্ত্বের অনেক দিক। আছে প্রাচীন ঋষিমন্ত্র, রামায়ণের তত্ত্ব, নারীর মাতৃরূপ। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে দেশভাগের যন্ত্রণা, বঞ্চনা ও উন্মূল জীবনের করুণ রূপ। ‘সুবর্ণরেখা’ প্রসঙ্গে ঋত্বিক লিখেছেন, ‘প্রত্যক্ষভাবে “সুবর্ণরেখা” ছবিতে উপস্থাপিত সংকট উদ্ধাস্তু সমস্যাকে অবলম্বন করে আছে। কিন্তু উদ্বাস্তু বা বাস্তুহারা বলতে এ-ছবিতে কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদেরই বোঝাচ্ছে না ওই কথাটির সাহায্যে আমি অন্যতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছি। আমাদের দিনে আমরা সকলেই জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে আছি এটাও আমার বক্তব্য। বাস্তুহারা কথাটিকে এইভাবে বিশেষ ভৌগোলিক স্তর থেকে সামান্য স্তরে উন্নীত করাই অন্বিষ্ট, ছবিতে হরপ্রসাদের মুখের সংলাপে (“আমরা বায়ুভূত, নিরালম্ব”) কিংবা ছবির প্রথমেই এসে একজন কর্মচারীর মুখে “উদ্বাস্তু! কে উদ্বাস্তু নয়?” এই কথায় সেই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।’ এ-হয়তো ছবির দার্শনিক সত্য, কিন্তু সাধারণ সত্যে আছে দেশভাগজনিত উদ্বাস্তুসমস্যা যা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বয়ান করেছেন ঋত্বিক। ‘আমরা এক বিড়ম্বিত কালে জন্মেছি।… রূপকথা, পাঁচালি আর বারো মাসের তেরো পার্বণের গ্রামবাংলা নবজীবনের আশায় থৈ থৈ করছে। এমন সময় এলো যুদ্ধ, এলো মন্বন্তর, মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসরা দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটিকে দুটুকরো করে দিয়ে আদায় করল ভগ্ন-স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বন্যা ছুটল চারদিকে। গঙ্গা-পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। এ-আমাদের নিজের চোখের অভিজ্ঞতা।’ এই অভিজ্ঞতা এমনটাই নির্মম যে চিরটাকাল ধরে যে-বাঙালি পরস্পরের আত্মীয় হিসেবে বসবাস করে আসছিল উদ্বাস্তু হওয়ার ফলে এরা সকলে কেমন স্বার্থপর, হীন আর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। নিরাশ্রয় বাগদি বউ যখন নবজীবন কলোনিতে আশ্রয় চায় শুধু পাবনা জেলার নয় বলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আবার যে-ঈশ্বর চক্রবর্তী সংগঠক হিসেবে উদ্বাস্তু শিবিরের বাচ্চাদের পড়াশোনার ভার নিতে স্কুল খুলে সেও একটা চাকরি পেয়ে ভাগ্যান্বষণে শরণার্থী শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ে। যাওয়ার আগে তা বলতে গেলে বন্ধু ও সহসংগঠক হরপ্রসাদ তাকে পলাতক বলে অভিহিত করে। তাদের কথোপকথনটি ছিল এমন—
হরপ্রসাদ: তোমাদের ইংরেজিতে একটা কথা আছে না? deserter, পলাতক? মাফ করে দিও ভাই তোমার সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখলাম না।
ঈশ্বর: দাঁড়াও! আমার সমস্ত দায়িত্ব ওই মেয়েটা…
হরপ্রসাদ: আর ওই অভিরামরে তুমি কুড়াইয়া আনছিলা। যাইবার আগে গলায় পাও দিয়া মারিয়া যাও।
ঈশ্বর: ওর দায়িত্ব আমিই নেব।
হরপ্রসাদ: আর এই বেবাক মানুষের জীবনের দায়?
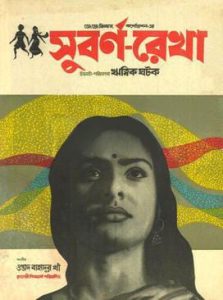 ঈশ্বর: একমুহূর্তে সব হারিয়ে গেছে আমার। সব ফেলে এসেছি। আমাকে আবার ঘর করতেই হবে। সীতার জীবনে এমন দুর্ঘটনা যেন আর না আসে। ওকে যেন অভাবে মরতে না হয়। এছাড়া আর কোনো দায়িত্বই আমার নেই।
ঈশ্বর: একমুহূর্তে সব হারিয়ে গেছে আমার। সব ফেলে এসেছি। আমাকে আবার ঘর করতেই হবে। সীতার জীবনে এমন দুর্ঘটনা যেন আর না আসে। ওকে যেন অভাবে মরতে না হয়। এছাড়া আর কোনো দায়িত্বই আমার নেই।
এই ঘটনার অনেক বছর পরে যখন হরপ্রসাদ আর ঈশ্বরের দেখা হয় তখন ঈশ্বরের উদ্দেশে হরপ্রসাদ বলেছিল, ‘দেখলা, আমরা এক্কেবারেই পরাজিত। আত্মহত্যা করার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নাই।’ দেশভাগের নির্মমতা এভাবে প্রত্যেকটি জীবনকে খর্ব করে দিয়েছিল। ঋত্বিক নির্মোহ দৃষ্টিতে যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন চলচ্চিত্রে তাই রূপায়িত করেন। তাঁর কথায়ও এমন প্রমাণ মেলে, ‘বিভক্ত জরাজীর্ণ বাংলার যে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি দিনের পর দিন, তার ওই পতিতালয়ের সীতার মতোই দশা। আর আমরা অবিভক্ত বঙ্গের বাসিন্দারা যেন উন্মত্ত নিশিযাপনের পর আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে বেঁচে আছি।’ ছবিতেও ন্যুব্জপীঠ হরপ্রসাদ নিজেকে শরীরী মানুষ নয় এক প্রেতাত্মা হিসেবেই ভাবে, ‘না, আমার প্রেতাত্মা। হেরেছি গেছি আমি, সর্বস্বান্ত। লড়ি, ছড়ি, আছি-বাজে-পোড়া তালগাছ। প্রতিবাদ করেছিলাম। কার প্রতিবাদ? কীসের প্রতিবাদ? এমন হয়েছে একটা দেয়ালে ধড়াম করে ধাক্কা খাইয়া, জাঁতাকলে অন্ধ হইয়া আষ্টেপৃষ্ঠে আটকাইয়া আছি।…আসল কথা কি জানো ভাইডি, প্রতিবাদই করো আর লেজ গুটাইয়া পলাইয়াই যাও কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সব লোপাট, আমরা সব নিরালম্ব, বায়ুভূত আমরা-আমরা মিটে গেছি!’ এইসব ঘটনা, কাহিনি ও সংলাপের ভেতর দিয়ে ঋত্বিক ব্যক্তিক স্তর পেরিয়ে সমষ্টিক চেতনাকেই প্রতিষ্ঠিত করেন। যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, বাস্তুচ্যুতি, জন্ম, মৃত্যু, হাহাকার পেরিয়ে ‘সুবর্ণরেখা’র সমাপ্তিতে দুর্মর আশাবাদ বা জীবনই হয়ে ওঠে প্রতিভূ; আর নবীন প্রজন্মের বিনুকে দিয়ে নবজীবনের সংগ্রাম ও আশাবাদ ব্যক্ত করেন ঋত্বিক অদ্ভুত গতিময়তায়। ছবিটি মুক্তির পর এবারও ঋত্বিক দর্শকের মন ভরাতে পারেননি। অনেকে একে নৈরাশ্যবাদ বা অবক্ষয়ের ছবি বা মেলোড্রামাটিক বলে অভিহিত করেন। ঋত্বিকের মতে যারা অর্থনেতিক ভাঙন আর রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে জানেন এবং পীড়িত মানুষকে উপলব্ধি করেন তাদের পক্ষে অভিরাম, সীতা, হরপ্রসাদ, ঈশ্বর প্রমুখ চরিত্রের সংকট কিংবা পতিতালয়ে ঈশ্বরের বোনের মুখোমুখি হওয়া ফানুশ বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। আসলে দেশভাগের রাজনীতি বাঙালিজীবনে সংকট তৈরি করেছিল তার প্রথম বলি ছিল মানুষের বোধশক্তি। এ প্রসঙ্গে ঋত্বিকের কথাও হচ্ছে, ‘এই সংকটের প্রথম বলি হচ্ছে আমাদের বোধশক্তি। সেই শক্তি ক্রমশ অসাড় হয়ে এসেছে আমাদের মধ্যে। আমি সেটাকেই ঘা দিতে চেয়েছিলাম।’ আর সেই ক্ষতে উপশম হিসেবে বরাবরের মতো সংস্কৃতিচেতনার আশ্রয় নেয় ঋত্বিক-দুই বাংলার প্রকৃতি, ভাষা, লোকগান, রবীন্দ্রনাথের গান ও সুর ছবির পরতে পরতে ব্যবহার করে মনের ভেতর একটা ঐক্যের বন্ধন তৈরি করেন।
দীর্ঘ এক দশক পর ১৯৭৩ সালে ঋত্বিক ঘটক নির্মাণ করেন ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস অবলম্বনে একই নামের ছবি। ঔপন্যাসিক ঋত্বিকের বন্ধু ছিলেন এবং উপন্যাসটি প্রকাশের পরই এটি দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন তিনি। চলচ্চিত্রটি নির্মাণের পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কিছু প্রেক্ষাপটও জড়িত ছিল। প্রথমত সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তি অর্থনৈতিক শোষণ আর পদাঘাতে কুমিল্লার তিতাসপারের মালোদের জীবনকে একেবারে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছিল। অদ্বৈত নিজে মালো হওয়ার কারণে জীবনের মূলসূত্র, শোষণ-বঞ্চনাকে তীব্র করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। দেখিয়েছিলেন এমন রূপ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যরস্থার চক্র থেকে মালোদের নিস্তার নেই। আবার নদীও যেখানে শুকিয়ে যাচ্ছে; তাই তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দুই বাংলার জনগণকে দারুণভাবে আন্দোলিত করে; সাংস্কৃতিকভাবে মানুষ তখন উজ্জীবিত হয়। তাই ঋত্বিক ভাবলেন গণমানুষের জীবনযুদ্ধ, বঞ্চনা ও শোষণকে মালোদের জীবনের মাধ্যমে, পূর্ববঙ্গের নদী ও নিসর্গের প্রেক্ষাপটে অখণ্ড বাংলাকে রূপায়িত করা যায়। যদিও উপন্যাসের বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ছিল না, কিন্তু ঋত্বিক ছবি নির্মাণকালে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রয়োগ করেন। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ভাঙা বাংলার অবস্থা বিবেচনা করে যে-সাংস্কৃতিক মিলনের কথা ঋত্বিক ভাবতেন চলচ্চিত্রটির মূল সুর তাই। ঋত্বিক তিতাসের রাজনীতি প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘অদ্বৈতবাবুর পক্ষে যা স্বাভাবিক ছিল, তা-ই তিনি করেছেন, শেষ করেছেন একটা অবক্ষয়ের মধ্যে, সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমার রাজনৈতিক বক্তব্য, সেখানে আমি সম্পূর্ণ প্রাণের পক্ষে, নতুন জীবনের ইঙ্গিতে ছবি শেষ করেছি। একে মার্কসিজম বলা যায়, আবার হিউম্যানিজম বলা যায়, রাজনীতি বলা যায়, আবার না-ও বলা যায়।’
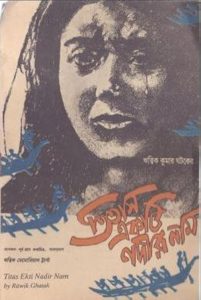 ঋত্বিক পূর্ববাংলা, তিতাস ও জনপদেও মানুষের যূথবদ্ধ মানুষের জীবনকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নদীমাতৃক বাংলায় যে-নদী একটা সাস্টেনিং ফোর্স—এরকম একটা নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, নদীতে চর উঠেছে, আর চাষিরা ফোরফ্রন্ট-এ এসে গেছে। তাই ইকোনমিক বেসটা ছবিতে বারবার তুলে ধরেছেন ঋত্বিক। কারণ ওই টাকা ধার দেওয়া, চক্রবৃদ্ধি সুদের ফাঁদে পড়া, তারপর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া—এই যে ইকোনমিক বেস, এটা দেশভাগ কিংবা স্বাধীনতার আগেও ছিল। কারা ছিল এর নায়ক ঋত্বিক জানতেন, কীভাবে কাদের ওপর এই শোষণপদ্ধতি চালু ছিল আর কার মদদে। ‘বাবুরা যে কী পরিমাণ অত্যাচার করেছে ওদের ওপর, ওই তোমরা যাকে সিডিউল কাস্ট বলো, তাদের ওপর ভাবা যায় না। এবং সে কারণেই দে অল ভোটেড ফর মুসলিম লীগ। এবং during partition এবং before partition they all sided with মুসলিম লীগ। এবং after partition তারাই রয়ে গেছে। যতগুলো জমিদার, সব চোর almost all, very few হয়তো ভালো। ওই ভাবে কতবার যে তারা কত লোককে, কত সম্প্রদায়কে উৎখাত করেছে, তার ঠিকঠিকানা নাই। আমি নিজে জমিদার বাড়ির ছেলে, আমার নিজের পরিবারে নিজের বাড়িতে দেখেছি। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান কোনো ব্যাপার নয়, ওই বাবুরা মুসলমান চাষিদের ওপর অত্যাচার করেছে, হিন্দু চাষিদের ওপরও অত্যাচার করেছে। ওই so called scheduled caste-দের ওপর।’ বোঝা যাচ্ছে ঋত্বিক কতটা সজাগ ছিলেন, তাই এটাকে রাজনৈতিক বয়ানে না নিয়ে আর্থসামাজিক বয়ান দিয়ে রাজনৈতিক ভাগ্য উন্মোচন করেছেন। দেখাতে চেয়েছেন সাতচল্লিশের স্বাধীনতা বলি, আর একাত্তরের স্বাধীনতা বলি এসব রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরেও নিম্নবর্গের মানুষের বাস্তবতা ওই সমান পর্যায়েই রয়ে গিয়েছিল। আর এসব মানুষ তাকে নিজেদের নিয়তির অভিসম্পাত বলে মেনে নিয়েছিল। ঋত্বিক চেয়েছেন সেই শ্রেণিশোষণকে উন্মোচন করা আর শ্রেণিসংগ্রামকে উসকে দেওয়া। এটা যদি রাজনৈতিক ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ একটি রাজনৈতিক ছবি বটে।
ঋত্বিক পূর্ববাংলা, তিতাস ও জনপদেও মানুষের যূথবদ্ধ মানুষের জীবনকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নদীমাতৃক বাংলায় যে-নদী একটা সাস্টেনিং ফোর্স—এরকম একটা নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, নদীতে চর উঠেছে, আর চাষিরা ফোরফ্রন্ট-এ এসে গেছে। তাই ইকোনমিক বেসটা ছবিতে বারবার তুলে ধরেছেন ঋত্বিক। কারণ ওই টাকা ধার দেওয়া, চক্রবৃদ্ধি সুদের ফাঁদে পড়া, তারপর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া—এই যে ইকোনমিক বেস, এটা দেশভাগ কিংবা স্বাধীনতার আগেও ছিল। কারা ছিল এর নায়ক ঋত্বিক জানতেন, কীভাবে কাদের ওপর এই শোষণপদ্ধতি চালু ছিল আর কার মদদে। ‘বাবুরা যে কী পরিমাণ অত্যাচার করেছে ওদের ওপর, ওই তোমরা যাকে সিডিউল কাস্ট বলো, তাদের ওপর ভাবা যায় না। এবং সে কারণেই দে অল ভোটেড ফর মুসলিম লীগ। এবং during partition এবং before partition they all sided with মুসলিম লীগ। এবং after partition তারাই রয়ে গেছে। যতগুলো জমিদার, সব চোর almost all, very few হয়তো ভালো। ওই ভাবে কতবার যে তারা কত লোককে, কত সম্প্রদায়কে উৎখাত করেছে, তার ঠিকঠিকানা নাই। আমি নিজে জমিদার বাড়ির ছেলে, আমার নিজের পরিবারে নিজের বাড়িতে দেখেছি। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান কোনো ব্যাপার নয়, ওই বাবুরা মুসলমান চাষিদের ওপর অত্যাচার করেছে, হিন্দু চাষিদের ওপরও অত্যাচার করেছে। ওই so called scheduled caste-দের ওপর।’ বোঝা যাচ্ছে ঋত্বিক কতটা সজাগ ছিলেন, তাই এটাকে রাজনৈতিক বয়ানে না নিয়ে আর্থসামাজিক বয়ান দিয়ে রাজনৈতিক ভাগ্য উন্মোচন করেছেন। দেখাতে চেয়েছেন সাতচল্লিশের স্বাধীনতা বলি, আর একাত্তরের স্বাধীনতা বলি এসব রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরেও নিম্নবর্গের মানুষের বাস্তবতা ওই সমান পর্যায়েই রয়ে গিয়েছিল। আর এসব মানুষ তাকে নিজেদের নিয়তির অভিসম্পাত বলে মেনে নিয়েছিল। ঋত্বিক চেয়েছেন সেই শ্রেণিশোষণকে উন্মোচন করা আর শ্রেণিসংগ্রামকে উসকে দেওয়া। এটা যদি রাজনৈতিক ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ একটি রাজনৈতিক ছবি বটে।
এটা গেল রাজনীতির এক দিক, অপর দিকে ঋত্বিকের যে এজেন্ডা দুই বাংলার মিলন তার ব্যাপারেও তিনি সমাজ সজাগ ছিলেন। শুরু থেকে একটা সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি, কারণ পশ্চিমবাংলা নিসর্গ-প্রতি, ভাষা, সংস্কৃতির ভেতরে লোকায়ত বাংলার সমস্তটা ধরা পড়ে না বলে তা দিয়ে অখণ্ড বাংলাকে আবিষ্কার কৃত্রিমই লাগত। তাঁর কাছে বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয়টা খটমটে। তাই তিতাসের আহ্বান যখন এলো তিনি লুফে নিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, ‘বাংলাদেশ কথাটাই আমার কাছে খুব খটকাজনক। এখনও ঠিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংজ্ঞা আমার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। এখনও পর্যন্ত ও-কথাটাকে আমি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানেতেই বুঝে থাকি। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যা-ব্রহ্মপুত্র-কুশয়ারা-তিস্তা-সুরমা ও তিতাস অধ্যুষিত বাংলার এই ভূভাগ আমাকে আকর্ষণ করে, তাই এই ছবি করার প্রস্তাব একজন হটেন্ট অথবা জুলুর কাছ থেকে এলেও সমানভাবে গ্রহণ করতাম।’ তিতাস ছবিটি শুরুও করলেন ঋত্বিক লালনের গান দিয়ে। নদীর সীমাহীন জলরেখা দিগন্তে মিলিয়ে যাছে, সেই জলে মাঘমণ্ডল ব্রতের ভেলা ভাসিয়ে দৃশের আরম্ভ। আর শেষ হলো তিতসের জল শুকিয়ে নদীতে চর উঠেছে আর চরের ধানগাছের সবুজ দেখা যাচ্ছে; বাঁশি বাজিয়ে একটি শিশু দৌড়াচ্ছে । এই শুরু ও শেষের মধ্যে আবহমান বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি ধারণ করা সম্ভব ঋত্বিক তাই করেছেন। যদিও ছবি করার আগে যে-মন নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন বাস্তবে দেখলেন ভিন্ন। কারণ এর মধ্যে তিরিশটি বছর কেটে গেছে, বদলে গেছে ভূপ্রকৃতি, বদলেছে জীবনপদ্ধতিও। কিন্তু ঋত্বিক তাঁর স্মৃতি থেকে, নস্টালজিয়া থেকে, নিজের জীবনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে তিতাসটা নির্মাণ করলেন। তিরিশ বছর আগেকার সেই পূর্ববাংলা উঠে এলো সিনেমায়। কিন্তু ভেতরে একটা হাকাকার ছিল সর্বদা, ‘ছবি করতে-করতে বুঝলাম সেই অতীতের ছিটেফোঁটা আজ আর নেই, থাকতে পারে না। ইতিহাস ভয়ংকর নিষ্ঠুর, ও হয় না, কিসসু নেই। সব হারিয়ে গেছে।’ তাহলেও সৎশিল্পীসুলভ ঋত্বিক এক অখণ্ড লোকায়ত বাংলাকেই হাজির করলেন দর্শকের সামনে; যেন বলতে চাইলেন এই হচ্ছে আমার নৈসর্গিক বাংলা; এই আমার যূথবদ্ধজীবনের সংস্কৃতি, আমাদের আত্মপরিচয়—আর আমরা একে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছি—আমরা আসলে এক। অন্যদিকে ছবিতে যে-গল্পটা বললেন ঋত্বিক, মূল কাহিনিকারের বক্তব্য থেকে একটু দূর সরে এলেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ গল্পের শেষে এসে দেখাতে চেয়েছেন তিতাস আর নেই, নদীকে কেন্দ্র করে মালোদের জীবন ও সংস্কৃতিও ক্ষয়ে গেল। সবকিছু স্মৃতি হয়ে গেল। অন্যদিকে ঋত্বিক দেখালেন তিতাসের বুকে চর উঠেছে, কিন্তু ধানখেত রয়েছে; বাঁশি বাজিয়ে একটি শিশু দৌড়াচ্ছে। অর্থাৎ এখানে ‘সুবর্ণরেখা’র মতো সমাপ্তিতে নতুন জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল শিশুর হাতে একটি নতুন পৃথিবীর সম্ভাবনা। ঋত্বিকের আশাবাদী জীবনদর্শনও তেমন যে, ‘সভ্যতার মৃত্যু নেই, সভ্যতা পরিবর্তিত হয় কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের। সেখানে তিতাসে ধানের খেত জন্মেছে, সেখানে আর-একটা সভ্যতার আরম্ভ। সভ্যতার মৃত্যু নেই। মানুষ অমর, individual মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষ অমর। সে একটা থেকে আরেকটা ধাপে গিয়ে পৌঁছয়, সেই কথাটিই আমি ছবিতে বলার চেষ্টা করেছি।’ সর্বোপরি ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ঋত্বিকের একটি অনুধ্যান; এককালের বাংলা—এখন তা আর নেই।
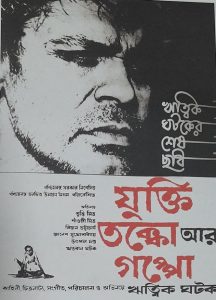 ঋত্বিক ঘটকের ব্যতিক্রমী ও সর্বশেষ ছবি হচ্ছে ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’। এটি ১৯৭৪ সালে নির্মিত হয়। ছবিটি রাজনৈতিক ধারার এবং আত্মজীবনীমূলক। ঋত্বিক নিজেও তা স্বীকার করেছেন। ছবিটি একটি দায়িত্বশীল জায়গা থেকে করা। ভারতীয় রাজনীতির যে স্বরূপ তিনি দেখেছেন, আর শিল্পীদের যে-ভূমিকা তা ঋত্বিককে সংক্ষুব্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন, ‘যুক্ত তক্কো গপ্পো সম্পূর্ণটাই ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সালের গোড়া পর্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে দিন-রাত্রি বাস করে যে-জীবনপ্রবাহ আমি দেখেছি, তার ওপর ভিত্তি করে করা। একটা সুতীব্র আক্রমণ এ ছবির লক্ষ্য। এমন সব ঘটনা ঘটছে, যা ঘটা উচিত নয়। এ অন্যায়, এ পাপ।…প্রতিবাদ করা শিল্পীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। শিল্প ফাজলামি নয়। যারা প্রতিবাদ করছে না, তারা অন্যায় করছে। শিল্প দায়িত্ব। আমার অধিকার নেই সে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার। শিল্পী সমাজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সে সমাজের দাস, এই দাসত্ব স্বীকার করে তবে সে ছবি করবে।’ দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঋত্বিকের কিছু ভাষ্য ছিল, অন্যের সঙ্গে তা না মিলতেও পারে। এই নিজস্ব বক্তব্য ও বোঝাপড়া নিয়ে ছবিটি করা আত্মজীবনের দর্পণে। কোনো কোনো সমালোচক একে বলছেন ঋত্বিকের এপিটাফ, ঋত্বিক একে বলেছেন, ‘It is completely a political film’. কিন্তু ছবিতে রাজনীতিটা কোথায়?
ঋত্বিক ঘটকের ব্যতিক্রমী ও সর্বশেষ ছবি হচ্ছে ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’। এটি ১৯৭৪ সালে নির্মিত হয়। ছবিটি রাজনৈতিক ধারার এবং আত্মজীবনীমূলক। ঋত্বিক নিজেও তা স্বীকার করেছেন। ছবিটি একটি দায়িত্বশীল জায়গা থেকে করা। ভারতীয় রাজনীতির যে স্বরূপ তিনি দেখেছেন, আর শিল্পীদের যে-ভূমিকা তা ঋত্বিককে সংক্ষুব্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন, ‘যুক্ত তক্কো গপ্পো সম্পূর্ণটাই ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সালের গোড়া পর্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে দিন-রাত্রি বাস করে যে-জীবনপ্রবাহ আমি দেখেছি, তার ওপর ভিত্তি করে করা। একটা সুতীব্র আক্রমণ এ ছবির লক্ষ্য। এমন সব ঘটনা ঘটছে, যা ঘটা উচিত নয়। এ অন্যায়, এ পাপ।…প্রতিবাদ করা শিল্পীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। শিল্প ফাজলামি নয়। যারা প্রতিবাদ করছে না, তারা অন্যায় করছে। শিল্প দায়িত্ব। আমার অধিকার নেই সে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার। শিল্পী সমাজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সে সমাজের দাস, এই দাসত্ব স্বীকার করে তবে সে ছবি করবে।’ দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঋত্বিকের কিছু ভাষ্য ছিল, অন্যের সঙ্গে তা না মিলতেও পারে। এই নিজস্ব বক্তব্য ও বোঝাপড়া নিয়ে ছবিটি করা আত্মজীবনের দর্পণে। কোনো কোনো সমালোচক একে বলছেন ঋত্বিকের এপিটাফ, ঋত্বিক একে বলেছেন, ‘It is completely a political film’. কিন্তু ছবিতে রাজনীতিটা কোথায়?
‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’র গল্পটি এক প্রৌঢ়, বিদগ্ধ ও মদ্যপকে কেন্দ্র করে। স্ত্রী যাকে ছেড়ে চলে যান দূর গ্রামে। দেশকে নিয়ে তরুণ বয়স থেকে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন এই নীলকণ্ঠ বাগচী। প্রতিহিংসায় ভাগ হয়ে যাওয়া দুই বাংলার মিলন চেয়েছেন সারা জীবন। কিন্তু নষ্ট রাজনীতি, স্বার্থপরতা ও বুদ্ধিজীবীদের কপটতা ও স্বার্থান্ধতা দেশকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তরুণরা হতাশ হয়ে অস্ত্র হাতে নেয়। কপর্দকহীন নীলকণ্ঠ রাস্তায় নেমে আসেন চাকরিপ্রার্থী তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের নচিকেতার সঙ্গে। দুজনের যাত্রা অজানার উদ্দেশে। এদিকে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রাম থেকে বাস্তুচ্যুত ও পাকিস্তানি আর্মির বর্বরতার শিকার বঙ্গবালা আশ্রয়প্রার্থী হয় নীলকণ্ঠের কাছে। তিনি তাকে গ্রহণ করেন মেয়ে হিসেবে এবং মনে করেন মেয়েটি নিছক বঙ্গললনা নয়, সে বাংলাদেশেরই আত্মা। আরও এক চাকরিহীন টোল পণ্ডিত তাদের সঙ্গী হোন। পরে পুরুলিয়ায় ভূমিদখলের লড়াইয়ে নিহত হোন পণ্ডিত। তার পরে তিন জনে মিলে যান বীরভূমে স্ত্রীর কাছে, দেখা হওয়ার পর রাতটা কাটান পার্শ্ববর্তী শালবনে। মদপান, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মদহনে দগ্ধ নীলকণ্ঠ বাগচীর সঙ্গে শালবনে দেখা হয় অস্ত্রধারী নকশালপন্থি তরুণদের সঙ্গে। দলপতির সঙ্গে চলে আত্মানুসন্ধান ও বিবৃতির দার্শনিক জিজ্ঞাসা। ভোররাতে বিদ্রোহী নকশালদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় সরকারি পুলিশের। ততক্ষণে স্ত্রীপুত্রও পৌঁছেছেন ঘটনাস্থলে। তাদের উপস্থিতিতেই একটা গুলি লাগে নীলকণ্ঠ বাগচীর তলপেটে। তিনি মারা যান। এইটুকু গল্পে ঋত্বিক একদিকে যেমন উন্মোচিত করেছেন আত্মজীবন ও আত্মদ্বন্দ্বের ক্ষতমুখ, অন্যদিকে চিত্রিত করেছেন সমকাল ও সমকালীন রাজনীতির বীভৎস দিক। ভারতরাজনীতি শান্তিপ্রিয়, দায়িত্বশীল ও সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীদের জীবনকে কীভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল এই সিনেমার নীলকণ্ঠ বাগচী সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। হতাশাগ্রস্ত অ্যালকোহোলিক নীলকণ্ঠ বাগচী একটি সংলাপে বলছে, ‘সাতচল্লিশের স্বাধীনতা? ফুঁ!’ আবার অন্য জায়গায় একাধিকবার বলছে, ‘সব পুড়ছে, ব্রহ্মা পুড়ছে, আমি পুড়ছি!’ ব্যক্তি ঋত্বিকের দশাও ছিল তেমন। এক সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক বলেছেন, ‘ওই সময়ে আমার জীবনে যা ঘটে গেছে, ওই একাত্তরে, সেখান থেকেই ছবির starting point. আর, ওই মাতাল অবস্থায় একাত্তরের গোড়ার কলকাতার বুকে বসে কলকাতাকে খুব ওতপ্রোতভাবে দেখা গিয়েছিল।… তাই আমি সমাজের প্রতিটি স্তরকে কেটে দেখা এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি, সমস্ত মানুষ কীভাবে react করছিল সে সময়, সালতামামি গোছের আর কী! starting of point, আরম্ভটা শুধু আমার জীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে। …রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পটভূমি তখন যা ছিল, তা যেভাবে আঘাত করেছিল শহরের মানুষকে, শহরের মানুষ শুধু না, এ-ছবিতে আমি গ্রামবাংলাতেও গেছি, তা বেশিরভাগই আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা। এদিক থেকে এ-ছবিকে কিছু ব্যক্তিগত, আত্মচরিতমূলক বলা যায়, তবে আত্মচরিতমূলক বলতে যা বোঝায়, এ-ছবি সে-ধরনের নয়।’
ছবিটি শুরু ও শেষ হয় এক স্থবির লোককে দিয়ে, যে নির্বাক হয়ে শুধু তাকিয়ে আছে আর ভূতের নৃত্য দেখছে। নৃত্যরত এই যে ফিগারগুলো তা প্রতীকী, আর ইঙ্গিতবহ। পরে ঋত্বিক ব্যাখাও দিয়েছেন, ‘আমি বাপু বলতে চেয়েছি ভূতের নৃত্য চলছে গোটা বাংলাদেশে।… তোমরা নাচনকোঁদন-কীর্তন করে যাচ্ছ, যে যার কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করছে অল পলিটিক্যাল লিডারস। এবং এই ভূতের নৃত্যের জন্য তুমি এবং তোমরা দায়ী এটা বারবার ব্যবহার বলা হয়েছে। Dancing figureগুলোর আঙুল, তোমাকে সব সময় পয়েন্ট আউট করছে—You are responsible.’ দায়িত্বজ্ঞানশীলতার আত্মদহন ঋত্বিককে যেমন, নীলকণ্ঠ বাগচীকেও বিকারগ্রস্ত করে তুলেছিল। তাঁরা জানতেন রাজনীতিবিদেরা দেশকে যেভাবে প্রেতনৃত্যের দিকে নিয়ে গেছে তা থেকে আশু মুক্তির পথ নেই। কারণ ওই প্রেতগুলো সকল মধ্যবিত্তের মগজের কোষে কোষে, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বার্থবুদ্ধির কারণে। নয়তো যে-নচিকেতা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, তাকে নীলকণ্ঠ মজুরের চাকরি নিতে পরামর্শ দিত না, কারণ নীলকণ্ঠ জানেন এদেশে ইঞ্জিনিয়ারের দরকার নেই। আর, মানুষ এতটাই সংবেদনহীন হয়ে পড়েছে যে, পূর্ববঙ্গ থেকে উৎপীড়িত হয়ে বাস্তুচ্যুত সর্বহারা বঙ্গবালার পরিচয় পেয়ে জেনে মধ্যবিত্ত আর্টকালচার করা যুবকের মন্তব্য এমন, ‘পঙ্গপালের মতো পিলপিলিয়ে আসছে।’ অথচ নীলকণ্ঠ বাবু একে প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন, ‘তুমি কি বাংলাদেশের, আমার বাংলাদেশের আত্মা?’ পরে নচিকেতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বলেন, ‘বাংলাদেশ, নীড়হারা পাখি’। যে-নীড়হারা পাখির সন্ধান ঋত্বিক তাঁর পূর্ববর্তী ছবিগুলোতে করেছেন, এখানেও সেই স্পষ্ট করে বলেন। ঋত্বিক জানেন সেই বাংলাদেশটা ধূসর হয়ে গেছে; তার তা করেছে রাজনীতি নামক কঠিন জিনিসটি। বঙ্গবালার সঙ্গে যখন তার কাহিনি নিয়ে কথা হয় বঙ্গবালা বলেছিল ‘কেউ সাহায্য করতে আসে নাই আমাগো, কেউ না।’ এর জবাবে নীলকণ্ঠ বাগচী বলেছিলেন, ‘কেউ সাহায্য করবে না। মাগো আমার, এটা এমন একটা জিনিস—যার নাম রাজনীতি।’ কিন্তু চিরটাকাল আশাবাদী ঋত্বিক পরমুহূর্তেই আশার কথা বলান নীলকণ্ঠকে দিয়ে, বঙ্গবালা ও নচিকেতাকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলেন, ‘ওরে আমার ভালোবাসার ধন, তোরা এই বাংলাদেশের অংশ। নবীন বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ আজও জন্মায়নি।… ওরে আমারও একদিন নবীনত্ব ছিল। অনেক আশা, অনেক বিশ্বাস, অনেক উৎসাহ পুঁজি করে প্রেমে পড়ে গেলাম।’ কিন্তু সে প্রজন্ম আজ ক্ষয়ে গেছে, ব্যর্থ হয়ে গেছে সে যৌবন। বঙ্গবালাকে নীলকণ্ঠ তেমন ব্যর্থ এক বন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘আমার এক পুরাতন বন্ধু, বিরাট লেখক।…পর্নোগ্রাফি বেচে খায়। একদিন আরম্ভ করেছিল একজন সংগ্রামী সমাজসচেতন শিল্পী হিসেবে। আর এখন, পাতাল, সুড়ঙ্গ, পোকামাকড় এসব নাম দিয়ে বই লিখে বেচে খায়। চলছে বেশ।’ বুদ্ধিজীবীরা এভাবে আত্মবিক্রয় করেছেন এদেশে, যা মানা যায় না। কিন্তু এর পেছনকার রাজনৈতিক ফ্যাক্টস কী আর সমাধানই-বা কী? ঋত্বিক ভেবে আসছিলেন শিল্পীজীবনের শুরু থেকে। তাই শালবনের দিকে অগ্রসর হতে হতে ক্লান্ত, অবসন্ন ও মদ্যপ নীলকণ্ঠের কণ্ঠ জড়িয়ে যাচ্ছিল আর বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি চলছিল আপন ভাষায়। ‘সমাধান একটা বের করতেই হবে। এ চলতে পারে না। আমাদের সমস্ত generationটার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ওয়ে আউটটা কী? পথটা কী? থাকতেই হবে একটা কিছু থাকতেই হবে। অনেক ভাবলাম আমাদের বাংলাটার হিস্টোরিক কন্ডিশনটাকে কেউ সায়েন্টিফিক্যালি অ্যানালাইসিস করে না। বিজ্ঞানের সূত্রে ইতিহাসকে গাঁথেনি। এবং ক্লাসগুলো গত দুশো বছরে—উত্থান-পতন বিশেষ করে—যাকগে কেউ—এই যে ’৪৭ সালের বিশাল বিশ্বাসঘাতকতা, জাতীয় মুক্তির আন্দোলন, ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেন্ট-এর পিঠে ছুরি মেরে বুর্জোয়াদের ১৫ই আগস্টের বিরাট Great Betrayal—স্বাধীনতা—Indipendence—ফুঁ!’ তখনই বিদ্রোহী নকশালদের কবলে পড়ে হেঁয়ালি করে নিজের পরিচয় দেন এভাবে, ‘আমি ভাঙা বুদ্ধিজীবী—ব্রোকেন ইন্টেলেকচুয়াল—তোমাদের ভাষায় ক্ষয়ে যাওয়া, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের একটা হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া প্রতিবেশী—নাম নীলকণ্ঠ বাগচী।’ বিদ্রোহীরা পরিচয় পেলে জিজ্ঞেস করে তার এমন মদ্যপ দশা কেন? জবাবে নীলকণ্ঠ জানান তিনি যে-জেনারেশনের তারা দেশের সঙ্গে নাড়ির যোগ হারিয়েছে। এই জেনারেশন হয়তো চোর, নয়তো বিভ্রান্ত, নতুবা কাপুরুষ হয়ে পালিয়ে যাওয়ার মিছিল। খাঁটি কেউ নাই, একজনও না। তিনি বরং এই তরুণ বিদ্রোহীদের ‘ক্রিম অব বেঙ্গল’ বলে অভিহিত করেন। বলেন, ‘আমাদের সম্পূর্ণ পুঁজি তোমরা’।
কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির বিভাজন এবং বিভিন্ন পথ ও মতে যে তরুণেরা বিভ্রান্ত ঋত্বিক তা জানতেন আর এটাই যে জাতীয় মুক্তির পথে প্রধান বাধা তাতে তিনি শঙ্কিতও ছিলেন। নকশাল দলপতিকে নীলকণ্ঠ বাগচী কথাপ্রসঙ্গে বলেছেনও, ‘তোমাদের সিনসিয়ারিটি, তোমাদের বীরত্ব, তোমাদের আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা এসবে আমার কোনো সন্দেহ নেই।
কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির বিভাজন এবং বিভিন্ন পথ ও মতে যে তরুণেরা বিভ্রান্ত ঋত্বিক তা জানতেন আর এটাই যে জাতীয় মুক্তির পথে প্রধান বাধা তাতে তিনি শঙ্কিতও ছিলেন। নকশাল দলপতিকে নীলকণ্ঠ বাগচী কথাপ্রসঙ্গে বলেছেনও, ‘তোমাদের সিনসিয়ারিটি, তোমাদের বীরত্ব, তোমাদের আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা এসবে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা সম্পূর্ণ মিসগাইডেড। অগ্নিযুগের ছেলেদের মতোই তোমরা একই সঙ্গে সফল এবং নিষ্ফল। একসঙ্গে গোঁয়ার এবং অন্ধ।’ এর প্রতিবাদে বিদ্রোহী নকশাল নেতা পচে গলে যাওয়া প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে ধিক্কার দেয় নীলকণ্ঠ বাগচীকে। তার ভাষায় ‘সত্যিই আপনি একজন ক্ষয়ে যাওয়া, পচে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্বজ্ঞানহীন মাতাল প্রতিনিধি।’ সুতরাং নীলকণ্ঠ বাগচীদের জ্ঞান, বুদ্ধি আর আঁতলামোর কোনো মানে নেই। নকশাল তরুণের সঙ্গে নীলকণ্ঠ বাগচীর কথোপকথনের পুরো বক্তব্যই ছিল রাজনৈতিক এবং এই বক্তব্যে ঋত্বিকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রকাশ শুধু ঘটেনি, নিজের আদর্শিক অবস্থানও ফুটে ওঠে। ঋত্বিকের ভাবনায় মার্কসবাদ দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দ্বারা পরিচালিত। মার্কস-অ্যাঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ, কমরেড লেনিন কীভাবে টেনে নিয়ে গেলেন পুঁজিবাদের দিকে এবং একটা বিকাশের স্তরে। স্ট্যালিনই-বা কীভাবে একে আমলাতান্ত্রিক সমাজবাদে পৌঁছালেন এবং এরপরে মাও সে তুং কৃষক শ্রেণিকে সংগঠিত করে বিপ্লবের পথে নিয়ে এলেন। আর ব্যাপরটা সেখানেই থামেনি; চে গুয়েভারা আর ফিদেল কাস্ট্রো নির্ভর করলেন বুদ্ধিজীবী এবং কৃষকলীগের ছাত্রদের ওপর, এগুবার চেষ্টা করলেন। এরপরে যা যা হলো ঋত্বিক একে নিহিলিজম, টেররিজম, অ্যাডভেঞ্চারিজম প্রভৃতি নামে অভিহিত করে যা লেনিনের ভাষায় Infantile disorder হিসেবেও উল্লেখ করেন। আর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কম্যুনিজমের বাস্তবতাকে দেখেছেন ঋত্বিক অন্যভাবে যে ভৌগোলিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ভিত্তিতে। ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকার বাস্তবতা আর ভারতের বাস্তবতা এক নয়, গন্ডগোলটা বেঁধেছে এক ভাবতে গিয়েই। কিউবা কিংবা বলিভিয়ার সভ্যতার বয়স যেখানে মাত্র তিন-চারশো বছরের, ভূগোল ও ইতিহাসও অর্বাচীনকালের; সেই তুলনায় ভারতের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরোনো। তাই একই তত্ত্ব দিয়ে দুই ভিন্নধর্মী সমাজ-সভ্যতাকে রিফর্ম করা ভুল একটা পথ। নীলকণ্ঠ বাগচীর মুখ দিয়ে তাই নবীনদের উদ্দেশে ঋত্বিকের বক্তব্য, ‘দেখো বাবারা, ভাব দেখিনি এই ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস কত হাজার বছরের এবং যতই গাল দিই এদেশে সবচাইতে উজ্জ্বল দার্শনিক চিন্তা কিছু জন্মগ্রহণ করেছে, কাজেই সবচেয়ে বড়ো ফিচেল বদমাইশদের হাতে এদেশ প্রচুর হাতিয়ার তুলে দিয়েছে। এগুলা বদমাইশির অস্ত্র। কিন্তু সেগুলোকে বুঝে জাপটে ধরে উপড়ে ফেলতে হবে। ওরা নেই বললেই চলে যাবে না। ওদের শেকড় উপড়াতে হলে ওদের শক্তি এবং ওদের দুর্বলতা ভালো করে জানতে হবে। বুঝলে, বুঝেছ?’ তবে চলমান বাস্তবতায় কোনো সিদ্ধান্ত ভারত কিংবা বাংলাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে সেটা ঋত্বিকের জানা ছিল না। কারণ তিনি বারবার বিভিন্ন লেখায় ও সাক্ষাৎকারে বলে এসেছেন তিনি শিল্পী, রাজনীতিবিদ নন। ‘তবু বলি একটি সত্যি কথা। আমি confused. হয়তো আমরা সবাই confused…. utterly confused. আমরা সবাই দিশেহারা হয়ে, হাতড়ে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি।’ ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ তাই দিশেহারা বাংলা গল্প, দিশেহারা মানুষদের গল্প। যে-রাজনীতি মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন, দেশকে ভাগ করেছে, সমাজকে ক্ষয়িষ্ণু করেছে; ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে তার ব্যাপারে একজন শিল্পীর আর কীই-বা বক্তব্য থাকতে পারে? নীলকণ্ঠ বাগচী গুলির আঘাতে মারা যান, মারা যাবার আগে তরুণ নকশালবাদীর কাছে নিজেকে ‘শুয়োরের বাচ্চা’ বলে উল্লেখ করেন একটা ব্যর্থজন্ম তুলে ধরে। জীবনে যে কম্প্রোমাইজ করেননি স্ত্রী দুর্গার কাছেও সেই শেষ বাণীটুকু এমন ছিল, ‘মানিকবাবুর সেই মদনতাঁতির কথা মনে আছে তোমার? সেই যে বলেছিল, ভুবন মহাজনের টাকায় সুতো কিনে তাঁত চালাব? তোদের সঙ্গে বেইমানি করব? তাঁত না চালিয়ে পায়ের গাঁটে বাত ধরে গেছে তাই খালি তাঁত চালালুম একটু। একটা কিছু করতে হবে তো?’ শোষণের বিরুদ্ধে জেদ আর প্রতিবাদ, আর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নিয়েই সিনেমাটির সমাপ্তি ঘটে। ঋত্বিকের অন্য ছবিতের সমাপ্তি যেমন আশা, বিশ্বাস ও জীবনের প্রতি ইতিবাচকতা দিয়ে হয়েছে, এখানেও তেমন। সংকটময় একটা রাত কাটিয়ে ভোরের আলোয় জীবনের কথা দিয়েই সমাপ্তি। একটা ক্ষয়িষ্ণু প্রজন্মের মৃত্যু এবং নবীন প্রজন্মকে জীবনের দুর্নিবার গতির দিকে বাহিত করে গপ্পের সমাপ্তি রেখা, অন্য এক শুরুকেও ইঙ্গিত করে।
ঋত্বিকের কাছে সিনেমা শুধু সিনেমা ছিল না। এটি ছিল একটি হাতিয়ার। একটি শিল্প ফর্ম। এই ফর্মটাকে তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। এই বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মুক্তি। মানুষের মুক্তির সঙ্গে রাজনীতি বিশেষভাবে জড়িত বলে সিনেমাতেও অনিবার্যভাবে রাজনীতি অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। ঋত্বিক নিজেও মনে করতেন, ‘ফিল্ম apolitical—কোনো শিল্পী এটা বলে না।’ তাই প্রথম ছবি ‘নাগরিক’ থেকে সর্বশেষ ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ পর্যন্ত ছবিগুলোতে নানাভাবে রাজনৈতিক অনুষঙ্গকে তিনি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’র আগপর্যন্ত শ্রেণিবিপ্লব, দেশভাগোত্তর মানবিক সংকট, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা প্রভৃতিকে সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য-আকারে প্রকাশ করেননি। সেটা তাঁর অভিপ্রায়ও ছিল না। ছবিগুলোতে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে কোথাও ‘নিউ-কলোনিয়ালাইজড’ বলে প্রকাশ করেননি। তিনি মনে করতেন তেমন উল্লেখ করলে ছবি রাজনীতি হয়ে যেত, সিনেমা হয়ে উঠত না। তাই ছবিগুলোতে বরাবর তিনি in human terms ব্যাপারগুলো তুলে ধরে শিল্প ও জীবনের সাযুজ্য রক্ষা করেছেন। অন্যদিকে স্লোগান মঙ্গারিং করে, সমাধান দেখিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়াও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সমস্যাগুলোর রূপায়ণ করেছেন মাত্র, যারা দর্শক তারা যেন নিজেদের আয়নায় দেখে নিজেদের সমস্যার সমাধান খুঁজে নেয়। তিনি মনে করতেন শিল্পের কাজ ওইটুকুই, এর বেশি নয়। ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ সরাসরি রাজনীতি নিয়ে হলেও শেষপর্যন্ত ঋত্বিকের ছবির ঘরানার বাইরে নয়। বুদ্ধিজীবী বা শিল্পীর কমিটমেন্ট কী কিংবা কেমন হওয়া উচিত ছবিতে তাও গভীর সংবেদন নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। যে-রাবীন্দ্রিক শিল্পদর্শনে ঋত্বিক বিশ্বাসী ছিলেন—শিল্পকে হতে হয় সত্যধর্মী, আর শিল্পীকে হতে হয় মন্যুষত্বের প্রতি দায়বদ্ধ—ঋত্বিক-নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোতে তার প্রতিফলন দেখা যায় গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। এই নিষ্ঠা তৈরি করেছে তাঁর ছবির আপন রাজনৈতিক ভাষা। এই ভাষা বাংলা ও বিশ্ব-চলচ্চিত্রের সম্পদ। …

জন্ম সিলেটে, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর। তিনি একাধারে কবি, আখ্যান-লেখক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩৭। ‘নির্বাচিত কবিতা’ ও ‘কবিতাসংগ্রহ’ প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ২০১৭ ও ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে। সর্বশেষ প্রকাশিত কাব্য ‘আমি করচগাছ’ (২০২১), উপন্যাস ‘একটা জাদুর হাড়’ (২০২০), ভ্রমণ-আখ্যান ‘না চেরি না চন্দ্র মল্লিকা’ (২০২১) ও গবেষণা-গ্রন্থ ‘সিলেটের তাম্রশাসন : ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি’ (২০২৪)। সম্পাদনা করেন ছোটোকাগজ ‘সুরমস’ ও গোষ্ঠী পত্রিকা ‘কথাপরম্পরা’।