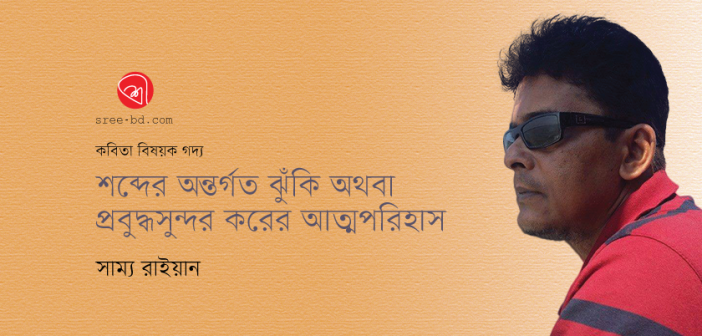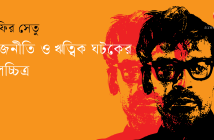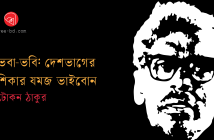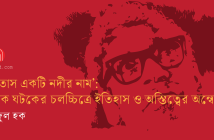কবিতা তার কাছে ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা, রাজনৈতিক মৃদু বিদ্রোহ এবং এক অন্তর্মুখী হাসির পুঁজি দিয়ে লালিত এক রচনাকৌশল। তার কবিতা কোনো প্রচলিত রোমান্টিকতা বহন করে না; বরং আত্মবিশ্বাসহীনতা, সংবেদী আত্মসমালোচনা এবং একধরনের চতুর, চাপা প্রতিবাদে আবৃত। বাংলা কবিতায় যা ‘সাবভার্সিভ কবিতা’ নামে পরিচিত, প্রবুদ্ধসুন্দর কর হয়তো তারই এক সংক্ষিপ্ত, নিরুচ্চার প্রতিনিধি—যার কবিতায় গভীর রাজনৈতিক উচ্চারণ নেই, কিন্তু মেদুর সামাজিক বিদ্রুপ আছে।
প্রবুদ্ধসুন্দর করের কবিতা আত্মজৈবনিক নয়, অথচ আত্মপরিহাসে পরিপূর্ণ; তাঁর কবিতা গম্ভীর নয়, বরং গম্ভীরতার মুখোশ ভেঙে ফেলে; এই কবিতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি জানায়, অথচ সংগঠিত রাজনীতির নয়, বরং অরাজনৈতিক সংকেত দিয়েই ভাষা তৈরি করে।
যেমন, ‘সংকর’ মাত্র তিনটি পংক্তির কবিতা। বাঙলা কবিতায় এত কম কথায়, এতটা আত্ম-আঘাতী সত্য অনেক কম লেখকই বলতে পেরেছেন:
`বাবা, বেগবান অশ্ব
মা, উদ্ভট সংসারের ভারবাহী গাধা
আমি খচ্চর, বাংলাকবিতা লিখি।’
এই কবিতাটি আত্ম-অবমাননা দিয়ে শুরু হলেও তা নিছক কৌতুক নয়। এখানে ‘খচ্চর’ শব্দটির মধ্য দিয়ে কবি যেন তার নিজের পরিচয়ের অনিশ্চয়তা তুলে ধরেন। খচ্চর—যে না অশ্ব, না গাধা—এই সংকর জাতটাই কবির কাব্যচর্চার উৎস। এবং এই সংকরতা দিয়ে কবি বাঙলা কবিতার নির্মাণকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন। এখানে ‘বাংলাকবিতা লিখি’ বলে যে আত্মসমাপ্তি, তা আসলে অনুচ্চারিত উপহাসও হতে পারে—যেখানে কবি নিজেই কবিতাকে লঘু করে তোলেন, আবার পাঠককেও ভাবতে বাধ্য করেন, কবিতা কাদের দ্বারা, কীসের দ্বারা রচিত হয়?
প্রবুদ্ধসুন্দর কর এক আশ্চর্য মর্মস্পর্শী অথচ সংযত বিদায় মুহূর্ত এঁকেছেন তিনি ‘দরজা’ কবিতায়। আমাদের আশেপাশের সম্পর্কগুলো যখন ভেঙে যায়, তখন সেই বিচ্ছেদের অনুভূতিকে কীভাবে সাহিত্যে ধরতে হয়, তা এই কবিতা নিঃশব্দে শিখিয়ে দেয়। কবি বলেন:
‘একটি কথাও না বলে তার
ব্রিফকেস গোছাতে সাহায্য করো।’
‘শুধু এগিয়ে দেওয়ার পথে নীচু স্বরে বোলো
দরজা ভেজানো থাকবে
টোকা দেওয়ার দরকার নেই।’
এই পরামর্শ—ভেতরে যে আবেগ জমে আছে তা যেন বাইরে না আসে—সেই অদ্ভুত সংযমের পাঠ, যা আমাদের সামাজিক আচরণেরও এক মডেল হয়ে দাঁড়ায়। বিচ্ছেদের মঞ্চে চিৎকার না করে, মৃদুস্বরে বলা “দরজা ভেজানো থাকবে” হয়ে ওঠে কবিতার হৃদয়। যেন এক লালন-কবি, যিনি বলেন, ‘যাহা বাহিরে, তাহাই অন্তরে’—তবে এখানে তা আরও সংযত, আরও নীরব, আরও গোপন।
তাঁর রাজনৈতিক কবিতার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক৷ যেমন ‘অস্ত্র’ কবিতাটি অনেকটা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞাপনের ছদ্মাবরণে লেখা রাজনৈতিক কাব্য। প্রথমদৃষ্টিতে মনে হবে এটি স্বাস্থ্য-পরামর্শ:
‘জল যখনই খাবেন, বসে দিনে জল বেশি খান, রাতে কম।’
‘ভুলে যাবেন না, অনেক কিছুর উপরই পেচ্ছাপ করে যেতে হবে আমাদের।’
এই কবিতাটি এক মোক্ষম কৌশল। কবি জানেন, আমাদের কোনো সংগঠন নেই, ম্যানিফেস্টো নেই, কিছুই নেই—শুধু আছে ‘বৃক্ক’। এই বৃক্ক বা কিডনি-কে কবি একমাত্র অস্ত্র বলেছেন, কারণ এটিই ছাঁকনি—ভালোকে রাখে, খারাপকে ত্যাগ করে। এখানে রাষ্ট্র বা সমাজের নোংরামি, কুৎসা, অবদমন এবং সহ্যশক্তির বিরুদ্ধে এক মেটাফোর তৈরি হয়। বৃক্ক সচল থাকলে, মানসিক প্রতিবাদও সচল থাকবে—এই বার্তাটি কখনোই সরাসরি দেওয়া হয় না, কিন্তু একটি স্বাস্থ্য-সতর্কবার্তার পেছনে যেন গোটা রাজনৈতিক কবিতাটিই ঢুকে পড়ে।
আধুনিক কবিতার কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব—সাহিত্যজগৎ বনাম ব্যক্তিগত অহংবোধ, তার এক নির্মম উপস্থাপনা ‘ইগো’। এ কবিতায় নিজেকে “এক নাস্তিক ব্লগার” হিসেবে দেখিয়ে কবি এমন এক দৃশ্যকল্প রচনা করেন, যেখানে “চাপ চাপ লাল ইগো মিশে যাচ্ছে পথের ধূলিতে।” কিন্তু এই ‘ইগো’ যেন কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং সামাজিক—কবি এখানে একতরফাভাবে প্রতারিত হয়েছেন বলেই নয়, বরং নিজের অবস্থান নিয়েও আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হয়েছেন। বাঙলাদেশে গত এক যুগের বাস্তবতা সম্পর্কে যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহলে তো জানেনই নিজেকে ‘ব্লগার’ শব্দদ্বারা পরিচয় করানোর অর্থই হলো মৌলবাদী গোষ্ঠীর কাছে নিজেকে হত্যাযোগ্য করে তোলা; আর যদি পরিচয় গড়ে ওঠে “নাস্তিক ব্লগার” তবে এদেশে তার হত্যা অনিবার্য৷ এমন পরিস্থিতিতে নিজকে “নাস্তিক ব্লগার” বলার মধ্য দিয়ে কবি আসলে এই সংখ্যালঘু, জিজ্ঞাসু অংশের মানুষেরই পাশে দাঁড়ালেই মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে৷
‘আমি তো তোমাকে ডাকিনি কখনো।
তুমিই এগিয়ে এসে খুব গায়ে পড়ে রেখেছিলে প্রণয়প্রস্তাব।’
এই ‘তুমি’ কে? প্রেমিকা? কবিতা? পাঠক? না কি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান? এই বহুব্যাখ্যামূলকতা কবিতাটিকে বহুমাত্রিক ও আধুনিক করে তোলে। এখানে চূড়ান্ত ব্যক্তিগত অপমান এবং সামাজিক বিদ্রুপ একসূত্রে বাঁধা।
তথাপি প্রবুদ্ধসুন্দর করের কবিতা কোনো নিরেট বক্তব্য দিতে চায় না—তারা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ‘ডামি’ পাঠকের সামনে রেখে আসল কবিকে গোপন রাখে। ‘ঝুঁকি’ কবিতার দিকে তাকানো যাক—
‘এতদিন যাকে দেখা গেল, সে আমার ডামি
…
আজ থেকে ডামি সরিয়ে সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিতে চাই।’
এই ঘোষণা, বাঙলা কবিতার জগতে এক নিজস্ব আত্মপ্রকাশ। আমরা যারা কবিতা লিখি, তাদের প্রত্যেকেরই এক-একটা ‘ডামি’ থাকে—নিরাপদ মুখ, সুস্থ স্বর, প্রতিষ্ঠানের উপযোগী ভাষা। কিন্তু এই কবিতাটি সেই মুখোশ খোলার কবিতা। এবং সেই মুখোশ খুলে কবি সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিতে চান—এই সাহসী উচ্চারণই প্রবুদ্ধসুন্দর করের কবিতাকে সমকালীন অন্য অনেক রচনার থেকে পৃথক করে তোলে।
শেষে যেটি বলা দরকার, তা হলো ‘কু-কবিতা’—যা প্রবুদ্ধসুন্দর করের রচনার সবচেয়ে সামাজিক এবং সবচেয়ে দার্শনিক নির্মাণ। একটি নীতিশিক্ষার খেলনা তিনটি পুতুল—যে পুতুলগুলো মুখ, কান ও চোখ বন্ধ রাখে—তার মধ্য দিয়ে কবি তুলে ধরেন সমগ্র সমাজের ভণ্ডামি। এমন লেখা কৌতুকের ঢঙে হলেও ভয়াবহ রকমের সিরিয়াস:
‘যে-পুতুল মুখ চেপে রাখে, তার চোখ ও কান খোলা থাকার কারণে সে সবসময় কু-কথা দেখে এবং কু-কথা শোনে।’
তিনটি পুতুলই নিজ নিজভাবে ব্যর্থ—কারণ তারা আংশিক নিষেধ মেনে চলে, পূর্ণত নিষিদ্ধ করে না। আর তাই: “আজ, দু-হাত খোয়ানো তরুণ কবিরা, কু-কথা বলতে বলতে, কু-কথা শুনতে শুনতে এবং কু-দৃশ্য দেখতে দেখতে, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মরুভূমির বালিতে, নীতিপ্রণেতাদের বিরুদ্ধে অজস্র কু-কবিতা লিখে রাখে।”
এই ভঙ্গিমার মধ্য দিয়েই প্রবুদ্ধসুন্দর কর হয়ে ওঠেন চূড়ান্ত প্রতিবাদী। কোনো রাজনীতি নেই, কোনো শ্লোগান নেই—তবু এই কবিতা কম্পিত করে। বালির ওপর পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে লেখা কু-কবিতার এই দৃশ্য আমাদের সময়ের অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাহসী কবির প্রতীক হয়ে থাকে।
প্রবুদ্ধসুন্দর করের কবিতা আমাদের সামনে তুলে ধরে একান্ত কাব্যিক ব্যক্তিত্ব, যে নিজেকে প্রচলিত কবিতার ‘ডামি’ থেকে মুক্ত করে “সম্পূর্ণ ঝুঁকি” নিতে চায়। তার ভাষা কখনো ঠাণ্ডা-বিদ্রুপে ভরা, কখনো আশ্চর্য নরম আত্মপরিচয়ে ঘেরা, কখনো আবার নিঃশব্দ বিস্ফোরণ। বাংলা কবিতার শ্লেষ, হাস্যরস, আত্মসমালোচনা এবং অন্তর্লীন বিদ্রোহকে যিনি এক কিমিয়া করে ফেলেছেন—তাঁর নাম প্রবুদ্ধসুন্দর কর। তাঁর কবিতা এক অস্ফুট দাহ—যার উত্তাপ পুড়িয়ে দেয় নৈতিকতা, নৈরাশ্য এবং নকল কবিতার মুখোশ।
পাঠ করুন প্রবুদ্ধসুন্দর কর-এর দশটি কবিতা

জন্ম ৩০ ডিসেম্বর; বাঙলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায়। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সম্পাদনা করছেন শিল্প-সাহিত্যের অন্যতর লিটল ম্যাগাজিন ‘বিন্দু’। কবিতা, প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি লিখেছেন নতুন ধরনের আখ্যানধর্মী গদ্য৷ সাম্য রাইয়ানকে নিয়ে ভারতের প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা ‘তারারা’ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের ‘মনমানচিত্র’, ভারতের ‘এবং পত্রিকা’ তাকে নিয়ে বিশেষ একক সংখ্যা ও বাংলাদেশের প্রখ্যাত লিটল ম্যাগাজিন ‘নিসর্গ’ বিশেষ মূল্যায়ন (ক্রোড়পত্র) প্রকাশ করেছে৷ ভারতের নব্বই দশকের কবি সুবীর সরকার সাম্য রাইয়ান প্রসঙ্গে ‘সাম্যপুরাণ’ শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।
প্রকাশিত গ্রন্থ: সুবিমল মিশ্র প্রসঙ্গে কতিপয় নোট [গদ্য, ২০১৪]; বিগত রাইফেলের প্রতি সমবেদনা [কবিতা, ২০১৫]; মার্কস যদি জানতেন [কবিতা, ২০১৮]; হলুদ পাহাড় [কবিতা, ২০১৯]; চোখের ভেতরে হামিং বার্ড [কবিতা, ২০২০]; লোকাল ট্রেনের জার্নাল [গদ্য, ২০২১]; লিখিত রাত্রি [কবিতা, ২০২২] ও হালকা রোদের দুপুর [কবিতা, ২০২৩]; জলের অপেরা [কবিতা, ২০২৪]; সকল প্রশংসা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের [উপন্যাস, ২০২৫]৷ সম্পাদিত গ্রন্থ: উৎপলকুমার বসু [নির্বাচিত রচনা ও পর্যালোচনা, ২০২২]; জন্মশতবর্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ [পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ সংকলন, ২০২৩]; শম্ভু রক্ষিত: পাঠ ও বিবেচনা [নির্বাচিত রচনা ও পর্যালোচনা, ২০২৫]।