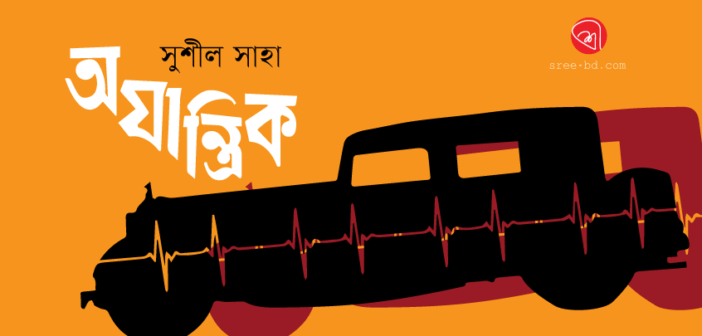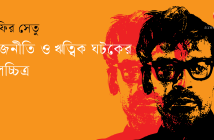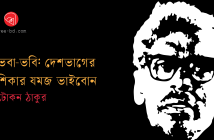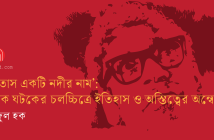১৯৪০ সালে ‘অযান্ত্রিক’ শিরোনামে একটি ছোটোগল্প লিখে পাঠকবর্গকে চমকে দিয়েছিলেন সুবোধ ঘোষ। সেটা ছিল ‘কল্লোল’ আর কালিকলম-এর যুগ। প্রায় একই সঙ্গে ‘ফসিল’ গল্পটা লিখে শ্রী ঘোষ বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসনটি পাকা করে নিয়েছিলেন। বিশিষ্ট সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যের কথায়, “…অযান্ত্রিকে’ যন্ত্রযুগ যেন কথা কয়ে উঠল। জড়ে আর জীবে এ যুগের জীবন যে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত, এই সত্যই যেন নতুন করে উদ্ভাসিত হলো এই গল্পে। সুবোধ ঘোষের শিল্পীমানসে যন্ত্র-যুগের প্রভাব যে কত গভীর, তার প্রমাণ পাই আরেকটি গল্পে, যেখানে যন্ত্রই মানুষের দেহযন্ত্রের উপমান হয়ে উঠেছে। …অযান্ত্রিক গল্পে যন্ত্রের প্রতি মানুষের মমতা, তার মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ-মিশ্র নৈষ্ঠিক অসক্তি চেতনার এক নূতন প্রদেশ উদ্ঘাটিত করে। … মানুষের প্রেম যেন অচেতন যন্ত্রের বুকেও প্রাণের সাড়া জাগাতে পেরেছে।
১৯৪০ সালে ‘অযান্ত্রিক’ শিরোনামে একটি ছোটোগল্প লিখে পাঠকবর্গকে চমকে দিয়েছিলেন সুবোধ ঘোষ। সেটা ছিল ‘কল্লোল’ আর কালিকলম-এর যুগ। প্রায় একই সঙ্গে ‘ফসিল’ গল্পটা লিখে শ্রী ঘোষ বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসনটি পাকা করে নিয়েছিলেন। বিশিষ্ট সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যের কথায়, “…অযান্ত্রিকে’ যন্ত্রযুগ যেন কথা কয়ে উঠল। জড়ে আর জীবে এ যুগের জীবন যে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত, এই সত্যই যেন নতুন করে উদ্ভাসিত হলো এই গল্পে। সুবোধ ঘোষের শিল্পীমানসে যন্ত্র-যুগের প্রভাব যে কত গভীর, তার প্রমাণ পাই আরেকটি গল্পে, যেখানে যন্ত্রই মানুষের দেহযন্ত্রের উপমান হয়ে উঠেছে। …অযান্ত্রিক গল্পে যন্ত্রের প্রতি মানুষের মমতা, তার মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ-মিশ্র নৈষ্ঠিক অসক্তি চেতনার এক নূতন প্রদেশ উদ্ঘাটিত করে। … মানুষের প্রেম যেন অচেতন যন্ত্রের বুকেও প্রাণের সাড়া জাগাতে পেরেছে।

‘অযান্ত্রিক’ সিনেমার শুটিংয়ের একটি দৃশ্য
গল্পটিতে এমন এক মহত্তর বার্তা ছিল যাকে চলচ্চিত্রের ভাষায় এক অনন্য রূপ দিয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক। ততদিনে তাঁর ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ মুক্তি পেয়ে গেছে। ‘বেদেনী’ শুরু করেও শেষ করতে পারেননি, আবার শেষ করেও মুক্তি পায়নি তাঁর পূর্ণদৈর্ঘ্যের প্রথম নির্মাণ ‘নাগরিক’। ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ মুক্তি পাবার অব্যবহিত পরেই মুক্তি পেল ‘অযান্ত্রিক’, বলা যায় ভারতীয় সিনেমার এক উচ্চাঙ্গের দিকবদলের বার্তা নিয়ে এলো এই ছবিটি। কিন্তু ছবির বক্তব্য সম-সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে থাকার কারণে সেটা তখনই দর্শকনন্দিত হলো না সেইভাবে। কিন্তু শিল্পীর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার সময় নেই। তিনি সৃষ্টির আনন্দেই মাতোয়ারা ছিলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও একটার পর একটা নির্মাণ করে গিয়েছিলেন, দর্শকের মনোরঞ্জনের কথা না ভেবেই।
সুবোধ ঘোষের ‘অযান্ত্রিক’ গল্পটিকে সেই অর্থে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে এক কথায় বিনির্মাণ করেছিলেন শ্রী ঘটক। আজ এতদিন পরেও ছবিটা দেখতে দেখতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই আমরা। কীভাবে একজন সত্যদ্রষ্টা শিল্পী তাঁর বলবার বিষয়টিকে কতদূর শিল্পীত করতে পারেন, তার উজ্জ্বল উদাহরণ এই ছবিটি।
সুবোধ ঘোষের ‘অযান্ত্রিক’ গল্পটিকে সেই অর্থে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে এক কথায় বিনির্মাণ করেছিলেন শ্রী ঘটক। আজ এতদিন পরেও ছবিটা দেখতে দেখতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই আমরা। কীভাবে একজন সত্যদ্রষ্টা শিল্পী তাঁর বলবার বিষয়টিকে কতদূর শিল্পীত করতে পারেন, তার উজ্জ্বল উদাহরণ এই ছবিটি। অথচ মূল গল্প থেকে একটুও সরে যাননি তিনি। লেখকের না বলা অনেক কথাই চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে বলতে পেরেছিলেন ঋত্বিক। অথচ ছবিটিতে তেমন করে গল্প বলার তেমন কোনো প্রগাঢ় কাঠামো নেই। তবু গল্প একটা তো আছেই। একটি পুরোনো গাড়ি চালকের দৃঢ় একরোখা এক ব্যতিক্রমী মনোভঙ্গির বিন্যাসে ছবিটির কাহিনি তরতর করে এগিয়ে যায়। ছবির নায়ক বিমলও তাই গড়পরতা মানুষের ভিড়ে একজন অন্যরকম মানুষ হয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
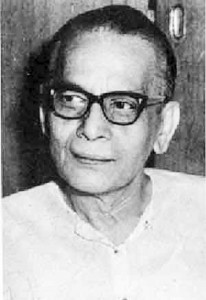
সুবোধ ঘোষ (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ – ১০ মার্চ ১৯৮০)
যে গাড়িটিকে নিয়ে ঋত্বিকের এই ছবি, সেটি এমনিতেই বহুদিনের পুরোনো এক মডেলের, যা একেবারে বাতিল হবার যোগ্য। সেই গাড়িটিকেই পরম মমতায় চালক বিমল বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এখানে সে প্রকৃত অর্থেই পালকের ভূমিকা নিয়ে নেয়। কীভাবে যেন প্রায় অচল সেই যন্ত্রদানবের সঙ্গে অলক্ষ্য এক মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ছবিটির বিন্যাসে এমন এক মুন্সিয়ানা দেখান ঋত্বিক যে সেই নির্মাণে কোথায় যেন একটু একটু করে জাদুবাস্তবতার ছোঁয়া লেগে যায়। অথচ তা কোনো প্রতীকের ছদ্মবেশ ধারণ না করে আমাদের বিশ্বাসের মূলে জাগিয়ে তোলে এক মানবিক অভিজ্ঞান।
এই মানবিক অভিজ্ঞানের একটি পাথুরে দৃষ্টান্ত দেবার জন্য সুবোধ ঘোষের মূল গল্প থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি এখানে, “…ভারী তেষ্টা পেয়েছে, না রে জগদ্দল? তাই হাঁসফাঁস কচ্ছিস? দাঁড়া বাবা দাঁড়া। জগদ্দলকে রাস্তার পাশে একটা বড় বট গাছের ছায়ায় থামিয়ে, বিমল কুঁয়ো থেকে বালতি ভরে ঠাণ্ডা জল আনে, রেডিয়েটরের মুখে ঢেলে দেয় বিমল। বগ বগ করে চার-পাঁচ বালতি জল খেয়ে জগদ্দল শান্ত হয়, আবার চলতে থাকে।”
ছবিটি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন কী অসীম দক্ষতায় ওই দৃশ্যটিকে নির্মাণ করেছিলেন ঋত্বিক। বিমলের অতি সাধের গাড়ি জগদ্দলের তৃষ্ণা নিবারণের সেই অসাধারণ নির্মাণে প্রাণ পেয়েছিল যন্ত্রটি। তার সেই ঢক ঢক করে জল খাওয়ার সময় নেপথ্যে বেজে ওঠা অসাধারণ শব্দবিন্যাস সমস্ত বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। যন্ত্রের নিষ্প্রাণ অবয়বেও যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। আমরাও অবুঝ বিমলের মতোই জগদ্দলকে জড়বস্তু না ভেবে এক প্রাণময় আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলি।

‘অযান্ত্রিক’ সিনেমার একটি দৃশ্যে কালি বন্দ্যোপাধ্যায়
মানুষের স্বাভাবিক প্রয়াণের মতোই একদিন জগদ্দলের প্রাণস্পন্দন থেমে যায়। পুরোনো লোহা-লক্করের মতো নির্জীব বস্তুখণ্ডের মতো সেগুলোও একদিন বিক্রি হয়ে যায় জলের দামে। সেগুলো গাড়ি ভর্তি করে নিয়ে যায় চতুর এক ক্রেতা। অন্যদিকে হতাশ-ক্লান্ত-বিমর্ষ বিমলের চোখের সামনে একটি ছোট্ট শিশু সেই গাড়ির পরিত্যক্ত হর্ণ বাজাতে বাজাতে যেন জানান দেয়, ‘প্রাণ আছে প্রাণ, আর প্রাণ থাকলেই বেঁচে থাকে মান’। বলাবাহুল্য ঋত্বিকের এই জীবনের জয়গানে মুখরিত শিশুপ্রতিমার প্রাণময় দৃশ্য আমরা দেখেছি তাঁর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এবং ‘সুবর্ণরেখা’য় যেখানে তিনি জোর গলায় বলতে পারেন, ‘জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের’। ‘শিশুতীর্থ’ কবিতার এই অমোঘবাণী শেষ পর্যন্ত যেন ঋত্বিকের জীবনদর্শন হয়ে ওঠে।
ঠিক এইভাবেই ঋত্বিক ঘটক একটি অসামান্য নির্মাণের মধ্য দিয়ে নিজের স্বতন্ত্র অস্ত্বিত্বের ঘোষণা দিয়ে যান এই ছবিতে। আর সেই কারণেই ‘অযান্ত্রিক’ এই বিশেষণটি আমাদের কাছে প্রকৃত অর্থেই ‘বিশেষ্য’ হয়ে ওঠে।
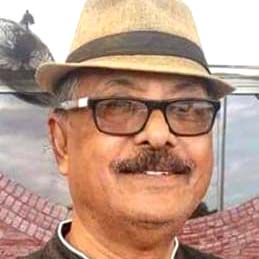
জন্ম (১৯৪৭) খুলনায়। লেখক ও সম্পাদক হিসেবে তিনি সুপরিচিত। দীর্ঘকাল সম্পাদকীয় সহযোগী হিসেবে যুক্ত ছিলেন ‘বিজ্ঞাপন পর্ব’ এবং ‘অনুষ্টুপ’ পত্রিকার সঙ্গে। সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩০। প্রিয় বিষয় সংগীত, নাটক ও নৃত্য। তাকে ‘দুই বাংলার নিরর্গল সেতু’ আখ্যা দিয়েছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। বর্তমান বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনার হৃদয়পুরে। পেশায় ছিলেন গ্রন্থাগারিক। ‘একটি গৃহের কথা’ শিরোনামে স্বল্পদৈর্ঘ্যের একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন।