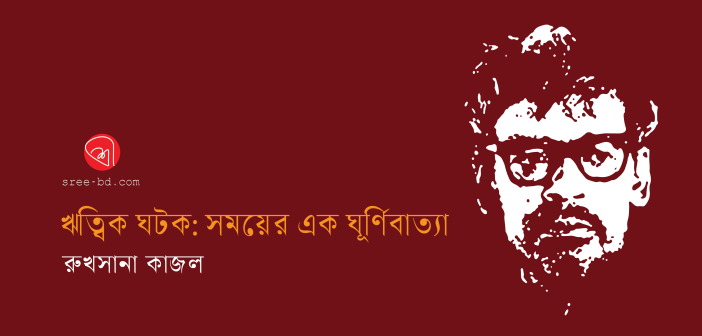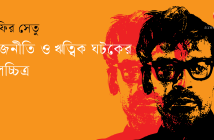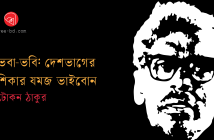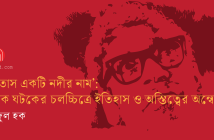বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটি ছোটো শহর। পাশে বয়ে যাচ্ছে কাটা মধুমতি। নদীর অন্যপারে ক্ষেতিজমির বিশাল বিস্তার পেরিয়ে পলাশ শিমুল কৃষ্ণচূড়ার ঘন সারি। শান্ত নিবিড় এই শহরে বর্ষা এলেই চাপা আনন্দে ফেটে পড়ত অধিকাংশ পরিবার। ছোটো ছোটো লঞ্চ ভাড়া করে পরিবার পরিজন নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ত পিকনিকের আবহে বর্ষা উদ্যাপন করতে। ঝুম বৃষ্টি, কাটা মধুমতি পেরিয়ে বড় মধুমতির তীর ঘেঁষে স্থির দাঁড়িয়ে থাকত নোঙর করা লঞ্চগুলো। বৃষ্টি ঢেকে দিচ্ছে ভেজা প্রকৃতির জলজ মুখ। বড় মধুমতীর স্ফীত বুক থেকে ডাক উঠেছে, গুমগুম। এরকম বর্ষাস্ফীত মধুমতির রুদ্ররাগ, ঘাটের ছাউনিতে আশ্রয় নেওয়া রাখালছুট কোনো গরুর ভয়ার্ত চিৎকার আর খিচুড়ির মৌতাতে উতলা পরিবেশে লঞ্চের বিশাল কেবিনের ভেতর কেউ হয়তো তখন গান ধরেছে বর্ষা মঙ্গলগীত, কেউ খেলছে দাবা। ঠিক সেসময়, সেই নিবিড় ঘন ঘোর আবহে, সিনেমা পত্রিকা চিত্রালী দেখতে দেখতে প্রচণ্ড আফসোস নিয়ে মা বলে উঠেছিল, কোলকাতা ছেড়ে না এলেই পারতাম গো। কত ভালো ভালো মুভি হচ্ছে জানো! দেখ—
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটি ছোটো শহর। পাশে বয়ে যাচ্ছে কাটা মধুমতি। নদীর অন্যপারে ক্ষেতিজমির বিশাল বিস্তার পেরিয়ে পলাশ শিমুল কৃষ্ণচূড়ার ঘন সারি। শান্ত নিবিড় এই শহরে বর্ষা এলেই চাপা আনন্দে ফেটে পড়ত অধিকাংশ পরিবার। ছোটো ছোটো লঞ্চ ভাড়া করে পরিবার পরিজন নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ত পিকনিকের আবহে বর্ষা উদ্যাপন করতে। ঝুম বৃষ্টি, কাটা মধুমতি পেরিয়ে বড় মধুমতির তীর ঘেঁষে স্থির দাঁড়িয়ে থাকত নোঙর করা লঞ্চগুলো। বৃষ্টি ঢেকে দিচ্ছে ভেজা প্রকৃতির জলজ মুখ। বড় মধুমতীর স্ফীত বুক থেকে ডাক উঠেছে, গুমগুম। এরকম বর্ষাস্ফীত মধুমতির রুদ্ররাগ, ঘাটের ছাউনিতে আশ্রয় নেওয়া রাখালছুট কোনো গরুর ভয়ার্ত চিৎকার আর খিচুড়ির মৌতাতে উতলা পরিবেশে লঞ্চের বিশাল কেবিনের ভেতর কেউ হয়তো তখন গান ধরেছে বর্ষা মঙ্গলগীত, কেউ খেলছে দাবা। ঠিক সেসময়, সেই নিবিড় ঘন ঘোর আবহে, সিনেমা পত্রিকা চিত্রালী দেখতে দেখতে প্রচণ্ড আফসোস নিয়ে মা বলে উঠেছিল, কোলকাতা ছেড়ে না এলেই পারতাম গো। কত ভালো ভালো মুভি হচ্ছে জানো! দেখ—
গলা বাড়িয়ে আমিও দেখলাম, কতগুলো চতুষ্কোণ সাদাকালো ছবির নিচে লেখা, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘ছেঁড়া তমসুক’, ‘সুবর্ণরেখা’—
কোলকাতা প্রসঙ্গ এলেই আব্বা চুপ করে যেতেন।
আমার আব্বা মাও ছিলেন শিল্পসাহিত্য, গান, কবিতা, নাটক সিনেমার তীব্র অনুরাগী। দেশভাগ ওঁদের এনে ফেলেছিল এই ছোট্ট শহরে যেখানে ছিল না কোনো সিনেমা হল, ছিল না মঞ্চ, নাটক। মাঝে মাঝে রবীন্দ্র নজরুল সুকান্ত, পয়লা বৈশাখ, ফাল্গুন উৎসব যাপিত হতো। কেউ কেউ কবিতা চর্চা করত, কবিতা সংখ্যাসহ দু-একটি লিটল ম্যাগাজিনও প্রকাশ পেত। একসময় শেষ হয়ে যেত এই সবকিছুর রেশ।
পূর্ববঙ্গের অনেকেই যারা পড়াশুনো, চাকরি, ব্যাবসা ইত্যাদির কারণে আবাস গেঁড়েছিল কোলকাতায়, দেশভাগ তাঁদের ফিরে আসতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু ততদিনে কোলকাতার শিল্প সংস্কৃতি আর প্রগতিশীল জীবন ধারার সঙ্গে কেউ কেউ অভ্যস্ত হয়ে গেছিল। আমার আব্বা মাও ছিলেন শিল্পসাহিত্য, গান, কবিতা, নাটক সিনেমার তীব্র অনুরাগী। দেশভাগ ওঁদের এনে ফেলেছিল এই ছোট্ট শহরে যেখানে ছিল না কোনো সিনেমা হল, ছিল না মঞ্চ, নাটক। মাঝে মাঝে রবীন্দ্র নজরুল সুকান্ত, পয়লা বৈশাখ, ফাল্গুন উৎসব যাপিত হতো। কেউ কেউ কবিতা চর্চা করত, কবিতা সংখ্যাসহ দু-একটি লিটল ম্যাগাজিনও প্রকাশ পেত। একসময় শেষ হয়ে যেত এই সবকিছুর রেশ। শুধু কয়েক জনের মনে জেগে থাকত শিল্প সংস্কৃতির প্রতি অগাধ ক্ষুধা। এই ক্ষুধা ওদের নিরালম্ব করে তুলত। মনে পড়িয়ে দিত কোলকাতার শিল্পসংস্কৃতির জগৎকে। তাই এরকম পরিবেশে বয়সে সামান্য অগ্রজ ঋত্বিক ঘটকের নাম উচ্চারণ করলে আমার আব্বা অন্যরকমের এক কষ্ট পেতেন।

ঋত্বিক ঘটক
মা জেনেছিলেন, আব্বা মঞ্চ নাটক, সিনেমা কবিতাতে ভীষণ আসক্ত। কল্লোলিনী কোলকাতার যেখানে যত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হোক না কেন আব্বা ছুটে যেতেন। দর্শকদের ভিড়ে শুধুমাত্র মুগ্ধ একজন হয়ে না থেকে মনে মনে তিনি মঞ্চের কোনো চরিত্র হয়ে যেতেন। মা ছিলেন সিনেমা, গল্পের বই আর নাটক পাগল। সদ্য বিবাহিত দুজন অচেনা মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ গড়ে দিয়েছিল দুজনের এই সংস্কৃতি প্রীতি। এরই মধ্যে ঘটে গেল দেশভাগ। বাঙালির রক্ত, মাংস, মেধা, বুদ্ধি, জ্ঞান, শুভমন, মনন, অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িকতার কূটপোকা। অগ্নিসাৎ হয়ে গেল সমস্ত শুভবুদ্ধি। ভ্রাতৃত্ব মুছে জেগে উঠল শত্রুতা। জেগে উঠল স্বার্থবাদী মন, তোমার-আমার, আমাদের-তোমাদের। রক্তগঙ্গা বয়ে গেল বাংলা আর পাঞ্জাবের ওপর দিয়ে। ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো টুকরো টুকরো হয়ে। কিন্তু সুখ কি এসেছিল হিন্দু-মুসলিম সমাজে? শান্তি পেয়েছিল কি হিন্দু-মুসলিম সমাজ? কোথায় স্বস্তি? একবুক কষ্ট নিয়ে ঋত্বিক চলে গেলেন কোলকাতা। সেই যে অসুখ, দেশভাগ যার নাম, ঋত্বিককে কুরে কুরে খেয়েছে আজীবন। না পারলেন মাতৃভূমিকে অনেকের মতো ভুলে যেতে, না পারলেন মাতৃভূমির বিভক্তি নিয়ে রংদার চলচ্চিত্র বানিয়ে বাণিজ্য করতে। বাংলা মায়ের দুয়ো রাজপুত্র হয়ে ঋত্বিক হয়ে উঠলেন ক্ষ্যাপা, অসম্ভব বুদ্ধিমত্ত, মাত্রাতিরিক্ত মননশীল, পরাক্রান্ত, আপসহীন এক প্রবল বুভুক্ষ।
যাপিত জীবনে কাগজে কলমে যতই ঋত্বিক ঘটক হয়ে উঠুন না কেন দীর্ঘ দেহের এই যুবকটি, আসলে তিনি তো ছিলেন পরিবারের ছোট্টটি, সবার আদরের ভবা। যমজ সহোদরা ভবির খেলার সঙ্গী। সেই ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর, ঢাকায় জন্ম এ দুটি ভাইবোনের। এদেশের জল মাটি আলোর শুদ্ধতা বুকে নিয়ে ভবা প্রতিদিন হেঁটে গেছেন জীবনের রুক্ষ পথে। কোলকাতায় পেয়েছিলেন এক বিশাল জগৎ। পেয়েছিলেন ক্যামেরার মতো দুটি চোখ। অসংখ্য ছবি তুলে মগজের ঘরে জমা রেখেছিলেন তিনি। আঠারোর তরুণ ঋত্বিক দেখেছিলেন তেতাল্লিশের মন্বন্তর। বাইশের ঋত্বিক দেখলেন ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর তেইশের ঋত্বিক নিজেই দেশভাগের ফাঁদে পড়ে হয়ে গেলেন উন্মূল, উদাসীন, বেপরোয়া, আপসহীন এক অগ্নিসখ উদ্বাস্তু । দেশভাগ কেড়ে নিয়েছিল ঋত্বিকের মানসিক আশ্রয়। ঋত্বিক কেবলই জ্বলেছেন, পুড়েছেন। সুগঠিত সচ্ছল শিক্ষিত মেধাবী পারিবারিক আভিজাত্যের আড়ালে তিনি সেই জ্বলুনিপোড়ানি ঢেকেঢুকে রাখার চেষ্টা করেননি। উগরে দিয়েছেন সপাট সাহসে। যখন সাম্প্রদায়িকতার উৎকট হনন ক্ষুধা মেটাতে রাজনীতিবিদরা নির্লজ্জের মতো টুকরো টুকরো করতে পেরেছিল দেশ মাতৃকাকে, যখন বাংলা আর পাঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশহারা, ঘরহারা, বন্ধু স্বজন, সম্ভ্রম, সম্মান, ইজ্জতহারা করে উদ্বাস্তু করে দিতে পেরেছিল রাজনৈতিক বোদ্ধারা, তখন ঋত্বিক কোনো লজ্জার ধার ধরে গল্প লিখবেন, নাটক করবেন, সিনেমা বানাবেন? ঋত্বিক, ঋত্বিকই।
তিনি ন্যুব্জ হননি। শিল্প নিয়ে জোচ্চুরি করেননি। কবিতা লিখেছন প্রথম জীবনে। এরপর গল্প। তারপর ঢুকে গেলেন বাম রাজনীতির অঙ্গনে। এরপর ভারতীয় গণনাট্য জগতে। আটাশ বছর বয়সে প্রেম নয়, বিরহ কিংবা জীবনকে সাধারণ মানুষের ছাঁচে ফেলে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়া নয়। বরং গণনাট্যকর্মী হিসেবে মঞ্চ কাঁপিয়ে ঋত্বিক বলে উঠেছিলেন, ‘বাংলারে কাটিবার পারিছ কিন্তু দিলটারে তো কাটিবার পার নাই।’ এ কী শুধু অভিনয় ছিল? বিশ্বাস হয় না। ঋত্বিক তো অভিনেতা হতে চাননি। তিনি সমগ্র বাংলাকে জড়িয়ে বুনতে চেয়েছিলেন এক অখণ্ড নকশিকাঁথা। পদ্মার পাড় থেকে আড়বাঁশি বাজাতে বাজাতে কোন এক সুরেলা প্রভাতে দিনের প্রথম সূর্যকিরণ গায়ে মেখে তিনি চেয়েছিলেন মহাগঙ্গাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাতে।
আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি, গোটা বিশ্বের গরিব, ভুখা, মানুষদের অধিকার কায়েমের সংগ্রামে রত বাম দলগুলো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে দুর্নীতি, ঘুস, অবৈধ ব্যাবসা বাণিজ্য আর ধর্মের পিচ্ছিল পথে। রাজনৈতিক পথ ছেড়ে অধিকাংশ তরুণ লোভের অলিগলি ঘুরে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়ে ব্যক্তিগত ভোগবাদীতে আস্থা রাখছে, যখন রাজনৈতিক অর্থনীতিতে প্রবীণ পোক্ত বুদ্ধিজীবীরা অর্থের বিনিময়ে দেশ বিক্রির ধান্ধায় দেশদ্রোহীদের সাথে হাত মেলাচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় উগ্র ধর্মান্ধ আর উগ্র জাতীয়তাবাদী মতাবলম্বী জনগণের একটি শ্রেণি যখন সমস্ত মেধা ঢেলে রাজনীতি মানে যুদ্ধ, আর যুদ্ধ মানেই প্রতিশোধ নেওয়ার সহজ হিসেবে মত্ত, যখন সংস্কৃতির বেড়ে উঠছে শিকড়ে বিচ্যুতির বনসাই, তখন কোথায় ঋত্বিক?
সার্কাসের হাতি মুক্তি পেলেও সে কি জানে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্তে বন অরণ্যে কীভাবে পদে পদে লড়াই করে জীবন বাঁচতে হয়? মুক্তি মিললেও হাতি তখন নতমুখে মানুষের দেওয়া কলাটা, মুলোটা, একগোছা চিটে ধান, পোকায় কাটা ফলমূল চোকলা খাওয়ার লোভে নেচেকুদে খেলা দেখায়। ঋত্বিক এ জীবন চাননি।
ঋত্বিকের সময়কালেও কি এই লোভের বেসাতি ছিল না? ছিল বলেই তো ঋত্বিক আপস করেননি। একা লড়েছেন। কম্প্রোমাইজ করার অর্থই তো হচ্ছে সারেন্ডার অর্থাৎ আত্মার স্বাধীনতাকে ছেঁটে ফেলা। সার্কাসের হাতি মুক্তি পেলেও সে কি জানে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্তে বন অরণ্যে কীভাবে পদে পদে লড়াই করে জীবন বাঁচতে হয়? মুক্তি মিললেও হাতি তখন নতমুখে মানুষের দেওয়া কলাটা, মুলোটা, একগোছা চিটে ধান, পোকায় কাটা ফলমূল চোকলা খাওয়ার লোভে নেচেকুদে খেলা দেখায়। ঋত্বিক এ জীবন চাননি। ওঁর বেঁচে থাকার সংবিধানে আপস বা জোচ্চুরির কোনো ধারা উপধারা ছিল না। অথচ প্রবলভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন। ‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতার মতো, ‘কোমল গান্ধারে’র ভৃগু অনুসূয়া, ‘সূবর্ণরেখা’র সীতা আর তিতাস একটি নদীর বাসন্তীর মতো! ট্র্যাজেডি এই যে, ঋত্বিক মরে গেল। মরে গেল নাকি নিজেকেই মেরে ফেলেছিল ঋত্বিক? বাঙালির ক্ষুদ্র মন মানসিকতার ওপর উপেক্ষার একটি দীর্ঘ রেফ রেখে ১৯৭৬ সালের ৫ মে মাত্র একান্ন বছর বয়সে যক্ষ্মা অর্থাৎ ক্ষয়রোগে তিনি মৃত্যুলোকে যাত্রা করলেন।
অথচ ইচ্ছে করলে ঋত্বিক তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলোকে কিছুটা রংদার উচ্চকিত করে তুলতে পারতেন। কিছুটা ব্যাবসায়িক পাঞ্চ মেরে, মোটা দাগের কিছু যৌনতা কিংবা গা চড়চড়ে বিশাল প্রতিবাদ দেখিয়ে তিনি পারতেন দর্শকদের মনে নানারঙের অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে। তাতে দর্শক ভি খুশ থাকত, চলচ্চিত্রটিরও লক্ষ্মীলাভ মানে অর্থকড়িসহ লাভের মুখ দেখত আর ঋত্বিকও কিছু টাকাপয়সা পেতেন। কিন্তু না, তিনি বিশ্বাস রেখেছেন আত্মসম্মান আর মানবিক মূল্যবধের ওপর। চলচ্চিত্রের সাথে মানবিক সত্যের সম্পর্ক রাখাকে তিনি জোর দিয়েছেন। সত্য কি এই যে, সাধ্য ছিল না বলে তিনি হেঁটো ধুতি পরেছেন, পাতার বিড়ি ফুঁকেছেন, বাংলা মদ গিলেছেন? একথা সত্য নয়। তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। যে প্রয়োজন বোধ করেননি লুম্বিনির রাজপুত্র গৌতম বুদ্ধ। শিক্ষিত সচ্ছল পরিবারের সন্তান, নিজেও শিক্ষিত, মেধাবী কিংবা শিক্ষিত বাউন্ডুলে, আয় রোজগারে গরজহীন বা দুর্ভাগ্যের শিকার এসব যুক্তির অবতারণা করে কোনো লাভ নেই। যুক্তি তো ধারালো ব্লেডের মতো। প্রয়োজনে আপাত উদ্ভূত সত্যকে কেটে দুভাগ বানাতে ওস্তাদ। যেভাবে ফেনিয়ে তোলা হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে দাবিতে পরিণত করে যুক্তির নিক্তিতে ফেলে রাজনীতিবিদরা অখণ্ড ভারতবর্ষকে কেটে তিন টুকরো করেছিল! তিনি তাই নিজের মতো করেই চলচ্চিত্র নির্মাণের কৌশল, পুরোনো আমলের যত্নে রাখা ধ্যানধারণাকে পাত্তা দেননি। তাই তো ‘সুবর্ণরেখা’ চলচ্চিত্রে দেখতে পাই, স্বামীর মৃত্যুর পর অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে দেহ ব্যাবসাতে নামা ছোটো বোন সীতার ঘরে আশ মেটাতে আসা পিতৃতুল্য বড় ভাই ঈশ্বরের আগমন। মাসখানেক আগে এই চলচ্চিত্রটি দেখার সময় শিক্ষিত স্বাবলম্বী কয়েকজন নারী ছি ছি করে বলে উঠেছিল, এটা আরোপিত। এটা হতেই পারে না। ঋত্বিক ঘটক এটা না দেখালেই পারতেন। ভাই বা দাদা কি কখনো দেহকামনা মেটাতে নিজ বোনের ঘরে যায়!

ঋত্বিক ঘটক
মেধার কী অথর্ব অনুশীলন আমাদের! দাদা ঈশ্বর কি জানতেন বারাঙ্গানা নারীটি তাঁর স্নেহসিক্ত ছোটো বোন সীতা! তিনি কি ইচ্ছে করে গিয়েছিলেন ওখানে?
প্রশ্ন জাগে, বিশ্বব্যাপী এত এত শুভ পরিবর্তনের পরে, আমাদের সমাজ কতটুকু পরিবর্তনের পথে এগিয়েছে? এগোলে তা কতখানি মুক্তমনা হতে পেরেছে? আদৌই কি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটেছে? মনের সংকীর্ণ দেওয়াল ভেঙে কবে আমরা চক্ষুষ্মান হব?
‘সুবর্ণরেখা’ চলচ্চিত্রটিতে দেশভাগ, অভিবাসন, শরণার্থী জীবন, দারিদ্র্য ছাড়াও জাতপাতের দ্বন্দ্ব বৈষম্যও দেখানো হয়েছে। বাগদী ব্রাহ্মণ জাতপাতের দ্বন্দ্ব। যা কিনা সতীর দাদা পরোপকারী ভালো মানুষ ঈশ্বরও অতিক্রম করতে পারেননি। অথচ এই জাতপাতের বৈষম্য আজ অবধি আমাদের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে কমবেশি করায়ত্ত করে রেখেছে। ঋত্বিকের এই সমাজ সচেতনতা বিষয়ে কিছু না বলে, না জেনে বোন সতীর ঘরে ঈশ্বরের ঢুকে পড়া নিয়ে আমরা ছিছিক্কার করছি ।
আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, ‘সোনা থুয়ে আঁচলে মারিছি গিট্টু।’
আদতে আমরা কি ঋত্বিককে ধারণ করার মতো, গ্রহণ করার মতো, যাপন করার মতো মেধা সাহস, শক্তি, মায়া, বোধ অর্জন করতে পেরেছি? সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পটভূমিতে হয়তো সহসা আর সম্ভব হবে না। অথচ ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ চলচ্চিত্রটি নির্মাণকালে ঋত্বিক ঘটক, মুহাম্মাদ খসরুকে দেওয়া সাক্ষাৎকার দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন, ‘চলচ্চিত্রকে নতুন করে ভালোবাসতে এসেছ তোমরা, ভালোবাসার মর্যাদা রেখো।’
আমরা কি ভালোবাসতে জানি? মর্যাদা বুঝি? এই মুহূর্তের বাংলাদেশকে দেখলে মনে হয়, জাতিগতভাবে বাঙালির রক্তের মধ্যে কোথাও বিচ্যুতির জিন সক্রিয় আছে। এত অবিশ্বাস, ভাঙচুরপ্রিয়, লোভী, হিংস্র, দেশদ্রোহী, অসম্মান জানাতে সিদ্ধহস্ত, কৃতঘ্ন, খুনি, অস্থিরমতি, নিষ্ঠুর তস্কর জাতি পৃথিবীতে আর নেই। তাই, গুণিজনদের কী করে শ্রদ্ধা জানাতে, ভালোবাসতে হয় কী করে সম্মান সম্ভ্রমের আবাহনে তাঁদের মর্যাদা জানাতে হয় আমরা সেসব জানি না, জানার চেষ্টাও করি না। ডি সিকার ‘বাইসাইকেল থিভস’ দেখে চলচ্চিত্র বানানোর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়, তেমনি আইজেনস্টাইনের ‘ব্যাটলশিপ পোটেমকিন’সহ ‘স্ট্রাইক’ চলচ্চিত্র দেখে মুগ্ধ ঋত্বিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য। বাংলাদেশের কেউ কি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সত্যজিত রায়, ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র নির্মাণ শৈলী দেখে? কিছু যে হয়নি তা বলব না, কিন্তু মানুষের জন্য সেভাবে কোনো চলচ্চিত্র কি নির্মিত হয়েছিল? আব্বাস কিয়রোস্তমি, ফারুগ ফারোগ্জাদ, সামিরা মাখমালবফ, মাজিদ মাজিদি লৌহ কঠিন শাসনের জালে বদ্ধ থেকেও বাস্তবভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করে চলেছেন। একটি জাতির শৈল্পিক উত্থান না ঘটলে আমরা হয়তো অনেক কালের জন্য হারিয়ে যাব।
বেগুনের একপিঠ ভেজে যেমন খাওয়া যায় না, তেমনি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর মার্যাদাও হতে হয় সাচ্চা। আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতারা সত্যকে ঢেকে অভুক্ত গরিব রাখালের সত্য প্রকাশের পরিবর্তে রঙিন বুটজুতা আর বাহারি পোশাক পরিয়ে এক রাখাল রাজকুমারকে গ্রামীণ পরিবেশে উপস্থাপনা করছে। গ্রামের তরুণীকে দেখাচ্ছে যৌবনমদে মত্তা পরাশ্রয়ী স্বাস্থ্যবতী পার্লারে সজ্জিতা হিসেবে। মধ্যবিত্ত ঘরের নারীরা সর্বাঙ্গে গহনা পরে রান্না করছে, টেবিল সাজাচ্ছে, অফিস করছে, ঘুমুচ্ছে। পুরুষের গার্হস্থ্যকর্মে কোনো অংশ নেই, উপার্জন করা ছাড়া। সংঘাত মানে কেবলই প্রেম, আর্থিক বৈষম্য, বংশ মর্যাদা, লুপ্ত জমিদারির অহংকার ঐতিহ্য মিলিয়ে মিশিয়ে এক আধা রূপকথার খইখিচুড়ি। এখানে সত্য কোথায়? আমাদের চলচ্চিত্র জগৎ এক অবাস্তব অসত্য কল্পিত কৌটায় বদ্ধ। ফলে বহুদিন আগেই মধ্যবিত্তরা হলে গিয়ে সিনেমা দেখা ছেড়েছে। আর এদেশের বুদ্ধিজীবী মহল এই শিল্পটি থেকে নিজের অবস্থানকে দূরাগত করে রেখেছিল। দেশের অধিকাংশ সিনেমা হল এখন শপিং মল কিংবা আকাশ ছোঁয়া ফ্ল্যাট বাড়িতে পরিণত হয়েছে। অথচ চলচ্চিত্র জনগণের কাছে পৌঁছানোর একটি শক্তিশালী মাধ্যম একথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও উল্লেখ করা হয়েছে ।
বিড়িতে ফুঁক দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘বাংলার আবার এপার ওপার কী?’ কথাটি কি অসত্য? মোটেও না। তবু ইতিহাসে যা কিছু ঘটে গেছে তা আর শোধরানো যাবে না জেনেও তিনি ছুটে এসেছিলেন একাত্তরে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত কিন্তু লড়াকু বাংলা ও বাংলাদেশের মানুষদের পাশে।
ঋত্বিক বলেছিলেন, চলচ্চিত্র হবে মানুষের জন্য। দেশের মানুষের হৃদয়ের টান বুঝতে হবে। এই টান এমন এক টান, যাতে পূর্বপুরুষের নাড়ি সকাতরে কেঁপে উঠে ডাক দেয়, ভাই, ও ভাই, বইনগো সন্তান মোর। ঋত্বিকের মনের টান এমনই ছিল। বিড়িতে ফুঁক দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘বাংলার আবার এপার ওপার কী?’ কথাটি কি অসত্য? মোটেও না। তবু ইতিহাসে যা কিছু ঘটে গেছে তা আর শোধরানো যাবে না জেনেও তিনি ছুটে এসেছিলেন একাত্তরে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত কিন্তু লড়াকু বাংলা ও বাংলাদেশের মানুষদের পাশে। কোলকাতার শিল্পী সমাজসহ সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে সাহায্য তুলেছেন আবার ওই দুঃসময়ে ‘দুর্বার গতি পদ্মা’ নামে একটি তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেছিলেন যেখানে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের অন্যায় নির্মমতাকে তিনি তুলে ধরেছিলেন। ঋত্বিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল নায়িকা নার্গিস দত্তের। তিনি অবসর নেওয়া সত্ত্বেও এই তথ্যচিত্রে বাংলা মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। জানি না, কজন বাংলাদেশি এ তথ্যটি জানে। জানলেও কতখানি শ্রদ্ধা ভালোবাসায় ঋত্বিককে যথাযথ মর্যাদায় সম্ভ্রম জানিয়ে একথা বলতে পারে, ঋত্বিক আপনি আমাদেরই লোক।
এখন সময় বদলেছে। প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রগতির পথ ছেড়ে মরুভূমির পথ ধরেছে বহুদিন ধরে। অনেককাল আগেই এদেশে যাত্রা শিল্প নিষিদ্ধ প্রায়। একসময় বাংলাদেশের মানুষের বিনোদন বলতে ছিল, যাত্রা। ছিল লোকজ গান। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে ‘লীলাবালি লীলাবালি ভরা যুবতী সই গো, কী দিয়া সাজাইমু তোরে’ ছাড়াও একটি লোকজ বিয়ের গান এই প্রথম আমি শুনতে পেলাম। চমৎকার সিলেটি গান। ‘আমের তলায় ঝামুরঝুমুর, কলা তলায় বিয়া, আইলা গো নয়া জামাই, মুটুক মাথাত দিয়া’—এছাড়া আছে, অসাধারণ শাস্ত্রীয় সংগীত আর রবীন্দ্র সংগীতের জীবনমুখী ব্যবহার। মৃত্যু, যা কিনা ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের অবিসংবাদী বিষয় ছিল, তার পাশে জীবনকে বহে যেতে দিয়েছিলেন তিনি, সেখানে গান থাকবে না—তাই কী হয়!
তবে কত দিন আমরা এসব শুনতে পাব জানি না। বর্তমান বাংলাদেশ যে পথে হাঁটছে সে পথে কেবল ধু-ধু বালু। ধর্মের দোহাই পেড়ে হয়তো একদিন সুর সংগীত দ্রুত নাজায়েজ ঘোষণা করা হবে। ইদানীং নারীর ওপর সহিংসতা বাড়ছে। বাড়ছে অগ্রগামী নারীসমাজকে ধর্মীয় বয়ানে রুদ্ধ করার অপচেষ্টা। পরিবার, সম্পত্তি, কর্মস্থল, বন্ধুত্ব, সহবসবাসের সমতার দাবি তুললেই, এক শ্রেণির মানুষ ‘বেশ্যার আবার হিস্যা’ বলে ট্রোল করছে তাতে বাংলাদেশের নারীদের ভবিষ্যৎ কতটা মুক্ত স্বাধীন থাকতে পারবে সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ, আশঙ্কা, ভয় জাগছে। আর এরকম অন্ধ বন্ধ বদ্ধ সময়ে আমার চোখে ভেসে উঠছে ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের নায়িকাদের মুখ। ঋত্বিক শুধু দেশভাগের যন্ত্রণায় ঘোর আবদ্ধ ছিলেন, তা নয়। তিনি জানতেন, রাষ্ট্র , দেশ, পরিবার, মানব জীবন এবং প্রাকৃতিক যেকোনো দুর্বিপাকের বিপক্ষে নারীকে লড়তে হয় সর্বস্ব দিয়ে। নারী লড়ে, নীতার মতো সর্বস্ব দান করে, গীতার মতো সুবিধাবাদী হয়ে, অনুসূয়ার মতো আরামের জীবন ছেড়ে, সীতার মতো অপার হয়ে আর বাসন্তীর মতো লড়াকু হয়ে নারীকেই লড়ে যেতে হয়, হয় জীবন, না হয় মৃত্যু আদায়ের শর্তে। সেই সংগ্রামে কোনো শাপশাপান্ত, প্রতিরোধ, সংস্কার, পুরুষতান্ত্রিকতা আর ধর্মের ঠাঁই নেই। নারীর লড়াইয়ের একটিই লক্ষ্য, বাঁচাতে হবে। এ কারণেই বিধাতা নারীকে গর্ভ দিয়েছেন। বিচ্যুতি নয়, ধারণই নারীর ধর্ম। নারী তাই ঈশ্বরী বৈকি!
ঋত্বিকের জন্মের শত বছর আর মৃত্যুর উনপঞ্চাশ বছর চলছে। প্রায় তিরিশ বছরের কর্মময় জীবনে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার মতো মানুষটিকে অগোছাল, হেঁটো, উদ্ধত, অবিনয়ী, আবেগী বলে মনে হলেও, তিনি কিন্তু নারীকে বুঝেছিলেন মানুষ হিসেবে। কিন্তু একমাত্র অনুসূয়া ছাড়া প্রতিটি দুঃখী লড়াকু নারীকে তিনি বাঁচতে দেননি। মৃত্যুই কি ছিল এদের প্রাপ্য উপহার?
ঋত্বিকের জন্মের শত বছর আর মৃত্যুর উনপঞ্চাশ বছর চলছে। প্রায় তিরিশ বছরের কর্মময় জীবনে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার মতো মানুষটিকে অগোছাল, হেঁটো, উদ্ধত, অবিনয়ী, আবেগী বলে মনে হলেও, তিনি কিন্তু নারীকে বুঝেছিলেন মানুষ হিসেবে। কিন্তু একমাত্র অনুসূয়া ছাড়া প্রতিটি দুঃখী লড়াকু নারীকে তিনি বাঁচতে দেননি। মৃত্যুই কি ছিল এদের প্রাপ্য উপহার? কেন? তবে কি ঋত্বিকও কোনো না কোনো সংস্কারের জালে আচ্ছন্ন ছিলেন? ভেবেছিলেন উদ্বাস্তু, অসহায়, দরিদ্র, স্বজনপীড়নে প্রতারিত, ক্লান্ত উপরন্তু রাজ রোগে দীর্ণ মানুষরা তো এভাবে টসকে যায়, তাই নীতাকেও মরতে হবে। আর সীতা? দেহবিক্রয়ের আদিম পেশায় গিয়েছিল বলেই কি মরতে হলো? আরেকটু উদার হলে, দাদা তো বোনকে ওই অন্ধগলি থেকে উদ্ধার করে আনতে পারত। পারত না? সে সুযোগ দেননি ঋত্বিক। কেন? অথচ ঋষি গৌতম মা হিসেবে বহুর পরিচর্চাকারী দেহপসারিনী জবালা মাকে অসম্মন করেননি। পুত্র সত্যকামের সুকীর্তির সম্মানে জবালা মা আজ অবধি বেঁচে আছেন জাবাল উপনিষদে। মালোপাড়ার দুঃসাহসী যুবতি বিধবা বাসন্তীকে কেন মরে যেতে হলো? মালো বলে? অভাব, দৈন্য, অসম্মান আছে বলেই কি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে দুস্থ, অসহায়, রোগাক্রান্ত, বিধবা নারীদের? নাকি সময়ের ঘাটে ঋত্বিকও বোতাম হয়ে গেছিলেন!
আজকের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নারীদের অধিকাংশই স্বাবলম্বী, সচল। যতই তাদের বেশ্যা বলে দাগিয়ে দেওয়া হোক না কেন, তারা উপেক্ষা করতে জানে। যদিও ধর্ম ও পুরুষতন্ত্র পিছু লেগেই আছে। যেমন বাংলাদেশে ইদানীং নারীর মাপকাঠি হিসেবে কেবলই ভোগ্যপণ্যকে নিরিখ করা হচ্ছে। ধর্মের পিঠে ভর দিয়ে জেগে উঠেছে পুরুষতান্ত্রিকতা। কিছু নারীও বিনা ক্লেশে জীবন কাটানোর ইচ্ছেয় পুরুষতন্ত্রের সহযোগী হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু নারীরা জাগছে। শত শত পিছুটানের দোহাই পেড়ে এই নারী অগ্রগতিকে আর ঠেকানো যাবে না। রামের সীতা মুখ লুকাতে বসুন্ধরার কোল চেয়েছিল, ঋত্বিকের সীতা বেছে নিয়েছিল আত্মহত্যা, কিন্তু বাংলাদেশের নীতা, সীতা বাসন্তীরা পুরুষতন্ত্রের ছুড়ে মারা অস্ত্রকে শান দিয়ে রাজপথে সমবেত চিৎকারে স্লোগান তুলেছে, ‘আমরা সবাই বেশ্যা, বুঝে নেব হিস্যা’
ঋত্বিক হয়তো এই হিস্যা পাওয়ার ব্যাপারটুকু নারীদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বেঁচে থাকলে লড়াইরত নারীদের দেখে বিড়ির ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে হয়তো ভেজা চোখে হুহু করে হেসে উঠতেন।

একাডেমিক পড়ালেখা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। পারিবারিক আবহে লেখালেখির শুরু। নিভৃতে থাকতে ভালোবাসেন। স্বদেশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশের বিভিন্ন পত্রপরিকায় গল্প ও নিবন্ধ লেখেন। এ পর্যন্ত দুটি ছোটো কলেবরের উপন্যাস, কয়েকটি গল্প এবং অণুগল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। উত্তরণ প্রকাশনা থেকে সদ্য প্রকাশিত হয়েছে একটি গল্পের বই, ‘করালদুপুরের গল্পগুলো’। পেশায় অধ্যাপক । দেশি বিদেশি সাহিত্য, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ইতিহাস বিষয়ে পড়ালেখা করতে ভালোবাসেন।